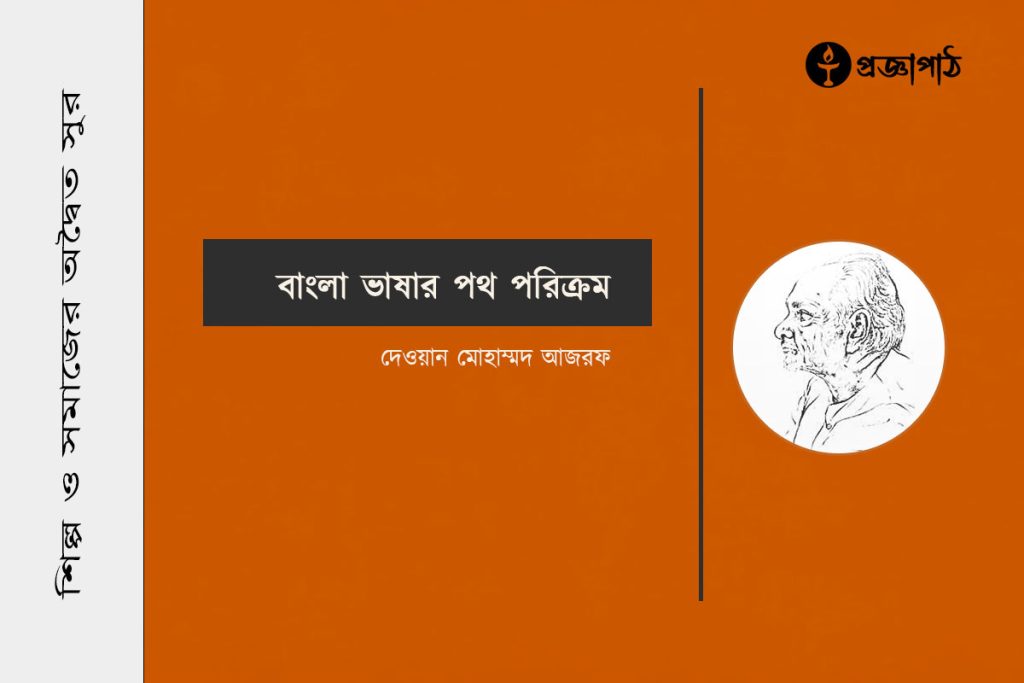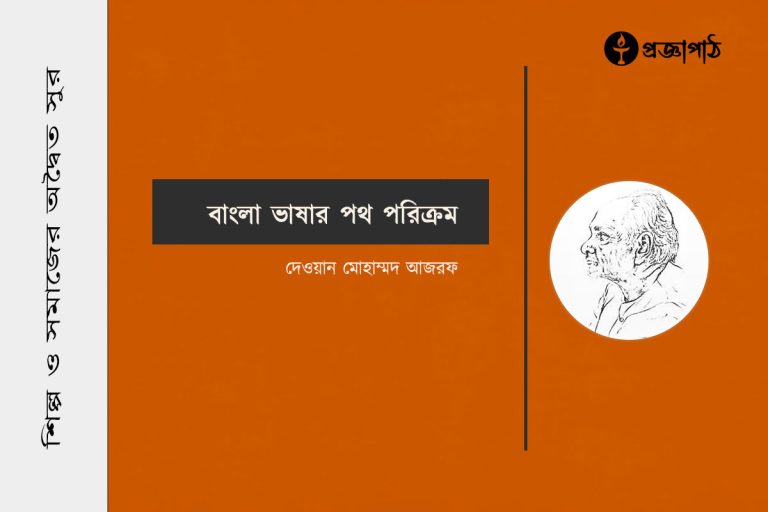এদেশে মুসলিম দরবেশদের বা সুফিদের আগমন আরম্ভ হয়েছে সপ্তম শতাব্দি থেকে । তাদের সমসাময়িক আরব বণিকেরাও চট্টগ্রামের উপকূলে উপস্থিত হয়ে ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম প্রচার করেছেন। তারা খুব সম্ভব আরবি ভাষাভাষী লোকই ছিলেন। তবে প্রচার বা ব্যবসায়ের তাগিদে তারা হয়তো এদেশীয় ভাষাও রপ্ত করেছেন। তাদের আগমন কালে ভারত সম্রাট ছিলেন হর্ষবর্ধন এবং বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন শশাংক। শশাংক ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসারী। এজন্য তিনি ইতোপূর্বে বাংলাদেশে আগত বৌদ্ধ ধর্মের উপস্থিতি মোটেই সহ্য করতে পারেননি। তিনি নানাভাবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের নির্যাতন করেছেন। তার মৃত্যুর পর প্রায় শতেক বছর বাংলাদেশে মাৎস্যন্যায় নীতি প্রচলিত ছিল অর্থাৎ জোর যার মুল্লুক তার। এ নীতির অনুসরণ করে প্রবল বা শক্তিশালী দুর্বলকে গ্রাস করতে পারতো। এ যুগের শেষে অষ্টম শতাব্দীতে পাল রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা হয় । পাল বংশের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী । তাদের রাজত্ব কালেই বির্তনের ধারায় বাংলা ভাষার উৎপত্তি । দেব ভাষা থেকে প্রাকৃত, পালি শৌর সেনী প্রভৃতি স্তর পার হয়ে, বাংলা ভাষা তার আদিরূপ নিয়ে দেখা দেয়। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের মিউজিয়ামে যে বাংলা ভাষার আদিরূপের পরিচয় পেয়েছেন—তাতে বৌদ্ধ চর্যাপদ রয়েছে। এতে সহজভাবেই ধারণা করা হয় বাংলা ভাষার আদিজনক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকেরা। তবে সে সময় বৌদ্ধ রাজাদের রাজত্ব থাকলেও শাসনকার্যে বাংলা ভাষা ব্যবহারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে পাল বংশীয় রাজা ২য় মহীপালকে দিব্যক নামক এক সামন্ত সরদার নিহত করে সমগ্র বরেন্দ্রভূমি অধিকার করলে পাল রাজত্বের অবসান ঘটে। তবে অচিরেই বিদ্রোহী দিব্যককে উৎখাত করে একাদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে সেন রাজগণ বঙ্গদেশ অধিকার করেন। সেন রাজগণ ছিলেন ব্রাক্ষ্মণ্য ধর্মের অনুসারী। এজন্য তারা তাদের পূর্ববর্তী রাজা শশাংকের মতো পুনরায় বৌদ্ধ নির্যাতনে আত্মনিয়োগ করেন। যেহেতু বাংলা ভাষা দেব ভাষা থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছিল এবং তাতে বৌদ্ধদের অবদান ছিল সর্বপ্রধান, এজন্য তারা এ ভাষাকে মোটেই আমল দেয়নি। তাদের রাজসভায় গীত গৌড় গোবিন্দ দাসের রচয়িতা জয়দেব সংস্কৃত ভাষার এক নতুন রীতির প্রচলন করেছিলেন। তা এখনও সুধীমহলে গৌড়ীরীতি নামে প্রচলিত। তাতে দোষী প্রমুখ আরও কবিদের উপস্থিতি থাকলেও তারা সকলেই সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে তাদের ভাব প্রকাশ করেছিলেন। বাংলা ভাষা ছিল ইতরজন বা সর্বসাধারণের ভাষা। অবিভক্ত বাংলাদেশে নানা অঞ্চলে সপ্তম শতাব্দী থেকে সুফি দরবেশদের আগমনের পরে তারা তাদের বাসস্থানের বা আস্তানায় খানেকাহ্ বা আধ্যাত্মিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে সে অঞ্চলের লোকদের ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণ করতেন। যেহেতু সমগ্র অঞ্চলই ছিল বাংলা ভাষাভাষী । খুব সম্ভব তাঁরা কুরআন-উল করীম ও হাদিস শরীফের নানা বাণীকে এদেশীয় ভাষার মাধ্যমে জনসমাজে প্রচার করেছেন।
১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক এদেশ অধিকৃত হলে এদেশীয় মুসলিম সুলতানদের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে তারা রাজভাষা হিসাবে ফার্সিকে গ্রহণ করেন। তেমনি ধর্মীয় ভাষা হিসাবে আরবিকে এবং তাদের খাসমহলে তাদের মাতৃভাষা তুর্কিকে বজায় রাখেন। তবে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত বাংলা ভাষাকে তারা অবজ্ঞা করেননি। তখনকার দিনে যারা বাংলা ভাষার চর্চা করতো, তাদের উৎসাহ দান করেন। তাদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে বাংলা ভাষায় প্রাচীন যুগের কবিগণ কাব্যরচনা করতে প্রবৃত্ত হন। এ সুলতানগণের মধ্যে গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দীন (যার কবর সোনারগাঁয়ে বর্তমান) এবং সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। সুলতান গিয়াসউদ্দীন কেবল বাংলা ভাষার লোকদের কাছেই প্রিয় ছিলেন না, তিনি ব্রজবুলি ভাষার সুপ্রসিদ্ধ কবি বিদ্যাপতির নিকটও অতিশয় প্রিয় ছিলেন। তার নিদর্শন বিদ্যাপতির কাব্যে রয়েছে।
সে যুগে এদেশে মুসলিম সুলতানদের রাজত্ব থাকার ফলে তাদের দ্বারা ব্যবহৃত আরবি, ফার্সি ও তুর্কি শব্দাবলি অবলীলাক্রমে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে। বাংলা ভাষায় সে যুগের লেখকদের মধ্যে যদিও হিন্দু সমাজের লোকেরাই অগ্রণী ছিলেন, তবুও তাদের লেখায়ও যথেষ্ট আরবি, ফার্সি ও তুর্কি শব্দের ব্যবহারে প্রমাণ পাওয়া যায় । তবে মুসলিম সুলতানদের আধিপত্য বঙ্গদেশে থাকলেও তারা দিল্লির সুলতানদের অধীন ছিলেন বলে এবং দিল্লির সুলতানদের সঙ্গে বাংলা ভাষার তেমন কোন যোগ না থাকার ফলে বাংলা ভাষা রাজভাষার মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। বাংলা ভাষা পূর্বাপর বঙ্গদেশের নাগরিকদের কথ্য ভাষার পর্যায়ে থেকে যায়।
বাংলা ভাষার মুসলিম কবিগণের রচনা আরম্ভ হয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে। তাদের কাব্য পাঠে দেখা যায় তারা বেমালুম আরবি ফার্সি শব্দাবলি ব্যবহার করেছেন। এতে যুক্তিসঙ্গতভাবেই অনুমান করার কারণ রয়েছে যে, তখনকার দিনে এদেশীয় মুসলিম সমাজে এ দেশীয় ভাষা ছিল জীবন্ত। যেহেতু এ সকল কবিদের সংখ্যক লোকেরাই ছিলেন পল্লিবাসী; এজন্য তাদের পক্ষে আরবি বা ফার্সি লেখক বা অভিধান সামনে রেখে কাব্য রচনা করা সম্ভবপর ছিল না। অপরদিকে যদিও হিন্দুসমাজে আরবি ফার্সির এরূপ চর্চা ছিল না, তবু দীর্ঘকাল ফার্সিকে রাজভাষা হিসাবে গ্রহণ করার ফলে তাদের কথ্য ভাষায় অনেক আরবি ফার্সি শব্দাবলি প্রবেশ লাভ করেছিল। ১৭৫৭ সাল থেকে এদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সূচনা থেকে ১৯৪৭ সালে এদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পূর্বপর্যন্ত যেভাবে নানাবিধ ইংরেজি শব্দ আমাদের কথ্য ভাষায় বা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে, তেমনি মুসলিম সুলতানদের দীর্ঘ পাঁচশ’ বৎসরের রাজত্বকালে অসংখ্য আরবি ও ফার্সি শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে। এখনও পুরাতন দলিল দস্তাবেজের ভাষা পাঠ করলে বোঝা যায় তখনকার দিনের বাংলা ভাষার পূর্বোল্লেখিত কত শব্দের প্রয়োগ রয়েছে।
ইংরেজরা অত্যন্ত চতুর জাতি হিসাবে রাজ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন ধারার পরিবর্তন করেনি। ধীরে ধীরে তাদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এক একটা করে নতুন ব্যবস্থার প্রয়োগ করে এদেদেশীয় মুসলিম সমাজকে পর্যুদস্ত করেছে। সর্বপ্রথমে ১৭৬৩ সালে দিল্লির নামেমাত্র বাদশাহ শাহ আলমের নিকট থেকে দেওয়ানীর সনদ গ্রহণ করে মুসলিম আমলাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়, তাঁর ফলে বাদশাহী আমলের রাজস্ববিভাগের লোকদের অপসারণ করে তাদের স্থানে হিন্দু কর্মচারী ও আমলা নিয়োগ করে একটা মস্ত বড় শ্রেণীকে বেকার করে ফেলে। তার অব্যবহিত পরে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার প্রবর্তন করে আবার মুসলিমদের জীবনে ভীষণ সংকটের সৃষ্টি করে । বাদশাহী আমলে জমিদার বা চৌধুরীগণ জমির মালিক ছিলেন না। তারা ছিলেন সরকারে অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র। জমিদারগণ এক বা একাধিক পরগণার শাসন নির্বাহ করতেন। চৌধুরীগণ ছিলেন কর আদায়কারী অফিসার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ পুরুষানুক্রমে জমির মালিক হয়ে পড়েন।
লর্ড কর্নওয়ালিশের শাসনকালে তার অধীনস্থ আমলা মুসলিমদের নানাভাবে পর্যুদস্ত করার উদ্দেশ্যে জমিবন্দোবস্ত দেওয়ার সময় হিন্দুদের নামেই অধিক তালুক বন্দোবস্ত দিয়েছেন। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সুলতানী আমলে মুসলিম জমিদারদের কর্মচারী কোম্পানি আমলে মুন্সি বেনিয়া বা মুৎসুদ্দি। তার ফলে পুরনো আমলের সরকারি আমলাদের যেমন পদচ্যুতি হয়, তেমনি সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে তাদের সর্বনাশ হয়। তবে কোম্পানি সরকার এখানেই থেমে যায়নি। ১৮৩৭ সালে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজিকে অফিস আদালতের ভাষা হিসাবে প্রবর্তন করে, মুসলিম আমলে যারা ফার্সি ভাষাভিজ্ঞ বা যারা ফার্সি-নবীস হিসাবে অফিস আদালতে যথেষ্ট উর্পাজন করতে সমর্থ ছিলেন, তাদের জীবনকে নিতান্ত অসহনীয় করে তোলে। ইংরেজদের এই দারুণ জুলুমের সর্বশেষ উদাহরণ দেখা দেয় ১৮৪৭ সালে Resumption বা বাজেয়াপ্ত আইন পাশ করার ফলে এ আইনের কবলে পড়ে মুসলিমদের বরাবরে সুলতানী বা নওয়াবী আমলে যতগুলো যায়গা, জায়গীর, চেরাগী বা ওয়াকফ সম্পত্তি ছিল তা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। এ বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি পরিশেষে হিন্দুদের বরাবরে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। ইংরেজ শাসকগণ কর্তৃক অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মুসলিমদের এভাবে নাস্তানাবুদ করার পূর্বে ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে তাদের সাংস্কৃতিক জীবনে চরম দুর্বিপাক দেখা দেয়। ফোর্ট উইলিাম কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল সদ্য নিযুক্ত ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা শেখাবার উদ্দেশ্য। এজন্য পণ্ডিত রামজয় তর্কালংকার, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালংকার এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আদর্শ পাঠ্য পুস্তক লেখার জন্য আহ্বান করা হয় । তারা কোম্পানি সরকারের নির্দেশক্রমে এমন সব পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেন যেগুলোকে অনুস্বর-বিসর্গবর্জিত সংস্কৃত ভাষার লিখিত পুস্তক বলা যায়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত সীতার বনবাস, কথামালা প্রভৃতি পুস্তকপাঠে এ বক্তব্যের সত্যতা সহজেই উপলব্ধি করা যাবে।
মুসলিম সমাজ এ ভাষাকে তাদের নিজস্ব ভাষা বলে গ্রহণ করেনি। তারা এতদিন পর্যন্ত যে ভাষার আওতায় লালিত পালিত হয়েছিল, সদ্যপ্রস্তুত ভাষার মধ্যে তার কোন দূর সম্পর্কও আর আবিষ্কার করতে পারেনি। কাজেই এ ভাষাই স্কুল কলেজের ছাত্রদের ভাষা হলেও তা বাঙালি হিন্দুদের ভাষা হিসেবেই এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকার লাভ করলো। যদিও এ ভাষার প্রতিবাদস্বরূপই প্যারীচাঁদ মিত্র, টেকচাঁদ ঠাকুরের ছদ্মনামে ‘আলালের ঘরের দুলাল’ ও ‘হুতুম প্যাঁচার নকশা’ বলে দু খানা সুখপাঠ্য পুস্তক লিখেছিলেন; তবুও তার ভাষা স্কুল কলেজের পুস্তকাদিতে কোন স্থান পায়নি। মুসলিম সমাজের লোকদের পক্ষে ইংরেজদের দ্বারা স্কুল কলেজ বর্জন করার স্থলে এ ভাষার বিভ্রাট ছিল এক কারণ। অপর কারণ ছিল তারা তাদের এ দুশমনদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকার জন্য ছিলেন বদ্ধপরিকর।
অবিভক্ত ভারতের বুকে দিল্লির সম্রাট বুলবনের শাসনকালে উর্দু ভাষার উৎপত্তি হয় । তার সভাকবি আমির খসরু ফার্সি ভাষার সঙ্গে দিল্লির চতুর্দিকে প্রচলিত সড়িবুলের যোগসাজস করে যে মিশ্র ভাষার সৃষ্টি করেন তাই ফলে শনৈঃ শনৈঃ বিকাশ লাভ করে, উর্দু ভাষায় পরিণত লাভ করে। যদিও বাদশাহী বা নওয়াবী আমলে উর্দু ভাষা রাজভাষার মর্যাদা লাভ করেনি, তবুও নানা অঞ্চলের প্রতিভাশালী লেখকগণের অবদানে সমৃদ্ধ হয়ে এ দেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই উর্দু ভাষা এক উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়। ইংরেজ শাসনের সূচনায় কোলকাতায় রাজধানী স্থাপিত হলে, অবিভক্ত ভারতের নানা অঞ্চল থেকে নানা ভাসাভাষী মুসলিম সমাজের লোকেরা নানা কর্ম উপলক্ষে কোলকাতাতে এসে বাস করতে বাধ্য হন। তারা একে অপরের ভাষা বুঝতে পারতেন না বলে, তাদের সাধারণভাষা Lingua Franca হিসাবে উর্দুকে গ্রহণ করেন । ফলে উর্দু তাদের মাতৃভাষায় পরিণত হয়।
অপরদিকে ফার্সি ভাষাকে স্থানান্তর করার ফলে মুসলিম সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা ফার্সির স্থলে উর্দুকে তাদের সংস্কৃতির ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে। কোলকাতায় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে মফস্বলের লোকদের পক্ষে কোলকাতার তমদ্দুনের অনুকরণ করা ফ্যাসানে পরিণত হয়, এজন্য একদিকে যেমন হিন্দুসমাজের লোকেরা কোলকাতার মুসলিমদের হাবভাব, ভাষা প্রভৃতির অনুকরণ করতে অভ্যস্ত হয়, তার ফলে বাংলাদেশের মধ্যে তৎকালীন মুসলিম প্রধান অঞ্চলের উঁচু মহলে রীতিমত উর্দু ভাষার চর্চা ও উর্দুতে পুস্তিকা প্রণয়নের প্রচেষ্টা দেখা দেয়। মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, মোমেনশাহী, সিলেট প্রভৃতি অঞ্চলের জেলা সদরে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত চালু ছিল।
একে নবগঠিত বাংলা ভাষার প্রতি মুসলিম সমাজের মোটেই আস্থা ছিল না, অপরদিকে মুসলিম সমাজের উঁচু মহলে উর্দুর চর্চা ব্যাপকভাবে দেখা দেওয়ায় নব গঠিত বাংলা ভাষার সমাদর মুসলিম সমাজে ছিল না। নওয়াব আব্দুল লতীফের মতো নেতাকেও বাংলা ভাষার প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করতে দেখা যায়নি। নওয়াব আবদুল লতীফেরা পরে যেসব জননেতা কর্তৃক মুসলিম সমাজ পরিচালিত হয়েছিল তাদের মানসেও এ দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল ছিল। ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহ্ তথা তার পরিবারের লোকেরা উর্দু ভাষাভাষী ছিলেন। এমন কি শের-ই-বাংলার ঘরোয়া ভাষা ছিল উর্দু। এঁরা সকলেই বাংলার চেয়ে উর্দু ভাষাকেই অধিকতর পছন্দ করতেন। এঁদের পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক ইংরেজি শিক্ষিত লোকদের মধ্যে অধিকাংশের ভার্নাকুলার ছিল উর্দু। সিলেটের মরহুম সৈয়দ আব্দুল মজিদ (খান বাহাদুর ও সি আই ই) তথনকার দিনে আসামে সর্বজনমান্য নেতা ছিলেন। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আইনের ডিগ্রিও লাভ করেছিলেন। তবে ডিগ্রি শ্রেণী পর্যন্ত ভার্নাকুলার হিসাবে তিনি উর্দুকে গ্রহণ করেছিলেন । ১৯১৯ সালে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমন্ত্রিত হয়ে সিলেট আগমন করলে বিপুল সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এ সংবর্ধনা সভার সভাপতি ছিলেন সৈয়দ আব্দুল মজিদ। তিনি তাঁর ভাষণ উর্দু ভাষায় পাঠ করেছিলেন। এতে স্পষ্টই বোঝা যায় নওয়াব আব্দুল লতীফের ঘোষণার পূর্বেই মুসলিম সমাজের মধ্যে একটা ভাগ দেখা দিয়েছিল। একদল উর্দুকেই তাদের ভার্নাকুলার হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। বাংলার প্রতি মুসলিম সমাজের ঝোঁক দেখা দেয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে। যদিও উঁচু মহলে বাংলার আদর ছিল না তবুও পল্লি অঞ্চলের মুসলিম কবিগণ পূর্বাপর বাংলার মাধ্যমেই তাদের মনের ভাব প্রকাশ করেছেন। তবে শহুর অঞ্চলে তাদের নামধাম সম্বন্ধে অনেকেই ছিলেন অজ্ঞ। এ পল্লি অঞ্চলের মুসলিম জনসাধারণকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যে যশোহরের বুকে পাদরি সাহেবগণ যে উৎপাত আরম্ভ করেন, তাকে প্রতিহত করর মানসে মুশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্ নব গঠিত বাংলা ভাষায় ছোট ছোট পুস্তিকা প্রণয়ন করতে থাকলে মুসলিম জনসাধারণের মনে আবার ইসলামের আলোক প্রতিভাত হয়। তার এ শুভ সূচনার পরে মীর মোশাররফ হোসেন ‘বিষাদ সিন্ধু’ নামক সুবিখ্যাত উপন্যাস রচনা করে। মুসলিম মনীষাকে বাংলা ভাষাপ্রবণ করে তোলেনা। এভাবে মরহুম মাওলানা আকরম খাঁ, মরহুম মাওলানা মনীর উজ্জামান ইসলামাবাদী, মরহুম মাওলানা আবদুল্লাহেল বাকী ও তাঁর ভাই মাওলানা আবদুল্লাহেল কাফী বাংলার মাধ্যমে ইসলামের নানাবিধ বিষয় পাঠকসমাজে পেশ করতে থাকলে ক্রমশ মুসলিমদের তথাকথিত অভিজাত মহলেও বাংলা ভাষা প্রীতি দেখা দেয়। তবে নজরুলের আবির্ভাবের পূর্বেপর্যন্ত বাংলা সত্যিকারভাবেই মুসলিমদের ভাষা কিনা এ সম্বন্ধে উচ্চ মহলে জমাটবাধা সন্দেহ ছিল।
কাজেই ভারত বিভাগের পরে কেবলই যে পশ্চিম দেশীয় মুসলিমেরা উর্দুকে এদেশের বুকে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল তা নয়, উর্দুর সমর্থক বাংলাদেশের মধে ও উপস্থিত ছিলেন। এঁদের বক্তব্য ছিল অবিভক্ত ভারতের বুকে যখন একটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, ভারতের সাধারণ ভাষা কোনটা? তখন কংগ্রেস তথা হিন্দুসমাজের সকল লোকই একবাক্যে বলেছিল হিন্দী। অপরদিকে মুসলিম সমাজের লোকেরা বলেছিল উর্দু। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সারা ভারতের রাষ্ট্রভাষা যদি হিন্দী হতে পারে তবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে না কেন? যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ নয় বলে উর্দুকে গ্রহণ করতে আপত্তি দেখা দেয় তাহলে অবিভক্ত ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা হিসাবে হিন্দীকে গ্রহণ করতে আপত্তির কারণ ছিল কি? তাদের অপর যুক্তি ছিল, দেশবিভাগ হয়েছে ধর্মীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে, কাজেই আরবি অক্ষরে লিখিত এবং ইসলামি ভাবধারায় বাংলা থেকে অধিকতর অনুরঞ্জিত উর্দু ভাষাকে প্রত্যাখ্যানের মূলে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করা ব্যতীত আর কি থাকতে পারে? তখনকার দিনে পাকিস্তানি শাসকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অত্যন্ত স্পর্ধার অধিকারী। এদের বাসনা ছিল ইংরেজরা যেভাবে এদেশ শাসন করে গেছে, তারাও ইংরেজদের উত্তরাধিকারী হিসাবে এদেশ শাসন করবেন। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে প্রকারান্তরে তাদের ভাষাই হবে। কাজেই শাসকের ভাষা হিসাবে মর্যাদা লাভ করলে, তাদের ছেলেমেয়েরা অবাধে সে ভাষার দক্ষতা অর্জন করে শাসিতের উপর প্রাধ্যান্য লাভ করতে পারবে।
তবে এদের এ যুক্তির ভিত্তিও সুদৃঢ় ছিল না। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে উর্দুর পার্শ্বে স্থান দান করলে ধর্মীয় ও জাতীয়তাবাদের মূলে কোন ফাটল দেখা দেওয়ার কারণ ছিল না। কারণ বিভিন্ন দেশে মুসলিম সমাজের লোকেরা অবস্থান করে বিভিন্ন ভাষায় কথা বললেও তাদের জীবনে আদর্শিক ঐক্যের ত্রুটি দেখা দেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই । কুরআন-উল-করীমের অক্ষরে উর্দু ভাষা লিখিত হলেও তা যে সর্বতোভাবে ইসলামি আদর্শেই গঠিত হয়েছ তাও বলা যায় না।
বাংলা ভাষাও ইসলামি আদর্শে গঠিত হতে পারে। কাজেই যারা ভাষা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং যারা এ আন্দোলনে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, তারা এ ভাষাকে তৃতীয় সংকট থেকে মুক্ত করেছেন। বাংলা ভাষার প্রথম সংকট দেখা দিয়েছিল সেন রাজাদের রাজত্বকালে। তারা কিছুতেই এ ভাষাকে যথাযথভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেননি। বাংলা ভাষার দ্বিতীয় সংকট দেখা দিয়েছিল, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে। পণ্ডিতদের হাতে এ ভাষা অস্বাভাবিক রূপ লাভ করেছে। বাংলা ভাষার তৃতীয় সংকট দেখা দিয়েছিল, যখন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করা থেকে বঞ্চিত হতে চলেছিল। যে দূরভিসন্ধি এ বাংলাদেশের বুকে উর্দুকে প্রতিষ্ঠিত করে মুসলিম সমাজেও তথাকথিত আশরাফ ও আত্রাফ শ্রেণী সৃষ্টি করে ও সমাজকে শ্রেণীবৈষম্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল, তাকে নস্যাৎ করেছেন বলেও সে আন্দোলনের হোতা এ আত্মদানকারীগণ আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র ।