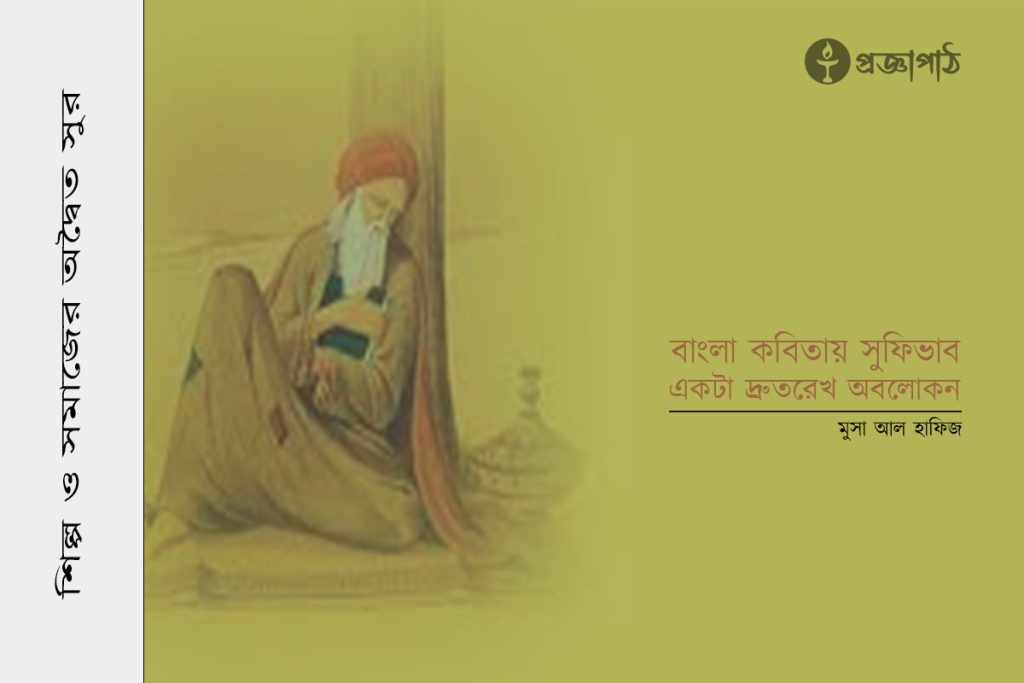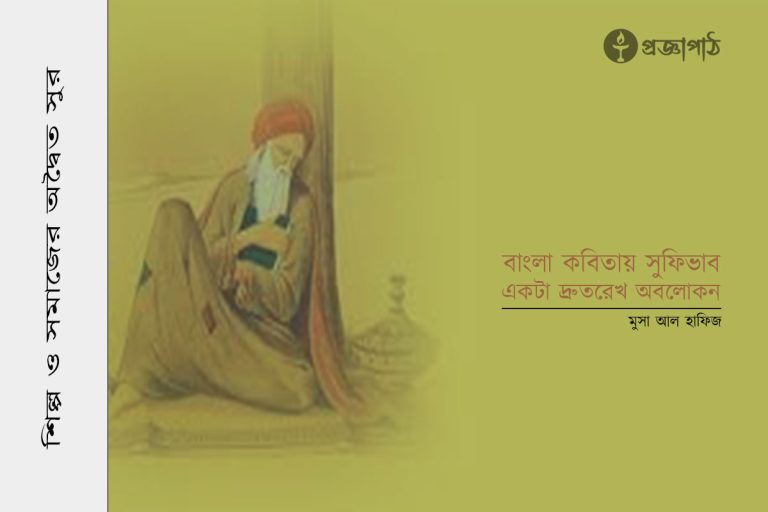কত রঙ্গ আর কত অনুষঙ্গ এই মহাবিশ্বে! কত রূপ আর কত রং এখানে। বিষাদে, বেদনায়, আনন্দে, উদ্দীপনায় জীবন এখানে সচকিত। মর্মের গূঢ়তা ছড়িয়ে আছে জন্মে, মরণে, জয়ে ও লয়ে। জীবনের যাপনে ও বিস্তারে, সঙ্কটে ও নিস্তারে নিয়ত কথা বলছে ঐশ্বরিক চেতনা। নিখিলের সৌন্দর্যময় মুখ, আলো-কালোর রহস্য, উত্থান ও পতন এবং জীবনের বিচিত্র ধারা ও ধরনে গূঢ়তত্ত্বের অমোঘ লীলা বহমান, যা রূপে-অরূপে, ধরায়-অধরায় বিম্বিত ও মন্ত্রিত। এর রূপ রস, ব্রীড়া ও বিভাকে কীভাবে উপেক্ষা করতে পারে কবিতা?
জীবনের স্বাভাবিকতার ভেতরে যে ছন্দ, মানুষের জীবনে যে অর্থ, সেই ছন্দ ও অর্থ বিপন্ন হলে কবিতা প্রাণদ অভিসারে উজ্জীবন পায়? সে তখন হয় ‘বিচিত্র ভঙ্গুর শব্দচূর্ণের উদ্যমহীন সমস্বর।’ এই যে জীবনের ভেতরতল, এই যে আবেগের নিবিড় ভাষা, এই যে অর্থের নিশ্চিত উদগতি, এর ভাবশৃঙ্খলাকে মিস্টিসিজম তথা অতীন্দ্রিয়বাদ বা মরমিবাদ নামে ডাকি বা না ডাকি, জীবনের সে সত্য।
এই সত্য স্রষ্টার অস্তিত্বে ও উপস্থিতিতে বিশ্বাস করে, তাঁর কর্ম, শৈলী ও প্রভুত্বের প্রজ্ঞায় আস্থা রাখে। বিশ্বসাহিত্যে আধ্যাত্মিক কবিতার রয়েছে বহুবিচিত্র স্রোত। প্রতিটি ভাষা ও অঞ্চলে তার সদর্থ উচ্ছলিত। মুসলিম বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের সুফি কবিতা এ ধারার প্রধান এক বৈশ্বিক প্রবণতা। সুফি কবিতা জীবনের স্বরূপ উন্মোচনে মানুষ ও বিশ্বের আত্মগত বহুস্তর রহস্যের স্বাদে পাঠক হৃদয়কে মথিত করে তোলে। প্রেমশীলতা ও মন্ময়তার ব্যাকুলতায় এমনসব গূঢ় কথনে সে কবিতার শরীর ও আত্মায় সাড়া তোলে, যা সীমার মাঝে অসীমার তৃষ্ণা, উন্মুখিত ও সান্নিধ্যে আমাদের পুলকিত করে, জাগ্রত করে। আত্মতত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্বের দিব্যউন্মোচনে সত্যযাপনের হৃদয়জ অভিজ্ঞতায় উপলব্ধিকে স্নাত করে সুফিবাদ দেয় মানব মুক্তির পথের প্রস্তাব। কবিতাকে সে সরবরাহ করে এক অভিমুখ, যা মানুষ ও মহাজগতের মন ও হৃদয়কে চায় বুঝতে ও আস্বাদন করতে এবং এর সারসত্যকে করে বয়ন ও বয়ান। এতে ধ্যানশীল কল্পনা বিশ্বাত্মার সাথে যোগাযোগসেতু গড়ে দেয় এবং যা হয় জীবন্ত। প্রেমের যে পরম ভাষা, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, ব্যক্তিতে-নিখিলে এবং ব্যক্তি, নিখিল ও পরমসত্তায়, তারই ভাবকল্পনার ভাষিক উন্মোচন সুফিকাব্যের স্বভাব। এ স্বভাব গড়ে দেয় ইসলামের মরমিতত্ত্ব। যার কেন্দ্রীয় অভিপ্রায় খোদাপ্রাপ্তি। নিজের প্রবৃত্তি, আবেগ ও বুদ্ধিবৃত্তির অসুস্থতা-অসততাকে পরাজিত করে জীবনের শুদ্ধ, স্বচ্ছ ও কল্যাণী পবিত্রতায় অবগাহনের নিরন্তর এক লড়াই সুফিতত্ত্বের অভিপ্রায়, যা মানবকে করবে পরম মোক্ষের যোগ্য। আত্মপুজা, কাম, লোভ, মোহ, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা, ক্রোধ, ঘৃণা, ঈর্ষা, দ্বেষ, ভয় ইত্যাদিকে পরাজিত করে খোদাভীতি, ইবাদত, সংযম, ত্যাগ, দয়া, অনুকম্পা, প্রেম, শুভবাদ, কৃতজ্ঞতা, বিনয়, সৃষ্টিসেবা, আত্মশাসন, সম্ভ্রমশীলতা, সত্যবাদিতা, পরমের ধ্যান ইত্যাদি গুণের সমাহারে ব্যক্তিত্বের পুনর্গঠন এবং আত্মমুক্তি ও আত্মউন্নয়নের এক অবাধ-অগাধ পরিক্রমা রয়েছে সুফিসাধনার ধারায়।
এর যে দার্শনিক-নৈয়ায়িক মূল্য ও আবেদন, তার ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি নানা চরিত্রে মর্মরিত বিশ্বের প্রচলিত সব ভাষার সাহিত্য, বিশেষ করে কবিতা ও গানে।
সুফিবাদের সাথে সাক্ষাত ঘটেনি, বাংলা সাহিত্যের আদি পর্বের। কিন্তু সুফি বিষয়াবলীর সাথে চর্যার পদসমূহের ছিলো দূরান্বয়ী আত্মিয়তা। সেখানে মূলত বৌদ্ধ ধর্মের গূঢ় সাধন প্রণালী ও দর্শন-তত্ত্ব কুহকময় রূপকে, আভাসে, ইঙ্গিতে ভাষা লাভ করেছে। সেখানে ভাব ও অনুভূতি ধর্মের মরমী বোধের আশ্রয়ে দুর্বোধ্য ও কুয়াশাচ্ছন্ন ভাষা ও প্রকরণে ব্যক্ত হয়েছে। যা মূলত গীতিময়তার মধ্য দিয়ে লীলায়িত। এরপর উন্মেষের পরবর্তী লগ্নে ইসলামের আধ্যাত্মিক আবেদনের সাথে বাংলা ভাষার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। যার অস্পষ্ট- অস্বচ্ছ অভিব্যক্তি রয়েছে হলায়ুধ মিশ্র (১২ শতক) রচিত সেখ শুভোদয়ায় বিবৃত বাংলা গানে এবং এর সমধর্মী পীরমাহাত্ম্যসূচক ছড়া বা আৰ্যায়, প্রেমসঙ্গীতে। সেখশুভোদয়ার অধিকাংশ গল্পে একদিকে অলৌকিক ক্ষমতা ও আধ্যাত্মিক মহিমার অধিকারী শেখ শাহজালালের (র) চরিত্রগৌরব ঘোষিত, অন্যদিকে রয়েছে মসজিদ, খানকাহ প্রতিষ্ঠা ও মানবপ্রেমের পথ ধরে ইসলাম প্রচারের ইতিকথা। মানুষকে নীতি-উপদেশ শিক্ষা দেওয়ার জন্য গল্পের মাঝে মাঝে রয়েছে কতিপয় জ্ঞানগর্ভ শ্লোক। রামাই পন্ডিতের (১৩ শতক) গাঁথাজাতীয় রচনা শূন্যপুরাণেও মুসলিম সংস্কৃতির সাথে পরিচয় ঘটে বাংলা সাহিত্যের। বৌদ্ধদের ওপর বৈদিক ব্রাহ্মণদের অত্যাচার, উদ্ধারকর্তা হিসেবে মুসলমানদের জাজপুর প্রবেশ ইত্যাদি ঘটনার বর্ণনাসম্বলিত ‘নিরঞ্জনের রুম্মা’ শীর্ষক কবিতা আল্লাহ,পয়গাম্বর, পীর, ইবাদত, মওলানা ইত্যাদির সাথে ভাষার সাহিত্যিক যোগসূত্র নির্মাণ করে। অতৎপর বাংলা সাহিত্যের বিকাশের প্রধান যে স্রোত; বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গল সাহিত্য এবং অনুবাদ সাহিত্য, তাতে পড়ে ইসলামী জীবনদৃষ্টির সেই অভিঘাত, যার ফলে বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্রিয় বিষয় হয়ে ওঠে মানুষ, যাপনশীল মনুষ্য জীবন ও মানুষের পৃথিবী। আগে যে গুরুত্বে অধিষ্ঠিত ছিলো দেব-দেবী, অলৌকিকতা, কুসংস্কার ও অপবিশ্বাস।
মালাধর বসুর (১৫শ-১৬শ শতক) শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও তাঁর পরবর্তী পাঁচালি কাব্যের ধারা, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি অনুবাদকাব্য, সত্যপীরের মহিমা প্রচারে রচিত বিদ্যাসুন্দর কাহিনী কেবল মুসলিম শাসনের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত, তা নয়। বরং এ পৃষ্ঠপোষকতার গোড়ায় ছিলো ভাষা ও জ্ঞানসম্পদের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি। চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) আবির্ভাব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত প্রচার সুফিবাদের বৈষ্ণব-আত্মীকরণের মধ্য দিয়ে নিশ্চিত হয়। এরপর বাংলা সাহিত্যের নতুন দিক উন্মোচিত হয় এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বৈষ্ণব আন্দোলনের সাথে সুফিবাদের প্রকৃতিগত মিল শুধু ছিলো তা নয়, মিল ছিলো প্রবৃত্তিগতভাবেও। প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮–১৯৪৬) ঠিকই লিখেছেন ভারতবর্ষের মধ্যযুগের এই নববৈষ্ণব ধর্ম অর্থাৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম সনাতন হিন্দু ধর্মের একটি নব শাখা মাত্র, তবে এই নবত্বের কারণ মুসলিম ধর্মের প্রভাব। এ ধারার কবিরা তো বটেই, অন্যান্য হিন্দু কবিদের মধ্যে ফারসিবাহিত ইসলাম ও সুফিপ্রভাব এক বাস্তবতায় পরিণত হয়। যার অন্যতম নজির অষ্টাদশ শতকের প্রধান কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (১৭১২–১৭৬০। হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামের রামচন্দ্র মুন্সীর কাছ থেকে ফারসি ভাষা রপ্ত করেন তিনি। সত্যপীরের পাঁচালি বা সত্যনারায়ণের পাঁচালি রচনার মধ্য দিয়ে কাব্যে তার উত্থান হয়। যেখানে মুসলমানী বাংলার উজ্জ্বল নিদর্শন প্রতিফলিত। এর বিষয়বয়নে রয়েছে মঙ্গলকাব্য ও সুফিকাব্যের মিলিত সংরাগ।
সুলতানি আমলে কাহিনীকাব্য বা রোম্যান্টিক কাব্যধারার প্রবর্তনে মুসলিম কবিরা মূলত আবুল কাশেম ফেরদৌসী (৯৪০-১০২০), নেযামী গঞ্জাবী (১১৪১-১২০৯), শেখ আবু মুহাম্মদ মুসলেহুদ্দীন সাদী (১২১০-১২৯১), আমীর আবুল হাসান ইয়ামিনুদ্দীন খসরু (১২৫৩-১৩২৫), জালালুদ্দীন মুহাম্মদ রুমী (১২০৭– ১২৭৩), হাফিজ শামসুদ্দীন সিরাজী (১৩২৫-১৩৮৯/৯০), আবদুর রহমান জামীর (১৪১৪-১৪৯২) মতো সুফিকবিদের দ্বারা প্রণোদিত ছিলেন। কাহিনীকাব্য ও ধর্মীয় সাহিত্যের পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়মূলক সাহিত্য, চৌতিশা, জ্যোতিষ, এলিজিকাব্য ও সঙ্গীতশাস্ত্রীয় কাব্যে এ প্রভাব পরিকীর্ণ।
শাহ মুহম্মদ সগীরের (১৪ শতক) ইউসুফ-জুলেখা ছিলো আবদুর রহমান জামীর ইউসুফ ও জুলাইখা মহাকাব্যের ভাবানুবাদ। জামীর গ্রন্থে সুফিপ্রেমের আত্মাকে ব্যক্ত করা হয়েছে মানবীয় প্রেমকাহিনীর পটভূমিতে। সুলতান ইউসুফ শাহের (১৪৭৪-১৪৮১) সভাকবি জৈনুদ্দীনের রসুলবিজয়, মুজাম্মিলের (১৫ শতক) সায়ানামা, সুলতান হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) নবদ্বীপের কাজী চাঁদ কাজীর বৈষ্ণব পদ, নাসিরুদ্দীন নসরত শাহের (১৫১৯-১৫৩৩)কর্মকর্তা শেখ কবীরের পদাবলি, আফজাল আলীর নসিহতনামা (১৬৬২ খ্রিস্টাব্দের দিকে রচিত), সাবিরিদ খানের (১৬ শতক) বিদ্যাসুন্দর, রসুলবিজয় এবং হানিফা ও কয়রাপরী, দোনাগাজীর (১৬শতক) সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামান, শেখ ফয়জুল্লাহর (১৬ শতক) গাজীবিজয়, সত্যপীর ইত্যাদি সুফিতত্ত্বে মর্মরিত এবং সুফিবাদে উজ্জীবিত কাব্যপ্রয়াস। দৌলত উজীর বাহরাম খার (১৬ শতক) লায়লী-মজনু (রচনাকাল : আ. ১৫৬০-১৬৭৫) সুফিকবি আবদুর রহমান জামীর ফারসি ভাষায় রচিত মহাকাব্য লাইলি ওয়া মজনু-এর ভাবানুবাদ। এতে মূলত রূপকে বিবৃত হয়েছে পবিত্র প্রেমের বাখান। সৈয়দ সুলতানের (আনু. ১৫৫০-১৬৪৮) ইবলিসনামা, মারফতি গান উজ্জল সৃষ্টিকর্ম। তার জ্ঞানপ্রদীপ ও জ্ঞান চৌতিশাকাব্যে রয়েছে খোদাতত্ত্ব, সাধনা-উপাসনা, আত্মসন্ধান, জিকির ইত্যাদির অনুপুঙ্খ বয়ান। মুহম্মদ কবীরের (১৬ শতক) মধুমালতী (রচনা ১৫৮৮), শেখ পরানের (আনু. ১৫৫০-১৬১৫) নূরনামা, নসিহৎনামা, আবদুল হাকীমের (আনু. ১৬২০-১৬৯০) নূরনামা, দৌলত কাজীর (আনু. ১৬০০-১৬৩৮) সতীময়না, আলাওলের (আনু. ১৬০৭-১৬৮০) হপ্তপয়কর, তোহফা, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল ও সিকান্দরনামা ইত্যাদি সুফিজারকরসে বিধৌত ও বিগলিত।
এসব রচনা মনন ও সৃজনশীলতার দ্বিবিধ ধারায় ছিলো প্রসারিত। শাস্ত্রীয় গ্রন্থও ছিলো অনেকগুলো, যা রচিত হয় কাব্যে। সুফিচেতনাজাত এসব রচনা সৃষ্টিতত্ত্বকে অলিঙ্গন করেছে, ধ্যানশীলতাকে উদযাপন করেছে, এর বীধি ও ঐতিহ্য বয়ান করেছে, মূল্যতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব এবং জন্ম-মৃত্যুর রহস্য সন্ধানে থেকেছে উন্মুখ।
জীবনময় উত্থান-পতনের ঘনঘটা, সুখের পরশ ও আতিশয্যের ভ্রান্তি, দুঃখের যাতনা ও ব্যর্থতার দহন, হতাশা ও পরাজয়ের বিকার, সহজ-স্বাভাবিক জীবনপন্থা, সুখের উপায় ও চিরসুখের ঠিকানা, সত্যউপলব্ধির স্বরূপ এবং ধর্মের বাহ্য অর্থের পর্দা উন্মোচন করে তত্ত্ববাণী ও সাধনার ইশারাকে প্রায়ই লৌকিক ও অপরিশীলিত উপায়ে উপস্থাপন করেছে তখনকার কবিতা। বিচিত্র হেঁয়ালি এসব কাব্যের চরিত্রে যুক্ত থেকেছে। সাধনার পথ ধরে জীবনের স্বরূপ উপলব্ধিতে বিশ্বাসী ছিলেন সুফিবাদে সমর্পিত কবিগণ! কিন্তু সুফিজ্ঞান ও তত্ত্ব লোকজ প্রথা ও কাহিনীর স্বেচ্ছাচারে প্রায়ই থেকেছে ম্রিয়মান। রহস্য তৈরির অবাধ প্ৰয়াস বাস্তবতাবোধের প্রতি করেছে উপেক্ষা। রসঘন এসব কাহিনী রূপ ও প্রেম- আনন্দকে রূপকাশ্রয়ে ব্যক্ত করেছে নানা মেজাজে। এরই মধ্যে খেলে গেছে মানব-মানবী এবং প্রেমিক ও পরমের নিত্য বিরহমিলনের লীলা-বৈচিত্র্যের হিন্দোল। যা লৌকিক পথ ধরে অলৌকিক রসস্বরূপ পরমের অনুভূতিকে মানব হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে চেয়েছে। শক্তি ও সীমাবদ্ধতার সঞ্চারি বাস্তবতার মধ্যে শাহ সগীর থেকে দৌলত উজির, আলাওল হয়ে যে দীর্ঘ কাব্যপরিক্রমা, তাতে অনেকগুলো শক্তিমান, শিল্পঋদ্ধ ও জীবনরসে সজীব কাব্য উপহার দিয়েছেন সুফিবাদলগ্ন কবিরা। বাউল তথা যোগী-ফকিরদের উপর পড়েছে সুফিবাদের প্রভাব। গুহ্যসাধনা ও প্রেম তাদের অবলম্বন। প্রেমভিত্তিক ধ্যান-সাধনা, দেহতত্ত্ব ও নাড়িজ্ঞান তাদের ভাব ও কর্মে রেখেছে গভীর ছাপ।
যাদেরকে বলা হয় বে-শরা ফকির, লালন সাঁই (১৭৭৪-১৮৯০) তাদের পরম গুরু। লালনপন্থীরা বীর্য বা শরীরী সাধক, তারা সন্ধান করেন মানবশরীরে লুকিয়ে থাকা সহজ মানুষ বা অচিন মানুষকে। দেহের ভেতরে বসবাসকারী বস্তু বা ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়ার বাউল অনুধ্যানে সুফি সাধকদের স্রষ্টা ও সৃষ্টি, আশেক ও মাশুকের মধ্যেকার মিলনের আকাঙ্ক্ষার মিল দেখেন অনেকেই। তবে আল্লাহর প্রতি সুফি ভালোবাসা মূলত অশরীরী ভালোবাসা। যার পথ ও প্রক্রিয়া কুরআন-সুন্নাহ থেকে উৎসারিত।
এখানকার মাটি ও মানুষ এবং প্রাকৃতিক বিন্যাসের মধ্যে সুফিবাদ লোকজ অনুশীলনে একটি নতুন চারিত্র্য লাভ করে। এখানকার লোকধর্ম, বৌদ্ধ তান্ত্রিক, বৌদ্ধ সহজিয়া এবং বেদান্তবাদীদের আচরিত নানা উপাদানের সাথে সুফিভাবনা একাকার হয়ে ক্রমান্বয়ে ভাবের সম্মিলন ও সমন্বয়ের ধারাবাহিকতায় জন্ম নেয় বাউল ধারা। যা মূলত লোকায়ত এক দর্শন।
সুফিবাদের যে বিকৃতি শরীয়াকে অবজ্ঞা করে, স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং রব ও বান্দার ভিন্নতাকে কবুল করে না, তার প্রভাব বাউল ভাবনায় পড়েছে অধিক- মাত্রায়। লালন বলেন—“আলেফে আল্লাজি, মিম মানে নবি/লামের হয় দুই মানে/এক মানে হয় শরায় প্রচার/আরেক মানে মারফতে।”
শরীয়ার বিধানকে উপেক্ষা করে বাউলপন্থা। “মারফতি ধ্যানধারণার প্রতিষ্ঠানবিরোধী ও অন্তর্ঘাতমূলক প্রবণতাই তাঁদেরকে বেশি আকর্ষণ করেছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তাঁদের গোটা বিশ্বাসের জগতটাই ছিল শরীয়তী রীতিনীতির বিপক্ষে।” লালন বলছেন— “শরাকে সরপোষ লেখা যায় / বস্তু মারফত ঢাকা আছে তায়/সরপোষ থুই তুলে কি দেই ফেলে লালন বস্তু- ভিখারী।”
নবীজীর প্রতি ভক্তি নিবেদনে লালন ছিলেন অকৃপণ। কিন্তু এ ভক্তির মধ্যে গুপ্তপথ ছিলো তার অন্বিষ্ট। লালন বলেন—
“তরীক দিলে নবিজী জাহের বাতেন
যেথা যোগ্য লোক জেনে
সে রোজা আর নামাজ ব্যক্ত এহি কাজ
গুপ্ত পথ মেলে ভক্তির সন্ধানে।”
হাসন রাজা (১৮৫৪-১৯২২) ছিলেন মরমী সাধক। সর্বমানবিক ধর্মীয় চেতনার এক লোকায়ত ঐকসূত্র রচনা করেন তিনি। তাঁর গানগুলো মনের মাঝে জন্ম দেয় সঞ্চারি আধ্যাত্মবোধ। জমিদার হাসন রাজা যখন বলেন- “লোকে বলে, বলেরে ঘরবাড়ি ভালা না আমার।/ কি ঘর বানাই আমি শূন্যেরও মাঝার। কিংবা ‘রূপ দেখিলামরে নয়নে/দেখিলামরে আপনার রূপ/আমার মাঝত বাহির হইয়া দেখা দিল মোরে’, অথবা আঁখি মুঞ্জিয়া দেখ রূপ রে,আঁখি মুঞ্জিয়া দেখ রূপ/আর দিলের চক্ষে চাইয়া দেখ বন্ধুয়ার স্বরূপ,
তখন এমন এক ভাবুকের চেহারা ভেসে উঠে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যার চিন্তা ঘোষণা করছে “ব্যক্তি স্বরূপের সহিত সম্বন্ধ সূত্রেই বিশ্ব সত্য”।
বাংলা কবিতায় আধুনিকতার অন্যতম কাণ্ডারি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪–১৮৭৩ )। তার বীররসের গভীরে আত্মার আর্তি উচ্চারিত, রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় ঘিরে রচিত তার ব্রজাঙ্গনা বৈষ্ণব পদাবলীর তুল্য মরমী আকুলতার “চিরস্থির নীর” বইয়ে দিতে চায় “জীবন নদে!” তার ‘আত্ম-বিলাপ’ উচ্চারণ করে চিরায়ত মরমী জিজ্ঞাসা—
“আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবী মনে?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন হীনবল দিন দিন, –
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? এ কি দায়!
রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি?
জাগিবি রে কবে?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কত দিন রবে?”
তার ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ উচ্চারণ করে জন্মিলে মরিতে হবে/ অমর কে কোথা কবে/চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে? এর প্রভাব মরমীচিত্তের আর্তনাদ ও হাহাকার হয়ে পাঠকের মনে মন্ত্রিত হয়।
মাইকেল তার জনমভূমি সাগরদাঁড়ির নিকটবর্তী শেখপাড়া গ্রামে জনৈক মাওলানা সাহেবের কাছে গিয়ে ফারসি শিখতেন। শুনতেন পারস্যের কবিদের মনমাতানো গজল। সেখান থেকেই কবিতা তাকে আচ্ছন্ন করতে শুরু করে। পরিণত পর্যায়েও ফার্সী তাকে আসক্ত করে রাখে। ফলে দেখি, ১৮৪৪ সালে কলিকাতার Circulator পত্রিকায় তার ইংরেজি অনুবাদে প্রকাশিত হয় শেখ সা’দীর গজল। ODE নামে প্রকাশিত এ গজল দিয়েই শুরু হয় তাঁর ইংরেজি সাহিত্যচর্চা।
মাইকেল ছিলেন মুসলিম সাহিত্য ও শিল্পকলার শুভার্থী ও রসজ্ঞ। জালাল উদ্দিন রুমীর কবিতাকে ইষৎ পরিবর্তন করে তিনি লিখেন বিখ্যাত ‘রসাল ও স্বর্ণলতিকা”। ১৮৬১ সালে রচিত তাঁর বিখ্যাত আত্মবিলাপ এ আছে শেখ সা’দীর নালায়ে ইয়াতিমের প্রতিধ্বনি। তিনি ইংরেজি, গ্রীক, ল্যাতিন, ফরাসি ইত্যাদি ভাষা জানতেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় আধুনিকতার প্রবর্তক এ কবি ফার্সি কবিতার ঐতিহ্য ও মর্মবাণীকে দেখতেন ভক্তের নজরে। তিনি আক্ষেপ করেছেন, মুসলমানরা বাংলা ভাষায় কারবালার মতো উপাখ্যান নিয়ে কেন রচনা করেনি কোনো মহাকাব্য ?
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) আধ্যাত্মিকতার মূলে আছে বিশ্ব নিয়ন্ততার প্রতি বিশ্বাস। ‘সীমার মাঝে অসীম তুমি/ বাজাও আপন সুর/ আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ/তাই এত মধুর।’ জোড়াসাকুর ঠাকুর পরিবারের ভাবসাধনা, রবীন্দ্র-পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) ফার্সিকাব্য সংযোগ, উপনিষদ এবং ব্রাহ্মসমাজ ও রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) প্রভাব রবীন্দ্রমনে আধ্যাত্মিক যে আনন্দলোক তৈরি করে, তা ব্রাহ্মমতের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলো বৈদিক মন্ত্রের আত্মাকে। কিন্তু বৈদিক আচারের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলো বেদান্তবাদী হৃদয়ের ধর্মকে।
‘বৃথা আচার বিচার। সমাজের চেয়ে হৃদয়ের নিত্য ধর্ম সত্য চিরদিন।’
হৃদয়ের ধর্মের অন্বেষা পরম সত্তা। যিনি সব মানুষের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট থেকে মহত্ত্বের শ্রেয়োবোধের প্রেরণা দিচ্ছেন। চিত্রার ‘এবার ফিরাও মোরে’ কবিতায় তার পরিচয় আছে। ‘কে সে? জানি না কে? চিনি নাই তারে শুধু এইটুকু জানি তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর -পানে ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে অন্তর প্রদীপখানি।…’
রবীন্দ্রনাথের ভাবুকতা গভীরভাবে উজ্জীবিত ও বিনির্মিত ছিলো ফারসি ও হিন্দি কবিতার সুফি ভাবরসে। শেখ সাদী, হাফিজ বা রুমী প্রতিধ্বনিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। সুফিবাদের মন, তার অপার্থিব মিলনতিয়াস এবং পরমানন্দময় ভাবাবেশের প্রতি রবীন্দ্রনাথ কতো গভীরভাবে আসক্ত ছিলেন, তার বিবৃতি নিজেই দিয়েছেন পারস্য-যাত্রী সফরনামায়।
সর্বোপরি এর জ্বলন্ত স্বাক্ষর রয়েছে কবিতায় কবিতায়। আমরা পাঠ করতে পারি রবীন্দ্রনাথের কবিতা:
“ছিন্ন ক’রে লও হে মোরে,
আর বিলম্ব নয়।
ধুলায় পাছে ঝ’রে পড়ি
এই জাগে মোর ভয় ।
এ ফুল তোমার মালার মাঝে
ঠাঁই পাবে কি জানি না যে,
তবু তোমার আঘাতটি
তার ভাগ্যে যেন রয়।
ছিন্ন করো, ছিন্ন করো,
আর বিলম্ব নয়।
কখন যে দিন ফুরিয়ে যাবে—
আসবে আঁধার ক’রে,
কখন তোমার পূজার বেলা
কাটবে অগোচরে।”
(গীতাঞ্জলি: গীত সংখ্যা ৮৭)
“পাশাপাশি হাফিজের এই কবিতাটি পড়ুন :
মিলনের বারতা কোথা? আমায় ঊর্ধ্বে নেবে ডেকে-
বরণ করতে তোমায়, ধুলোর ধরা ছেড়ে যাব ঊর্ধ্বলোকে!
প্রাণ আমার নীড় চেনা সেই পাখির মতো স্বর্গ কামনায়,
ধরার ফাঁদ এড়িয়ে কেবল ঊর্ধ্বপানেই ধায়।
ডাকবে যখন প্রণয় স্বরে তোমার চরণসেবায়,
সুদূরপানে উঠবো ফেলে ক্ষণ কালের সীমায়
বাধা জগৎ-সংসার আর নশ্বর এ জীবন;
হে প্রভু! তোমার করুণা মেঘ হতে করো বর্ষণ। ”
(সৈয়দ শামসুল হক অনূদিত)
রবীন্দ্রনাথ লিখেন :
“গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি,
বাদল-জল পড়িছে ঝরি ঝরি
এ ঘোর রাতে কিসের লাগি
পরান মম সহসা জাগি
এমন কেন করিছে মরি মরি।”
সুফি কবি শেখ সাদী লিখেছিলেন :
“মেঘ থেকে এক বিন্দু বারি পড়ে ঝরে
সাগরের বিশালতা দেখে সে লাজে বুঝি মরে :
কী অসীম এ সাগর আর আমি কত হীন!
যেথায় এ সাগর বিরাজে আমি সেথা লীন।”
(সৈয়দ শামসুল হক অনূদিত)
হাফিজ বা রুমীর সাথে রবীন্দ্রনাথের নানা কাব্যের মিল এত প্রগাঢ় ও প্রখর, যা খোলা চোখেই ধরা পড়ে। মিলগুলো চিত্রনির্মাণের ধারা ও ধরণে, কাব্য- স্থাপত্যের বৈচিত্রে, গতিবিধির বর্ণিলতায় এবং গভীরতার সংগঠনেও সক্রিয়।
পারস্যে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন “আপনাদের পূর্বতন সূফীসাধক কবি ও রূপকার যাঁরা, আমি তাঁদেরই আপন, এসেছি আধুনিক কালের ভাষা নিয়ে।” সেই যে তাদের সখা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে ব্যক্ত করলেন, তার কবিতা সেটা করে আর বেশি। সেখানে রবীন্দ্রনাথের মনোলোকে গভীর শেকড় পেতে সুউচ্চ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সুফিবাদ ও ব্রাহ্মবাদ। যদি সেই সব মহান কবির সাথে রবীন্দ্রনাথের মিল সন্ধান করা হয় তাদের অলৌকিক জ্যোতির্ময়তাকে বাণীদান, রস, রসাবেগ, রসবোধ ও চিত্তের বেদনা এবং মহত্ত্বের অধিষ্ঠানে একে অন্যকে প্রতিফলিত করণের দিক থেকে, তাহলে বহু ক্ষেত্রে হাফিজ- রুমী থেকে রবীন্দ্রনাথকে আলাদা করা কঠিন হবে খুবই। যেভাবে হুসাইন ইবনে মনসুর হাল্লাজের ( (৮৫৮- ৯২২)পরমের সাথে একাত্মবোধের আনাল হক জাতীয় কাব্য থেকে আলাদা করা কঠিন হয় রবীন্দ্রনাথের উচ্চারণকে, যখন তিনি বলেন—
“তুমি আর আমি/মাঝে কেহ নাই/কোনো বাধা নাই ভুবনে।”
কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬ ) মনেও আলোকসম্পাত করেন সুফি আধ্যাত্মিক কবি খাজা শামসুদ্দীন মুহম্মদ হাফিজ-ই-সিরাজী ও জালালুদ্দীন রুমী। হাফিজে তিনি আসক্ত হন কবিতার ভোরবেলায়। ১৯১৯ সালে তিনি তর্জমা করেন মুহাম্মদ হাফিজের একটি কবিতা; ‘আশায়’। পরিণত নজরুল মহাকবি হাফিজের দীওয়ান-ই-হাফিজ ও রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ থেকে অনেকগুলো কবিতা অনুবাদ করেছিলেন। সুফি কবি ওমর খৈয়ামও (১০৪৮-১১৩১) নজরুলের জাগর মনকে দুলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি অনুবাদ করেছিলেন রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম-এর বেশ কিছু কবিতা। মওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর মসনবির প্রথম কবিতা অনুবাদ করেছিলেন নজরুল। মূলের আস্বাদে শিহরিত সেই কবিতা হলো—
“শোন দেখি মন বাঁশির বুক ব্যেপে কী উঠছে সুর,
সুর তো নয় ও, কাঁদছে যে রে বাঁশির বিচ্ছেদ-বিধুর।
কোনো অসীমের মায়াতে
সসীম তার এই কায়াতে,
এই যে আমার দেহ-বাঁশি, কান্না সুরে গুমরে তায়,
হায়রে, সে যে সুদূর আমার অচীন-প্রিয়ায় চুমতে চায়।
প্রিয়ায় পাবার ইচ্ছে যে,
উড়ছে সুরের বিচ্ছেদে।”
(বাঁশির ব্যথা)
এই যে পরমের বিচ্ছেদে কান্না, তা ঘনীভূত মেঘ হয়ে অঝোর বরিষণে গ্লাবিত করেছিলো নজরুলের হৃদয়কেও। তিনি যখন বলেন-
“খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে বেহুঁশ হয়ে রই পড়ে
ছেড়ে মসজিদ আমার মুর্শিদ এল যে এই পথ ধরে,
তখন এক লিপ্ত সুফির আত্মকথন শোনা যায়।”
‘নতুন চাঁদ’ কাব্যে নজরুল সুফি তত্ত্বজ্ঞানের গভীর, অধীর উন্মোচন ঘটিয়েছেন। অভেদম কবিতায় তিনি আবিষ্কার করেন
বীজ রূপে রই—নিজ রূপ কই? খুঁজিতে সহসা দেখি সেই বীজ-আমি মহাতরু হয়ে ছড়ায়ে পড়েছি—এ কী!
সুফিতত্ত্বের পরম অনুসন্ধানে মগ্নচেতন তার কবিতা একা এবং একা হয়, খেলে একা একা : সৃষ্টির ঘুড়ি উড়ায় শূন্যে, আনন্দে নাচায় প্রাণ। ঘোষণা করে—
“দেখিয়াছ সেই রূপের কুমারে, গড়িছে যে এই রূপ?
রূপে রূপে হয় রূপায়িত যিনি নিশ্চল নিশ্চুপ!
কেবলই রূপের আবরণে যিনি ঢাকিছেন নিজ কায়া
লুকাতে আপন মাধুরী যে জন কেবলি রচিছে মায়া!
সেই বহুরূপী পরম একাকী এই সৃষ্টির মাঝে
নিষ্কাম হয়ে কিরূপে সতত রত অনন্ত কাজে।
পরম নিত্য হয়ে অনিত্য রূপ নিয়ে এই খেলা
বালুকার ঘর গড়িছে ভাঙিছে সকাল সন্ধ্যা বেলা ।
আমরা সকলে খেলি তারই সাথে, তারই সাথে হাসি কাঁদি
তারই ইঙ্গিতে পরম ‘আমি’রে শত বন্ধনে বাঁধি।
মোরে ‘আমি’ ভেবে তারে স্বামী বলি দিবাযামী নামি উঠি,
কভু দেখি—আমি তুমি যে অভেদ, কভু প্রভু বলে ছুটি।”
আর কতদিন কবিতায় নজরুল প্রেমের লীলা ও নিবেদনে মগ্ন। অপলক চোখে কবি আকাশের ফিরোজা পর্দা-পানে চেয়ে দেখেন, তার সেহেলি গ্রহতারারা নিশি জাগে পরমের সন্ধানে। কবির চারপাশেও সেই সন্ধান। দধিয়াল বুলবুলি আপন শিসে সেই সন্ধানের উচ্চারণ করে যায়। এরই মধ্যে কামিনী-কুঞ্জে কবি লাভ করেন পরমের ইঙ্গিত। শুধু ইঙ্গিত নয়, পরমের ডাক যে পরম মঞ্জিলে নিয়ে দেখান অপরূপা। তারপর তসবিতে কবি নাম জপেন তার, চোখ ভেসে যায় নীরে। এবং—
“তশবিহি” রূপ এই যদি তার ‘তনিজহি’ কিবা হয়,
নামে যার এত মধু ঝরে, তার রূপ কত মধুময়
কোটি তারকার কীলক রুদ্ধ অম্বর-দ্বার খুলে
মনে হয় তার স্বর্ণ-জ্যোতি দুলে ওঠে কুতূহলে।
ঘুম-নাহি-আসা নিঝুম নিশি-পবনের নিঃশ্বাসে
ফিরদৌস-আলা হতে যেন লালা ফুলের সুরভি আসে।
চামেলী জুঁই-এর পাখায় কে যেন শিয়রে বাতাস করে,
শ্রান্তি ভুলাতে কী যেন পিয়ায় চম্পা-পেয়ালা ভরে।”
নজরুল ইসলাম কবি হিসেবে যেমন হৃদয়ধর্মী, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রেও তেমনি হৃদয়ধর্মী। সুফিতত্ত্বের প্রগাঢ় দাবি মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু তথা যে নিজেকে চিনতে পেরেছে, সে চিনেছে আপন প্রভুকে। নজরুল এই তত্ত্বের প্রকাশ করেছেন জোরালো ভাষায় ও ছন্দে। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির আদি ও শেষ কথায় আছে আল্লাহর নির্ভরতা ও তার উপস্থিতির তীব্র ও সজীব উপলব্ধি, তাকে পাওয়া। হৃদয়ে পরম শক্তির সেই অভিপ্রকাশ নজরুলের আকাশে প্রথম ঈদের চাঁদরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। কেন জাগাইলি তোরা’ কবিতায় কবি সে কথাই তুলে ধরেছেন :
“মহা সমাধির দিকহারা লোকে জানি না কোথায় ছিনু
অমরা খুঁজিতে সহসা সে কোনো শক্তিরে পরশি –
সেই সে পরম শক্তিরে লয়ে আসিবার ছিল সাধ
যে শক্তি লভি এল দুনিয়ায় প্রথম ঈদের চাঁদ—”
‘রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজে’র ভূমিকায় কবি নজরুল ইসলাম বলেছিলেন, ইরানের অধিকাংশ কবিই যে শারাব-সাকি নিয়ে দিন কাটাতেন, এও মিথ্যা নয়। তবে এও মিথ্যা নয় যে, মদিনাকে এরা জীবনে না হোক কাব্যে প্রেমের আনন্দের প্রতিকরূপেই গ্রহণ করেছিলেন। শারাব বলতে এরা বোঝেন, ঈশ্বরের, ভূমার প্রেম, যা মদিরার মতোই মানুষকে উন্মত্ত কর তোলে। ‘সাকী’ অর্থাৎ যিনি সেই শারাব পান করার। যিনি সেই ঐশ্বরিক প্রেমের দিশারি, দেয়াসিনী। পানশালা সেই ঐশ্বরিক প্রেমের লীলানিকেতন। ‘সেই শারাব, প্রিয়া আর প্রিয়ার লীলানিকেতনের রসদ রয়েছে নজরুলেও। তার ভাষায়
“ওগো কবি, খামখা নীরস শাস্ত্রবাণী কও কাকে ?
ভাঙতে পারে প্রিয়ার ঈষৎ চাওয়া লাখো তৌবাকে।”
আর ‘বাদল-প্রপাতে শরাব’ এ বলেছেন,
“খামাখা তুমি মরছ কাজী শুষ্ক তোমার শাস্ত্র ঘেঁটে,
মুক্তি পাবে মদখোরের এই আলকিমিয়ার পাত্র চেটে।”
আত্মমুক্তির এ যাত্রায় নজরুল বহু পথে ঘুরেছেন, বহু ঘাটে তরী ভিড়িয়েছেন এবং অবশেষে ফিরেছেন স্রষ্টার প্রশান্ত সত্যতায়। আল্লাহর বাণী কুরআন তাকে দিলো সত্যস্বরূপ। এর কাব্যানুবাদে নজরুল খুঁজলেন আপন উপশম। হামদ-নাতে, নবীপ্রেমে এবং মা‘রিফতের রহস্যজলে তিনি দিলেন ডুব, জীবনের পরিণতি- বেলায়। শামসুন্নাহার মাহমুদকে (১৯০৮-১৯৬৪) লেখা এক পত্রে কবি বললেন, ‘আমার পনেরো আনা চলেছে আর চলেছে সৃষ্টি-দিন হতে আমার সুন্দরের উদ্দেশ্যে।’
‘আমার যত বলা আমার বিপুলতরকে নিয়ে, আমার সেই প্রিয়তম, সেই সুন্দরতমকে নিয়ে।’ সেই পনেরো আনা সুন্দরের খোঁজ কবি অবশেষে পেয়েছেন আল্লাহর কাছে ইসলামের মধ্যে। সেই পত্রের এক লাইনে নজরুল বলেন, “আমার গোপনতম কে যেন একেবারে নিশ্চুপ হয়ে থাকতে আদেশ করে।’ (পত্ৰ সংখ্যা- ১৩, নজরুল রচনাবলি)। এই নিশ্চুপ করে রাখান প্রয়োজনে স্রষ্টা হয়তো তাকে শেষ জীবনে নির্বাক করে দিয়েছিলেন। নির্বাক হওয়ার আগে ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভায় হঠাৎ বলে ফেলেছিলেন, ‘আমি আল্লাহকে দেখেছি। কিন্তু সে কথা বলার সময় এখনো আসে নাই। সেসব বলবার অনুমতি যেদিন পাব, সেদিন আবার আপনাদের সামনে আসব।’ কিন্তু কবি খোদাদর্শনের অর্থ ও স্বরূপ কী, তার বিস্তারিত অবগতি আমরা আর পেলাম না। কাজী নজরুল পূর্ববর্তী ও সমকালী, কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১), মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), হামিদ আলী (১৮৭৪ – ১৯৫৪), সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৫-১৯৫৬), ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), শেখ ফজলল করীম (১৮৮২-১৯৩৬), প্রমুখের কবিতায় সুফিতাত্ত্বিক রসদ ও মেজাজ থাকলেও কাজীর কবিতা ও গানে এর যে স্বচ্ছল অবগাহন হলো, তা ফারসী ভাষার মহান সুফিকবিদের কবিতার ভাবসম্পদের কথাই মনে করিয়ে দেয়।
জসীম উদ্দীনের (১৯০৩-১৯৭৬) কবিতায় মরমিতা বিম্বিত হয়েছে সরল দর্পনে। শেখ সাদীর তত্ত্বে মানবপ্রেম আর সেবাই হচ্ছে তাসাউফের প্রাণ। তিনি বলেছিলেন-
সেজদা ও তাসবিহ দেখে খোদ এলাহী ভুলবে না।
মানবসেবার কুঞ্জি ছাড়া স্বর্গ দ্বার খুলবে না।
জসীমের কবিতায় সেই সেবাব্রতী মন প্রেমিক অবয়বে মানুষকে দেয় আঘাতের প্রতিদান। প্রতিদান কবিতা যেন সুফিশিক্ষার প্রতিহিংসাহীন উদার মনস্ক অমিয়বাণী-
“আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা, আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।…..
যে মোরে, দিয়েছে বিষে ভরা বান,
আমি দেই তারে বুকভরা গান।
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনমভর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।”
জসীমের কবিতায় প্রেমের অন্তরে রয়েছে মরমি ভাবাবেশ। দুর্বিষহ যাতনা ভোগ করেও যে প্রেম নিঃস্বার্থ হবার মন্ত্র শেখায় – সুফিসাধকগণ একে বয়ে বেড়ান জীবনে ও জীবনবোধে। জসীমউদ্দীনের কবিতা সেই ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে।
প্রচুর ভাটিয়ালী গানের স্রষ্টা জসীম উদ্দীনের কবিতা ও গান হৃদয়ের আর্তি ও মর্মবেদনায় বিধৌত হয়ে পাঠক-শ্রোতাকে করে সিক্ত। তার ‘মুসাফির’ কবিতায় যে মুসাফির দুর দুরাশার জনহীন পথ পাড়ি দেয়, ভয়ঙ্করের পথে ধায়।
বেদনাকে সাথে নিয়ে খ্যাপা হয়ে দিগন্ত পাড়ি দেয়, বুক ভরা তার ব্যথা, যাকে দেখাতে চাইলে ছিঁড়তে হবে বুক, যার বুকের ক্রন্দনে জমাট বাঁধে শূন্যতা, সেই মুসাফির যেন একাগ্র সুফির প্রতীক। কেননা তার লক্ষ্য সুস্পষ্ট এবং ‘চলে মুসাফির আপনার রাহে, কোনো দিকে নাহি চায়।”
ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) মূলত রোমান্টিক কবি। তার কবিতা সুফিচৈতন্যে সারবান। ধ্রুপদ উদগতির যেসব কাব্য তিনি লিখেছেন, সেই কাহিনীকাব্য ‘হাতেম তায়ী’, কাব্যনাট্য ‘নৌফেল ও হাতেম’ আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ও আবেদনে সিক্ত। এর প্রধান চরিত্র হাতেম কল্যাণব্রতী নিষ্ঠা ও আত্মদানের এক অভিযাত্রী, যার প্রত্যয়ে বিম্বিত হয়েছে ফররুখের কাঙ্খিত মানুষ। সনেটগ্ৰন্থ ‘মুহূর্তের কবিতায় সুফি কবি শেখ সাদী, ফেরদৌসী, হাফিজ, রুমী, জামীকে নিবেদন করে ফররুখ লিখেছেন অন্তর্মুখী সনেট। দীওয়ানা মদীনা, জালালী কবুতর, তাজকেরাতুল আওলিয়া, চিরাগী পাহাড়, শবে ক্বদর উপলক্ষে ইত্যাদি সনেটে মূর্ত হয়েছে নিমজ্জিত এক সুফিমন। তেমনি সিরাজামমুনীরা কাব্যগ্রন্থে প্রেমপন্থী, অশ্রুবিন্দু, গাওসুল আজম, সুলতানুল হিন্দ, খানা নকশবন্দ, মুজাদ্দিদে আলফেসানী, মৃত্যু সংকট, অভিযাত্রিকের প্রার্থনা, মুক্তধারা ও ইশারা ইত্যাদি কবিতায় সুফিভক্তি উচ্চরোলে অভিপ্রকাশ লাভ করেছে। মহানবী (সা) ও তাঁর মহান খলিফাদের নান্দিবয়ানে দীপিত, উন্মুখরতায় পুলকিত কবি। সে পুলক প্রেম, নিবেদন ও ভক্তির প্রগাঢ়তায় প্রবুদ্ধ।
ফররুখকাব্যের শিরোভাগে দাঁড়িয়ে আছে বিখ্যাত ‘ডাহুক’। কবিতাটি ফররুখের প্রধানতম সৃষ্টি ও কাব্যসাফল্যের চিহ্নায়ক। একে অনেকেই বাংলা সাহিত্যের স্কাইলার্ক কিংবা ‘ওড টু নাইটিঙ্গেল’ বলে অভিধা দিয়েছেন। কিন্তু শেলী ও কীটসের এ কাব্যদ্বয় থেকে ডাহুক ছিলো আলাদা। রোমান্টিকতা ও সুফিভাবনার গভীরতর আবেশে কবিতাটি প্রাণপাতাল স্পর্শ করে। ডাহুকের সুর কবি হৃদয়ে এনে দেয় এক অনাবিল প্রশান্তি। ডাহুকের ডাকে কবি উপলব্ধি করেছেন অতীন্দ্রিয় এক অনুভূতি। গভীর নিস্তব্ধ রাতে সমগ্র পৃথিবী যখন অতল নিদ্রায়, কবি তখন জেগে আছেন একাকী। তখনই রাত্রির গভীরতা ভেদ করে ভেসে আসে অশ্রান্ত ডাহুকের ডাক। কবির অন্তর্জগতে শুরু হয় আলোড়ন। সেই সুর রাগিনী সুরা স্রোত হয়ে কবিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অন্য এক জগতে। মানবাত্মার চিরচেনা অথচ অচেনা সুরটিই কবি রাত জেগে শুনতে থাকেন ডাহুকের কণ্ঠে। অনাবিল প্রশান্তিতে ভরে যায় কবি হৃদয়। সুরের সুরার মত্ততায় কবি যেন মানবাত্মার মুক্তির পথ খুঁজে পান।
মানুষ সংসারে, মিথ্যায় নিয়ত প্রবঞ্চিত হয়। অতৃপ্তি অপ্রাপ্তির বেদনা তাকে করে রক্তাক্ত। আত্মনিপীড়নে দগ্ধ হয় মানুষ, সে চায় মুক্তি, কিন্তু পথ জানা নেই। তখনই কবি মুক্তির পথ খুঁজে পান ডাহুকের ডাকে। কেননা সে নিজে ডাকে না, অসীম সত্তার সুর ডাহুকের এ সুরের প্রতীকে কবি মূলত উপস্থাপন করেন সুফি সাধনাকে। সাংবাদিক আখতার উল আলমকে বলেছিলেন “তুই তো জানিস, মুজাদ্দিদী তরিকায় জিকির কী জিনিস। ‘ডাহুক’ রাত ভর ডেকে ডেকে গলায় রক্ত ওঠায়। মুজাদ্দিদী সাধকও তেমনি রাতভর ‘আল্লাহু’ ‘আল্লাহু’ জিকির করে নিজেকে ফানা করে দেন। গভীর রাতে নীরব নির্জন কোনো গ্রাম্য মসজিদে মুজাদ্দিদী তরিকার কোনো সাধক যখন ‘আল্লাহু’ ‘আল্লাহু’ জিকির করতে থাকেন, তখন মনে হয় অবিকল যেন একটা ডাহুক একমনে ডেকে চলেছে। আমার ‘ডাহুক’ কবিতা এই ধরনের মুজাদ্দিদী সাধকের জিকির নিয়েই রচিত।
(যুগ-প্রবর্তক কবি, আখতার-উল-আলম, ফররুখ আহমদ : কবি ও ব্যক্তি, শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত, পৃ. ১৯৮)
সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), মোহিতলাল মজুমদার ১৮৮৮–১৯৫২), জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯—১৯৫৪), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬), সুধীন্দ্ৰনাথ দত্ত (১৯০১–১৯৬০), কিংবা প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) মিস্টিক অনুভূতিতে ঋদ্ধ যে বাণীভাষ্য কবিতার অন্তঃস্রোতে বইয়ে দেন, তা বেদান্তবাদী অঙ্গীকারে জাগর হয়েও সুফিবাদী সুরের অনুচ্চারিত প্রভাবকে অস্বীকার করে না।
গোলাম মোস্তফা ( ১৮৯৭–১৯৬৪), বন্দে আলী মিয়া (১৯০৬-১৯৭৯) বেনজির আহমদ (১৯০৩-১৯৮৩), রওশন ইয়াজদানী (১৯১৭-১৯৬৭) কিংবা শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩) ফরাজী জুলফিকার হায়দার (১৮৯৯–১৯৮৭) এর মতো কবিরা বিচিত্র স্বভাবের কবিতার মধ্যেও আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা এনেছেন নানাভাবে।
চল্লিশের দশকে আহসান হাবীব (১৯১৭-৮৫), সিকান্দার আবু জাফর (১৯৯৮–৭৫), গোলাম কুদ্দুস (১৯২০ – ২০০৬), আবুল হোসেন (১৯২২- ২০১৪), সানাউল হক (১৯২৪–১৯৯৩) কবিতায় আধুনিকতা তীব্র মোচড় তৈরি করেছে এবং জৈবনিক উপলব্ধির প্রকাশ করছে অবলীল। এরই মধ্যে আত্মোপলব্ধির গভীর ভাষ্য রচিত হচ্ছে নিমগ্ন কলমে। বিশেষত সৈয়দ আলী আহসানের ‘আমার প্রতিদিনের শব্দ’ (১৯৭৪), ‘সমুদ্রেই থাবো’ (১৯৮৫) ‘চাহার দরবেশ’ ও অন্যান্য কবিতা (১৯৯২) সুফি অনুধ্যানে প্রবুদ্ধ। ‘জীবনের অন্তস্বরুপের রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা তিনি করেন। কিন্তু ভাববাদী, অলোক ধ্যানে তাত কবি রূপে এ রহস্যালোকের অনির্দেশ পরিক্রমণেই তাঁর আনন্দ।’ আবদুল কাদির, (১৯০৬–১৯৮৪), তালিম হোসেন (১৯১৮–৯৯), হাবীবুর রহমান (১৯২২–৭৬), আবদুর রশীদ খান ( ১৯২৪–২০১৯) আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭ – ২০২০), মযহারুল ইসলাম (১৯২৯-২০০৩), মনিরউদ্দীন ইউসুফ (১৯১৯-১৯৮৭), মতিউল ইসলাম (১৯১৫-১৯৮৪) প্রমুখের কবিতার শরীর ও মনে সুফিবাদের স্বাক্ষর নানাভাবে মুদ্রিত। এর মধ্যে সুফিবাদী অভিব্যক্তিপ্রধান কবি হিসেবে সৈয়দ আলী আশরাফ (১৯২৪–১৯৯৮) ছিলেন স্থিরলক্ষ্য ও সুফিচর্চায় মজ্জমান। তার ‘অন্বেষা’ কাব্যকে সেই স্থিতধী ভাষা দেয়, যা তার উচ্চারণে মূর্ত: “অসীম সসীম তার মিলে গেছে সমুদ্র-উল্লাসে। অতনু প্রবাহ তার অন্তরের অন্তরীক্ষে বাজিয়েছে প্রত্যক্ষ কিঙ্কিনি।”
চল্লিশ ও এর পরবর্তীতে নান্দনিক চরিত্রের পরিবর্তনের প্রভাব কথা বলছিলো কবিতার অন্তরতলে,যার প্রধান প্রবনতা শিল্পসর্বস্বতার নান্দীপাঠ, সমাজচেতনার মুক্তভাষ্য, প্রগতিচেতনার উল্লম্ফন। এরই মধ্যে ভাষা ও ভূখণ্ডের প্রতি অঙ্গীকার যেমন তাজা ছিলো পঞ্চাশের কবিতায়, তেমনি সাংস্কৃতিক আত্মচেতন কবিতাধারা সুফিবাদী উপাদানকে অঙ্গীভূত করেছে।
মানবতাবাদ, সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রভাব, আধুনিকতার অন্বেষা, নতুনত্বের কামনা, আত্মচেতন স্বাতন্ত্র্যবাদী বোধের সোচ্চারতা, মাতৃভূমি- মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সামাজিক প্রত্যয়, ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রভাব পঞ্চাশের কবিতাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে। সুফিবাদে অলগ্ন কবিদের কবিতায়ও সুফি ঐতিহ্যের উচ্চারণ এবং প্রতীক ও ভাবধারার ব্যবহার জারি থাকে। কয়েকটি নমুনা দেয়া যাক।
শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬)
“সূর্যের তেজ ম্লান হতেই প্রশান্ত অদূরে
গাছতলায় একজন বুজুর্গকে দেখতে পাই। কী যেন
আমাকে তার দিকে টেনে নিয়ে যায়। পক্ক কেশ আলেম
তাকান আমার দিকে অপরূপ
দৃষ্টি মেলে। হাতে তাঁর এক অজানা কেতাব।
ইচ্ছে হলো তাঁর পা ছুঁয়ে অবনত হই। পরক্ষণে
দৃশ্য মুছে যায়। আমি মেঘমালার দিকে তাকিয়ে
নতুন এক কবিতার প্রতিমা পেয়ে যাই। আড়াল ফোটে
আসমানে ভাসমান কার্পেট প্রবীণ যাত্রী
তাকান আমার দিকে হাসিস্নাত দৃষ্টিতে।”
(দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে)
সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬)
কিছু শব্দ উড়ে যায়, কিছু শব্দ ডানা মুড়ে থাকে,
তরল পারার মতো কিছু শব্দ গলে পড়ে যায়।
এমন সে কোনো শব্দ নক্ষত্রের মতো ফুটে থাকে
তুমি কি দেখেছো তাকে হৃদয়েশ্বরের আয়নায়?
(কিছু শব্দ উড়ে যায়)
শহীদ কাদরী (১৯৪২-২০১৬)
“এই গ্রহের মহাপুরুষরা কে কী বলেছেন
আপনারা সবই জানেন। এখানে বক্তৃতা আমার উদ্দেশ্য
নয়। আমি এক নগন্য মানুষ, আমি
শুধু বলি: জলে পড়ে যাওয়া ঐ পিঁপড়াটাকে ডাঙায় তুলে দিন”
(আপনারা জানেন)
সুফিচেতনা যাদের ব্যাকুল করেছিলো পঞ্চাশের এমন কবিদের অন্যতম হলেন আবদুস সাত্তার (১৯২৭-২০০০)। তাঁর পবিত্র নামের কাব্য নিরেট সুফিধারার এক কবিতাগ্রন্থ। বিশ্বাসে সমর্পণ এবং পরিচ্ছন্ন জীবনবোধ তার কাব্যের উন্মোচক বৈশিষ্ট।
তাঁর — অন্তরঙ্গ ধ্বনি’কাব্য গ্রন্থে এর জোরালো অনুভুতি বাঙময়।
“পবিত্র বাণীর মন্ত্রে ভালোমন্দ চিনেছি এখন
সত্তার অঙগনে হেঁটে; জীবনের বাগানে একক
বসন্তের মঞ্জরিত সকল ফুলের ভালোবাসা
নির্বিঘ্নে ফোটাই সুখে, অবজ্ঞার আস্তাকুঁড়ে ফেলি
পঙ্কিল জীবন বৃত্তি অবারিত ইচ্ছার বিলাসে।”
নামের মৌমাছি কাব্যগ্রন্থও সুফিভাবে সুগন্ধিময়। জীবনাবেদনের বিশিষ্টতা এবং রহস্য সন্ধানী প্রশ্নশীলতা তার শব্দাবলিকে করেছে বহুঅর্থী। একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি—
“সাগরের জলে কি লেখা আছে !
প্রেমিক ! তুমি কি জানো সে ভাষা ?
নীরবে দাঁড়িয়ে তটের কাছে
পড়ে দ্যাখো জলে কি লেখা আছে।
ঢেউয়ের দোলায় কেমন নাচে,
অযুত কামনা মায়াবী আশা!
সাগরের জলে কি লেখা আছে
প্রেমিক তুমি কি জানো সে ভাষা ?
(নামের মৌমাছি)
আল্লাহর উপস্থিতির বোধ ও নবীপ্রেম সুফিসাধনার পরম ইপ্সা। আবদুস সাত্তার এই বোধের বিবৃতি দিচ্ছেন প্রশ্নবোধক কুহক সহকারে। লিখেন-
“আমার এ দেহ ধরে মহান আল্লাহ বাস করে
তুমিও সেখানে আছো, হে আমার রাসুল, এ ঠিক
আল্লাহ রাসুল মিলে এই দেহ আত্মার অধিক
তখন কি আমি থাকবো না আল্লার ভিতরে?”
(আল্লাহ-রাসুল-এর আলোকে)
আল মাহমুদের (১৯৩৬ -২০১৯) কাব্যে সুফিচেতনার অবলীল উপস্থিতি তৈরি করে সম্পন্ন খড়ের গম্বুজ। আল মাহমুদ বলেছিলেন, সুফি মত আমার কবিতায় বিশেষ প্রভাব ফেলেছে! আর পবিত্র কুরআন আমার কবিতা লেখার প্রধান পাথেয়!
বিকাশের প্রথম প্রহর থেকে আল মাহমুদের কাব্যে সুফিভাবের পদপাত ছিলো প্রচ্ছন্ন। কালের কলসে বেজে উঠে কবির উচ্চারণ—
“তাকান, আকাশে অই অন্ধকার নীলের দ্যুলোকে
এমন তারার কনা, যেন কোনো স্থির বিশ্বাসীর
তসবিহ ছেঁড়া স্ফটিকের দানা! শূন্য সৌরলোকে
পরীর চাঁদের নাও দোল খায়! অলীক নদীর
অস্থির পানির আভা স্পর্শ করে দূর বাতাসের
অসীম সাহস—”
(অসীম সাহসী
সোনালি কাবিন দিয়ে বাংলা কবিতার সাথে বাসর নিশ্চিত করছেন যখন,
তখনই কবি জানাচ্ছেন—
“কোথাও রয়েছে ক্ষমা, ক্ষমার অধিক সেই মুখ
জমা হয়ে আছে ঠিক অন্তরাল আত্মার ওপর!
আমার নখের রক্ত ধুয়ে গেলে
যেসব নদীর জল লাল
হয়ে যাবে বলে আমি ভয়ে দিশাহারা
আজ সে পানির ধারা পাক খেয়ে নামে
আমার চোখের কোনে
আমার বুকের পাশ ঘেঁষে!”
(তোমার আড়ালে, সোনালী কাবিন)
এরপর পৃথিবীর সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থটি বুকের ওপর রেখে কবি যখন ঘুমিয়ে পড়লেন, তারপর তার চেতনালোকের মায়াবি পর্দা দুলে উঠলো । যার ফাঁক দিয়ে ধরা পড়ে রহস্যময় স্বপ্ন। চলে যান সেই মুহূর্তে, যখন নামুস জিব্রাইল পৃথিবীর শেষ পয়গাম্বরকে আদেশ করেন, পাঠ করো। সেই পাঠের দ্যুতিতে স্নিগ্ধ হয়ে কবি জানালেন ঋদ্ধ অভিজ্ঞতা—
ঘুমের মধ্যে কারা যেন, মানুষ না জিন
আমার কবিতা পড়ে বলে ওঠে, আমিন, আমিন!
(সবুজ ঈমান)
অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না কাব্যগ্রন্থের হযরত মোহাম্মদ (সা) কবিতায় তিনি লেখেন—
“হেরার বিনীত মুখে বেহেশতের বিচ্ছুরিত স্বেদ
শান্তির সোহাগ যেন তার সেই ললিত আহ্বান,
তারই করাঘাতে ভাঙ্গে জীবিকার কুটিল প্রভেদ
দুঃখের সমাজ যেন হয়ে যাবে ফুলের বাগান!
লাত মানাতের বুকে বিদ্ধ হয় দারুন শায়ক
যে সব পাষাণ ছিল গঞ্জনার গৌরবে পাথর
একে একে ধসে পড়ে ছলনার নকল নায়ক
পাথর চৌচির করে ভেসে আসে ঈমানের স্বর!”
সুফি কবিতা মানুষের পরিণতি নিয়ে ভাবিত হয়, অনন্তকালীন জিজ্ঞাসায় হয় তাড়িত। প্রকৃতির নিদর্শন সমূহে নিহিত ইঙ্গিত সমূহকে অবলোকন করে বিশ্বাসের চোখ দিয়ে। আল মাহমুদে লক্ষ্য করা যায় এর স্বাক্ষর—
“অনন্তকালের মধ্যে তুমি কি করে থাকবে?
যেখানে একটি নদী চলতে চলতে অদৃশ্য হয়ে যায়,
একটা পাখি উড়ে যায় এমন অসীম শূন্যতায়
মনে হয় নিজের দৃষ্টিই ফিরে এলো নিজের দিকে!
অনন্তকাল কি করে চুম্বনের শব্দ?
কোনো পরিচিত বৃক্ষের সবুজ কি অনন্তকাল?
আমাদের বাড়ির পুকুর পাড়ে
সবনে গাছে একটি পাখি!
আমার সমস্ত সচেতন কালের মধ্যে এর পালক খোঁচানো
আমি অবলোকন করি!”
(অনন্তকাল, অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না)
ঈদের চাঁদ কবির কাছে হযরত আলীর খঞ্জরের ছবি নিয়ে হাজির হয়, যে আলী আছেন সুফিপন্থাসমূহের কেন্দ্রে। জনশূন্য রাস্তায় লাইটপোস্টের গায়ে হাত রেখে কবি বলেন ঈদ মোবারক। বস্তু ও ইট-পাথরের শহর সাড়া দেয় এতে। সাড়া দেয় রাতের চাঁদোয়া। যেমনটি ঘটে দরবেশের অভিজ্ঞতায়। কবি যেন সেই অভিজ্ঞতার পাঠকে বাঙময় করলেন—
“সাথে সাথে ঢাকা মহানগরী থেকে এক অপার্থিব জ্যোৎস্নায়
ঝলসে গিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে গেলে
পশ্চিমাকাশ থেকে মেরাজের ঘোড়ার মতো
নেমে এসে আমার সামনে নূহের নৌকার
মতো দুলতে লাগলো — ঈদের চাঁদ!”
(সব ইমারতের বাইরে)
সন্ধ্যায় আবছা ছায়ার নিচে দূর যখন সূর্য ডুবে যায়, পড়ন্ত আলোর মধ্যে কবি প্রকৃতির রহস্যে আচ্ছাদিত হন। দেখেন—
“তোমার সিজদা দেখে এ ঘরের পায়রা ডেকে ওঠে
গম্বুজের ভিতরে যেন দম পায় সুপ্ত এক দরবেশের ছাতি,
কি শীতল শ্বাস পরে! শান্ত শামাদানের সম্পূটে
বাতাসে যেন নিভে গেল ফজরের মগ্ন মোমবাতি!
তুমি কি শুনতে পাও অন্য এক মিনারে আযান?
কলবের ভিতর থেকে ডাক দেয়, নিদ্রা নয়, নিদ্ৰা নয়, প্রেম
সমুদ্রে খলিয়ে ওযু বসে থাকে কবি এক বিষণ্ণ, নাদান!
সবারই আর্জি শেষ! বাকি এই বঞ্চিত আলেম!
তোমার সালাত শেষে যেদিকে ফেরাও সালাম
বামে বা দক্ষিনে, আমি ওমুখেরই হাসির পিয়াসী,
এখন ও তোমার ওষ্ঠে লেগে আছে আল্লাহর কালাম
খোদার দোহাই বল ও ঠোঁটেই আমি ভালোবাসি!
আমার রোদনে যেন জন্ম নেয় সর্বলোকে ক্ষমা
আরশে ছড়িয়ে পড়ে আলো হয়ে আল্লাহর রহম,
পৃথিবীতে বৃষ্টি নামে, শষ্পে ফুল, জানো কি পরমা
আমার কবিতা শুধু ওই দুটি চোখের কসম!”
(কালো চোখের কাসিদা, বখতিয়ারের ঘোড়া)
শুধু সেজদা দেখা ও দেখার অনুভূতির ভেতর উবুড় হয়ে পড়ে থাকা নয়, সেজদায় লুঠিয়ে পড়াটাই সুফিচেতনার আদেশ। কবি লুঠিয়ে পড়েন সমর্পণের সেজদায়, কথন হয় রুহের পাখির সাথে। কবির ভাষ্য—
“ইশকের আগুনে বসে মাওলানা রুমির গজল
গাও কি রুহের পাখি? নাকি কোনো সুফির সাধনে
দেহের বিনাশ মেনে ভর রাখে নূরের ওপর!
প্রেম কি আলোই তবে? দীপ্তিরই অন্য পরিণাম?”
(নেকাব্য)
সুফি সান্নিধ্য অনুভব করেন কবি আপন সত্তায়। জিকির ধ্বনিত হয় হৃদয় ফুঁড়ে। আল মাহমুদীয় বচনে এর প্রকাশ :
ঠিকানা বিহীন নাওয়ের ভাসান ঠেকলো অজান চরে
হালের মুঠি ছেড়ে শ’তান ডুবল রে অন্তরে!
বাতাস এসে ছড়িয়ে দিল বদর পীরের ফু
বুকের মাঝে উঠলো জিকির আল্লাহু আল্লাহু!
(ঠিকানাহীন নাওয়ের ভাসান)
প্ৰাৰ্থনায় নত আল মাহমুদ কদর রাত্রিতে চান সেই বিভূতি, হেরার হৃদয়ে স্বর্গীয় আলিঙ্গনের শিহরণ যে পুলকের পরম নমুনা। কবি চান—
হে আল্লাহ
হে সমস্ত উদয়দিগন্ত ও অস্তাচলগামী আলোকরশ্মির মালিক
আজকের এই পবিত্র মহাযামিনীর সব রকম বরকত আমাকে দাও !
আমাকে দাও সেই উত্তেজক মুহূর্তের স্বর্গীয় পুলক যাতে
একটি সামান্য গুহার প্রস্তরীভূত শিলাসহ কেঁপে উঠেছিলেন
মহানবী মুহাম্মদ (সা)
(কদর রাত্রির প্রার্থনা)
সুফিসাধনায় আত্মতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ। নিজের স্বরূপ, আত্মবিচার, আত্মজিজ্ঞাসা এবং আত্মখনন সুফির প্রাত্যহিক লড়াই। নিজের বিশ্বাসের সবল ঘোষণা এখানে চাই। আত্মপরিচয়ে অস্পষ্টতার জায়গা এখানে নেই। নিজেকে জানতে হবে আমি কী এবং কী নই? আমি কার এবং কার নই? আল মাহমুদ জানাচ্ছেন—
আমি তাল মাত্রা বাদ্যযন্ত্র ছাপিয়ে ওঠা আত্মার কেরাত!
আরম্ভ ও অন্তিমের মাঝখানে স্বপ্ন দেখি সূর্যের সিজদারত নিঃশেষিত
আগুনের বিনীত গোলক!
নবী ইব্রাহিমের মত অস্তগামী দের থেকে আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি!
আমিও জেনে গেছি কে তুমি কখনো অস্ত যাও না! কে তুমি চির বিরাজমান !
তোমাকে সালাম! তোমার প্রতি মাথা ঝুকিয়ে দিয়েছি! এই আমার রুকু,
এই আমার সিজদা—
অপ্রস্তুত আত্মা আমি! কিন্তু জানি তুমি ছাড়া আমার
দোদুল্যমান শরীরের নৌকা খানি অন্য ঘাটে জমায়নি পাড়ি!
পারানির কড়ি নেই! কিন্তু ছিল তোমাতে ভরসা !
পাপী আমি! কিন্তু জানি বহু দূরে আছে এক ক্ষমার তোরণ!
ভ্ৰান্ত আমি! কিন্তু জানি আছে এক দয়ার্দ্র হাসির দীপ্তি অনন্তে, অসীমে!
হে আমার আরম্ভ ও শেষ!”
(হে আমার আরম্ভ ও শেষ, দোয়েল ও দয়িতা)
কবির সর্বশেষ প্রার্থনা এক আধ্যাত্মিক আকুতির উচ্চারণে মথিত হয়ে জীবনাবেদনকে গ্রথিত করে অন্তিম উপসংহারে। সাফল্য প্রত্যক্ষ করে আত্মিক সফলতার প্রত্যাশায়। অতএব কবির দরবিগলিত মনের বিশ্বস্ত উচ্চারণ—
“কোনো এক ভোরবেলা, রাত্রিশেষে শুভ শুক্রবারে
মৃত্যুর ফেরেশতা এসে যদি দেয় যাওয়ার তাকিদ;
অপ্রস্তুত এলোমেলো এ গৃহের আলো অন্ধকারে
ভালোমন্দ যা ঘটুক মেনে নেবো এ আমার ঈদ!
আমার যাওয়ার কালে খোলা থাক জানালা দুয়ার
যদি হয় ভোরবেলা স্বপ্নাচ্ছন্ন শুভ শুক্রবার!”
(স্মৃতির মেঘলাভোরে, আমি দূরগামী)
পঞ্চাশের অন্যতম কবি মুহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর (১৯৩৬-২০১৩) জুলেখার মনপ্রতিনিধিত্বশীল এক কাব্যগ্রন্থ। এতে আল কুরআন ও বাইবেলজাত কাহিনীর শরীরে কাব্যস্থাপনা গঠিত। ঐতিহ্যলগ্নতা, বিশ্বাসের বরাভয় এবং আত্মিক স্বাচ্ছন্দ্যকে কামনা করেছে এই কাব্য। পঞ্চাশের কবিদের মধ্যে আলাউদ্দীন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩), বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (১৯৩৬–২০২০), ফজল শাহাবুদ্দীন (১৯৩৬– ২০১৪), আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৯৩৬–১৯৮৯) ওমর আলী (১৯৩৯- ২০১৫), দিলওয়ার (১৯৩৭-২০১৩) প্রমুখের কবিতার নানা বাকে অন্তরলোক- সন্ধানী উজ্জীবন প্রকটিত হয়েছে। যাকে সচেতন সুফিবাদ বলা যায় না বটে। তবে কবিতার বিচিত্র আধারে সহসা খেলে গেছে রূহানি পিপাসা ও কাতরতা।
সুফিবাদী বীক্ষায় নিষিক্ত কবিতা ষাটের কবিদের হাতেও জ্বলে উঠেছে। যার অগ্রপথিক ছিলেন আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩ – ২০১০) ও আফজাল চৌধুরী (১৯৪২–২০০৪)। সকল প্রশংসা তাঁর কাব্যে সৈয়দ কবি নিজের সঙ্গে আল্লাহর, মহানবীর, ফেরেস্তাদের এবং নিখিলরহস্যের নিগূঢ় সম্পর্কের অর্থসন্ধান করেছেন। তার পরম অভিপ্রায় ছিলো সেই জ্যোতি, যে অজর, অক্ষয়, অম্লান। সৈয়দের প্রার্থনা—
“জ্যোতির উপরে জ্যোতি, সৰ্বব্যাপ্ত হে মহামহিম
আমার হৃদয়ে ফ্যালো তোমার আলোর এক কণা।”
(জ্যোতির উপরে জ্যোতি)
সৈয়দ চিরন্তনের তালাশ করেছেন বিচিত্র রূপকল্পের আশ্রয়ে। প্রেমের চিরন্তনতা, সৃষ্টির বাহ্যিক প্রকাশে অন্তলীণ বার্তা, মানবসত্তার অন্তরঙ্গতা, মানবাত্মার ব্যাপ্তি ও গভীরতার অনুভাবকে উচ্চারণ করেছেন প্রতীকে, সনেটের বন্ধনে, পরাবাস্তব দৃষ্টির স্কেচে।
যে স্কেচে দেখা যায়—
“সশব্দে হেলিকপ্টার দিয়ে যায় আকাশে চক্কর-
তারও ধ্বনি ডুবে যায় ; কোনো স্বরে মিশে যায় স্বর?
তারই মধ্যে হয়ে উঠলো আমার সত্তাও চক্রবাক
গম্বুজ-গাছের মতো ঊর্ধ্ব হলো আমার পিপাসা
সব বস্তু দুহাত তুলেছে। সমস্ত পেয়েছে ভাষা
গুঞ্জন ভেতরে মেশে। নীরবতা। প্লাবিত মৌচাক।”
(স্কেচ)
ঘন-নীল রাত্রির ভেতরে পরমের মুক্তার প্রজ্জলন দেখেন সৈয়দ, দিবসের পূর্বললাটে দেখেন তার দীপিত হীরা। সকল প্রশংসা তাঁর নামকাব্যে তিনি দেখান সেই সত্তাকে, যিনি তুচ্ছতাকে যুক্ত করেন অসীমে-বিরাটে। আর সমস্ত সৌন্দর্য মূলত লোকোত্তর প্রতিভাস।
যখন মহানবীকে ব্যক্ত করেন তিনি, তখন দেখেন তিনি মূলত আত্মার দর্পন, যার দীর্ঘ বাহু চরাচরে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। তাঁর নীলিম চোখ নিজেই এক বিশাল গগণ। তাঁর অলৌকিক আলোর আভা ভাসিয়ে নেয় সকল চরাচর।
আফজাল চৌধুরী ছিলেন ষাটের দশকী বাস্তবতায় ভিন্ন মেজাজের এবং স্বতন্ত্র পথের যাত্রী। আধুনিক কিন্তু ঐতিহ্যাশ্রয়ী। ভাববাদী এবং প্রতীকী পরাবাস্তব কবি ছিলেন তিনি। প্রাচীনে-অর্বাচীনে সমন্বয় ছিলো তার ভাবানুশীলনে। তার কবিদৃষ্টিতে ছিলো নিশ্চয়তা, বাস্তবানুকূল্য এবং ব্যক্তিহৃদয়ের বিপুল আর্তি, যা সমগ্রের প্রতিধ্বনি হয়ে শিখায়িত। এ শিখা ছিলো তার কাব্যের প্রাণ, যার অপর নাম সুফিমনের সংরাগ। অতএব এ স্বাভাবি ছিলো যে, নিজের চিহ্নায়ক কল্যাণব্রত কাব্যে আফজাল চৌধুরী বলবেন—
“বলিও আমার প্রেম ঈশ্বরের ভষ্ম নয় ভূমা
আলোকিত কোলাহলে সমতল আত্মার সঙ্গীত
রাশি রাশি পুলকের বিন্দু বিন্দু বোধের অতীত
অন্য এক বোধ আর স্পন্দমান আলোর উপমা
আলোক সে নির্ভুলের আন্তরিক বলীয়ান ক্ষমা
বলিও আমার প্রেম ঈশ্বরের ভষ্ম নয়-ভুমা।”
জীবনবিশ্বাসের মূলীভূত মন্ত্রকে খোঁজে বেড়িয়েছেন আফজাল। বলিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়ী এবং প্রশান্ত উন্মীলনে তার কাব্য দ্বান্দ্বিক জড়বাদ, মানুষের আত্মপলায়ন এবং প্রকৃতির সরলতা থেকে সরে গিয়ে কৃত্রিম অস্থিরতায় ক্ষত- বিক্ষত প্রবৃত্তির বিরোধিতা করেছে। উপস্থাপন করেছে প্রখর,মোহন বিশ্বাসের বরাভয়।
এর স্বাক্ষর রয়েছে ‘হে পৃথিবী নিরাময় হও’ কাব্যনাট্যে। সত্য-মিথ্যার দ্বান্দ্বিক পৃথিবীর আবহ থেকে মানব জাতির নিরাময় হওয়ার আকুতি এর পঙক্তিতে পঙক্তিতে উপচে পড়েছে। কাব্যনাট্যের বিস্তার দরবেশের মাজারকে ঘিরে। যেখানে কবি বিক্ষত সমকালের যন্ত্রণায় উচ্চারণ করেন আপন আকুতি।
বলেন—
“মৃত্যুর মোহন নৃত্য বার বার চোখ বুজে দেখি,
পরলোকে ছায়া ফেলে এই কুঞ্জে দাঁড়াই যখনি
খুলে দাও দাও খুলে রহস্যের নিখিল দরোজা,
তোমার গৃহস্থ যারা তাদের স্বচ্ছন্দ বিচরণে
নিভৃত এ কুঞ্জ হোক ওপারের বিমূর্ত আঙিনা।”
(হে পৃথিবী নিরাময় হও)
কবি-চিন্তক ফরহাদ মজহারের (১৯৪৭) এবাদতনামা প্রবল সংবেদনে কবির ভাবকে রাষ্ট্র করে। একে সুফিবাদঋদ্ধ কাব্য হিসেবে ব্যক্ত করার সুযোগ সীমিত। বরং সুফিবাদকে ত্যক্ত করে এ কাব্যের অভিমুখ। কবি এবাদত করেন তার বুদ্ধিকে, যুক্তিকে (উৎসর্গ পদ্য, এবাদতনামা-১১)। কখনো এ কবিতা মুসলিম চরিত্র নিতে চায়, কখনো দাবি করে ‘আমি হিন্দু ঘোর পৌত্তলিক’ (এবাদতনামা ৮৪), এ কবিতা আল্লাহকে ইবাদত করতে নারাজ (এবাদতনামা ৫, ৮, ১৬, ৯৬)। এবাদতনামায় আল্লাহর প্রতি তিক্ত অভিযোগ প্রধানত উচ্চকিত। যেমন—
“তিলে হিম্মত নই, আধা ছটাকের নাই তেজ
সাত আসমানে প্রভু, খোদা তা’লা হয়ে বসে আছ।”
(এবাদতনামা : ৬)
বিশ্বাসে কবির ইমান নাই, বুদ্ধি অবলম্বন করে তিনি স্থির করতে পারেন ন তার পথ।—
বিশ্বাসে ইমান নাই তদুপরি তুমিও মালিক
বুদ্ধি দিয়েছো ঠিকই, অথচ খাটালে বুদ্ধি ভাবো
মস্তিষ্কে আসর করে বেতমিজ দুষ্ট ইবলিশ
ফাঁপরে পড়েছি মাওলা কী বা করি কোনো রাহে যাই।
(এবাদতনামা-১১)
এ গ্রন্থে মূলত নদীয়ার ভাবঅন্বেষা মূর্ত হয়েছে। যাতে কবি চৈতন্য বা গৌরাঙ্গ (১৪৮৬-১৫৩৪) লালন ফকির (১৭৭৪-১৮৯০) প্রমুখবাহিত ভাব- সম্পদকে মূর্ত করেছেন আপন দার্শনিক ও কাব্যিক অসামান্যতায়। কবিতা হিসেবে স্থাপত্য ও অন্তর্লাবণ্যে এবাদতনামা গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবক।
সৌন্দর্য, মানবকেন্দ্রিকতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপ্রকল্প, ভাব ও ভাষাবিদ্রোহ ইত্যাদির সাথে চৈতন্যপন্থী উত্তরাধিকার এবাদতনামার চতুর্দশপদীগুলোতে ব্রীড়ালিপ্ত। সুফি কবিতা হিসেবে এর প্রস্তাবনাকে কবুল করবে না সুফিতত্ত, নিজস্ব উসুলেই।