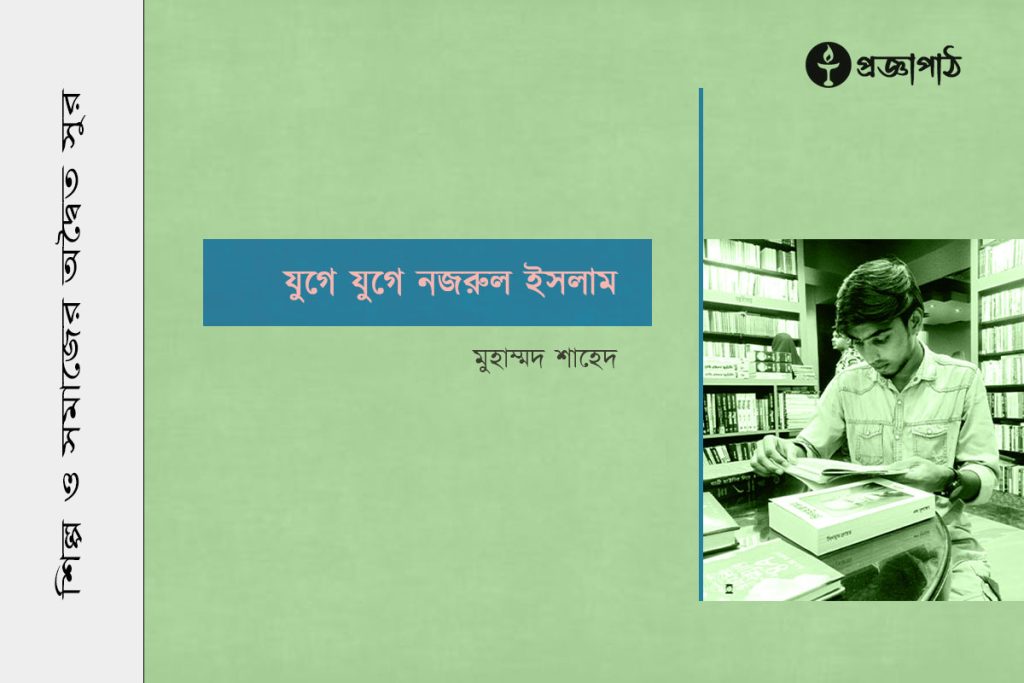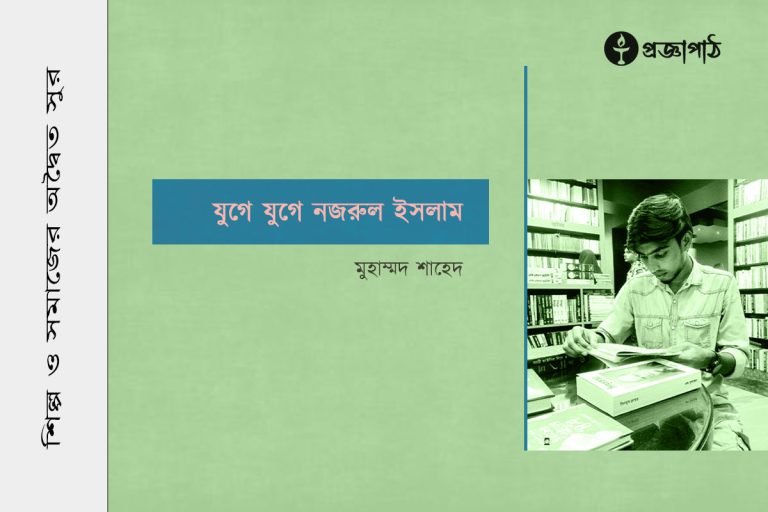বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হচ্ছে তবে আজ যেন অন্য দিনগুলোর চেয়ে ভিন্ন। বসন্তের হাওয়া শীতল, কিন্তু তার শীতলতা নিছক শীতের মতো কাঁপন ধরায় না বরং এক মিষ্টি শিহরণ ছড়িয়ে দেয় চেতনাজুড়ে। রেল স্টেশনের বাতাসে এক অদ্ভুত গন্ধ, কোনো অজানা ফুলের সৌরভ, রেললাইনের গরম লোহার গন্ধ, আর পুরনো কাঠের বেঞ্চের মৃদু পচন সব মিলিয়ে যেন এক জটিল রসায়ন, যা সময়ের অনুভূতিকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। টোঙের দোকানের ছাদে ঝোলানো হলুদ আলো এক অদৃশ্য বৃত্ত এঁকেছে কুয়াশার ভেতর, তার কিনারাগুলো ধীরে ধীরে মিশে যাচ্ছে বসন্তের নরম মেঘের মতো। পাশে বসে আছে শহীদুল ইসলাম আর জামিল মন্ডল। দুই পুরনো বন্ধু, বহুদিন পর জীবনের সমস্ত হিসাব-নিকাশ ভুলে এসে ঠেকেছে এই রেল স্টেশনের শান্ত অবয়বে। সামনে রাখা ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ, আর দূরে কোনো অজানা ট্রেনের ইঞ্জিনের দীর্ঘ বাঁশির শব্দ, যা যেন বাতাসের বুক চিরে রেখে যায় এক অতল দীর্ঘশ্বাস। কথার ফাঁকে ফাঁকে নীরবতা নেমে আসে। বসন্তের রাত এভাবে নিঃশব্দ হয়ে থাকে না, তার মধ্যে এক অপার্থিব প্রতিধ্বনি থাকে, পাতা ঝরার শব্দ, কোনো ক্লান্ত যাত্রীর কাশির প্রতিধ্বনি, অথবা দূর থেকে ভেসে আসা কোনো নাম না জানা গানের করুণ সুর। সেই সুরের মাঝেই শহীদুল আচমকা বলে ওঠে,“নজরুল কি কেবল সময়ের কবি?”
কথাটি বাতাসে ভেসে থাকে কিছুক্ষণ, কুয়াশার মতো ধীরে ধীরে চারপাশে মিশে যায়। জামিল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, যেন শব্দের ভেতর গিয়ে গভীর কোনো উপলব্ধির সন্ধান করছে। তারপর ধীরে বলে,“সম্ভবত তিনি সময়ের ঊর্ধ্বে এক কবি। তাঁর কবিতাগুলো কেবল বিদ্রোহী ভাষার নয়, বরং এক অনন্ত সুর, এক চিরন্তন স্রোত। আমরা কি তাঁকে বোঝার চেষ্টা করেছি? নাকি আমরা তাঁকে কেবল সেই পরিচয়ের মধ্যেই আটকে রেখেছি, যা আমাদের বোঝার সীমাবদ্ধতার কারণে সৃষ্টি হয়েছে?”
স্টেশনের বাতাসে একধরনের ধাতব শীতলতা মিশে থাকে, বসন্তের কোমলতা তার রুক্ষতাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে। চায়ের কাপের ধোঁয়া ধীরে ধীরে বাতাসে মিলিয়ে যায়, ঠিক যেমন কিছু কিছু স্মৃতি সময়ের ধুলোয় ঢাকা পড়ে যায়, অথচ সম্পূর্ণ মুছে যায় না। শহীদুল একটুক্ষণ চুপ থেকে বলে,“তবে নজরুল কি কেবল বিদ্রোহী? নাকি তিনি আমাদের চেতনার প্রতিটি স্তরে প্রবাহিত এক নীরব শক্তি, যার প্রতিধ্বনি আমরা উপলব্ধি করি কিন্তু ভাষায় ধরতে পারি না?”
জামিল মৃদু হেসে বলে, “তিনি প্রকৃত বিদ্রোহী, কারণ তিনি শুধু শাসনের বিরুদ্ধে নয়, বরং সময়ের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করেছেন। তিনি সীমানার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, এমনকি আমাদের বোঝার সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধেও। তাঁর সৃষ্টির আগুন কখনো নিভে যায় না, শুধু রূপ বদলায়।”
এক মুহূর্তের জন্য চারপাশ স্তব্ধ হয়ে যায়। দূরে কোথাও দুটো পাখি হঠাৎ ডানা মেলে উড়ে যায় রেললাইনের ওপারে, অন্ধকারের দিকে। স্টেশনের বাতাসে এক অদ্ভুত অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে যেন সময় থমকে গেছে, অথবা হয়তো এই স্টেশনে সত্যিই কোনো সময় নেই, কেবল স্মৃতির ভেতরে তার অস্তিত্ব বেঁচে থাকে।
নীরবতা ভেঙে শহীদুল চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলে উঠলো, আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম নিয়ে আজকাল তোমার কী ভাবনা? আমি তো ভাবি, তাঁকে নিয়ে আমরা যতই পড়ি, ততই নতুন কিছু পাই।
জামিল মণ্ডল: একদম ঠিক বলেছ। নজরুল তো এক জীবন্ত বহুমাত্রিক মহাকাব্য। বিদ্রোহী কবি বলে তাঁকে চিনি, কিন্তু তাঁর প্রেম, তাঁর ভাষার বৈচিত্র্য, আর তাঁর অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা কি কখনো পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছি?
শহীদুল ইসলাম: ঠিক তাই। জানো, যখন তাঁর ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি পড়ি, তখন মনে হয়, এটা শুধু একটি কবিতা নয়, বরং এক ধরনের জাগরণের মন্ত্র। তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছো, নজরুল আমাদের সাহিত্যে ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন? তাঁর বিদ্রোহ, তাঁর প্রেম, তাঁর মানবতা সবকিছু কি শুধুই ইতিহাসের পাতায় রয়ে গেল, নাকি আজও আমাদের সমাজের আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে?
জামিল মণ্ডল: আমি বলব, নজরুল সময়ের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা এক কণ্ঠস্বর। তাঁর সৃষ্টি শুধুই অতীতের নয়, বরং বর্তমানের এবং ভবিষ্যতেরও। তাঁর ভাষার শক্তি, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি সেগুলো আমাদের সমাজের ভিতরে থাকা অসাম্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে আজও তলোয়ার। তবে প্রশ্ন হলো, আমরা কি তাঁর থেকে কিছু শিখছি, নাকি তাঁকে কেবল পাঠ্যবইয়ের পাতায় বন্দি করে রেখেছি?
শহীদুল ইসলাম: ঠিকই বলেছো। তাঁর ‘বিদ্রোহী’ কবিতার প্রতিটি পঙক্তি যেন আজও বজ্রের মতো গর্জে ওঠে। “আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন!”এই পঙক্তি কি কেবল একটি কাব্যিক উচ্চারণ? নাকি এক চিরন্তন মানবিক মুক্তির দাবী? আমাদের তরুণ সমাজ কি এই সাহস আর মুক্তচিন্তার শক্তি তার কাছ থেকে নিতে পারছে?
জামিল মণ্ডল: এখানেই তো মূল সংকট। আমরা নজরুলের সাহিত্যে মগ্ন হই, কিন্তু তাঁর দর্শনকে ধারণ করি না। তিনি যে ভাষার ব্যবহার করেছেন, সেটি একদিকে যেমন বাংলার ঐতিহ্যবাহী সুরে বাঁধা, অন্যদিকে তাতে রয়েছে আরবী, ফার্সী, উর্দুর মিশ্রণ। এই বহুজাতিক ভাষার মেলবন্ধন কি শুধুই সাহিত্যের সৌন্দর্য? না কি এটি একটি সামাজিক বার্তা সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করার আহ্বান?
শহীদুল ইসলাম: অবশ্যই এটি একটি সামাজিক বার্তা। নজরুল দেখিয়েছেন, ভাষা কোনো সীমান্ত মানে না। তিনি ভাষার মাধ্যমে যে সেতু গড়েছেন, তা কেবল শব্দের খেলা নয়, বরং মানবিক সংহতির এক উদাহরণ। আমাদের বর্তমান সমাজে যেখানে বিভাজনের রাজনীতি চূড়ান্ত রূপ নিচ্ছে, সেখানে নজরুলের এই ভাষাগত ঐক্যের দৃষ্টান্ত কি আমাদের সামনে আলোর মশাল হতে পারে না?
জামিল মণ্ডল: তোমার কথা শুনে মনে পড়ে গেল নজরুলের ইসলামী গানগুলোর কথা। তিনি ইসলামি ভাবধারার সঙ্গে বাঙালি ঐতিহ্যকে মিশিয়ে যে গানগুলো রচনা করেছেন, সেগুলো একদিকে ধর্মীয় আবেগের প্রকাশ, অন্যদিকে বাঙালির ঐক্যের প্রতীক। কিন্তু তুমি কি দেখছো, এখন আমরা ধর্মের নামে কেবল বিভেদ তৈরি করছি? নজরুলের ‘তোরা সব জয়ধ্বনি কর’ বা ‘মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই’ এই বার্তাগুলো কি আজকের প্রেক্ষাপটে আরো বেশি প্রাসঙ্গিক নয়?
শহীদুল ইসলাম: প্রাসঙ্গিক তো বটেই। নজরুল ছিলেন এমন এক সাহিত্যিক, যিনি একইসঙ্গে প্রেমের কবি, বিদ্রোহের কবি, মানবতার কবি। তাঁর সৃষ্টিতে প্রেম এবং প্রতিবাদ একসঙ্গে বিরাজমান। সমাজের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ তিনি করেছেন, তা কোনো ধ্বংসাত্মক বিপ্লব নয়, বরং এক সৃষ্টিশীল সংগ্রাম। এই দৃষ্টিভঙ্গি আজকের তরুণ প্রজন্ম গ্রহণ করতে পারলে, হয়তো আমরা নতুনভাবে সমাজকে গড়ে তুলতে পারব।
জামিল মণ্ডল: ঠিক বলেছো। নজরুলের প্রেমিক দিকটি আমাদের অন্ধকারে পথ দেখায়। তাঁর ‘মরুঝর্ণার মত’ কাব্যের প্রেম যে গভীর মানবিকতা ও সংবেদনশীলতার কথা বলে, সেটি আমাদের বর্তমান সমাজে কতটা মূল্যবান হতে পারে, ভাবো। প্রেমের মধ্যে তিনি যে সাম্যের বীজ বুনেছিলেন, তা কি আমাদের মানসিক কাঠামো বদলানোর জন্য যথেষ্ট নয়?
শহীদুল ইসলাম: নজরুল আমাদের শিখিয়েছেন যে, সত্যিকারের প্রেম ও বিদ্রোহ একই মুদ্রার দুই পিঠ। সমাজের অবিচার ও অসাম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে হলে, আমাদের হৃদয়ে গভীর প্রেম থাকতে হবে। এই শিক্ষা যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি, তবে আমাদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে বিপ্লব আসবে।
জামিল মণ্ডল: তাহলে বলছি, নজরুলের সাহিত্য কেবল পড়ার নয়, বরং অনুভব করার। তাঁর সৃষ্টি আমাদের কণ্ঠে আর অন্তরে ধারণ করতে হবে। তবেই আমরা বুঝতে পারব, তিনি কেবল কবি নন; তিনি এক মানবিকতার মশাল। আর সেই মশালই আমাদের অন্ধকার দূর করতে পারে।
শহীদুল ইসলাম: হ্যাঁ, নজরুলকে পুনরাবিষ্কার করতে হবে। তাঁর দর্শন থেকে নতুন সমাজের ভিত্তি রচনা করতে হবে। কারণ তিনি কেবল অতীতের নন; তিনি আমাদের ভবিষ্যতেরও কবি।
বলতে বলতেই ট্রেনের আগমনী শব্দ যেন বাতাস কাঁপিয়ে দিলো, আর মুহূর্তেই চারপাশের ব্যস্ততা আরও গতি পেলো। কেউ প্রিয়জনের অপেক্ষায় উদগ্রীব, কেউ ছুটে যেতে চায় কারও আলিঙ্গনে। স্টেশনের এই ছন্দময় অস্থিরতার মাঝে, একমাত্র ব্যতিক্রম সেই মানুষটি গেটের সামনে একটি মলিন কাগজ বিছিয়ে বসে আছে, সামনে পড়ে থাকা ভাঙা থালাটি নীরব ভাষায় বলছে এক ভিন্ন গল্প। তার কোনো তাড়া নেই, নেই গন্তব্যের টান, নেই আমাদের মতো ব্যস্ততার অভিঘাত। ট্রেনের গর্জন, মানুষের চঞ্চলতা, সব যেন তার জীবনের বাইরে এক ম্লান ছায়া। এই বিশাল পৃথিবীর মধ্যেও সে যেন এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, সময়ের স্রোতে ভাসমান অথচ স্থির, এক অনন্ত অপেক্ষার প্রতিমূর্তি।
শহীদুল ইসলাম: নজরুলের কথা যখন উঠল, তখন একটা বিষয় ভাবছিলাম। তাঁর দর্শন ও সাহিত্যকে বর্তমান সমাজে প্রাসঙ্গিক করে তোলার দায়িত্বটা কি কেবল পণ্ডিতদের হাতে থাকাউচিত? নাকি আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরও একটা ভূমিকা আছে?
জামিল মণ্ডল: খুব ভালো প্রশ্ন করেছো। আমি মনে করি, নজরুলের সাহিত্য কেবল একাডেমিক চর্চায় সীমাবদ্ধ রাখা হলে তা আমাদের সামাজিক জীবনে কোনো গভীর পরিবর্তন আনতে পারবে না। আমাদের দরকার নজরুলকে প্রতিদিনের জীবনে নিয়ে আসা। তাঁর রচনা শুধু পড়া নয়, বাস্তবে প্রয়োগ করাও জরুরি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেটা আমরা কীভাবে করব?
শহীদুল ইসলাম: এই ব্যাপারে আমি মনে করি, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নজরুলকে আরও গভীরভাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। তাঁর সাহিত্য আর দর্শন নিয়ে যদি স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমে আলোচনা হয়, তাহলে নতুন প্রজন্ম তাঁকে শুধু বিদ্রোহী কবি হিসেবে নয়, বরং মানবিকতার প্রতীক হিসেবে চিনতে পারবে। তুমি কী বলো?
জামিল মণ্ডল: অবশ্যই। তবে নজরুলকে বোঝাতে গেলে কেবল তাঁর ‘বিদ্রোহী’ বা ‘অগ্নিবীণা’ নিয়ে আলোচনা করলেই হবে না। তাঁর ইসলামি গান, হিন্দু ভাবধারার কবিতা, বৈষ্ণব পদাবলী—সবকিছুকে সামনে আনতে হবে। আমাদের সাহিত্যিক বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতীক হিসেবে নজরুলকে দেখাতে হবে। তাঁর ‘তোরা সব জয়ধ্বনি কর’ থেকে শুরু করে ‘মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম’ পর্যন্ত প্রতিটি রচনায় এই বার্তাগুলো স্পষ্ট।
শহীদুল ইসলাম: ঠিক। কিন্তু আমরা কি মনে করি, বর্তমান সাহিত্যে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারছে? তুমি তো জানো, এখন সাহিত্যের ভাষা এবং রূপ অনেক পাল্টে গেছে। একদিকে গ্লোবালাইজেশনের প্রভাব, অন্যদিকে প্রযুক্তির অগ্রগতি, সবকিছুর মধ্যে নজরুলের দিকনির্দেশনা কীভাবে প্রাসঙ্গিক হতে পারে?
জামিল মণ্ডল: এটা আসলেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমি মনে করি, নজরুলের সাহিত্যে যে মানবিকতা আর সাম্যের বীজ রোপণ করা হয়েছে, তা কোনো নির্দিষ্ট সময় বা স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর দর্শনকে আধুনিক মাধ্যমগুলোর সাহায্যে প্রচার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর কবিতা বা গানকে নতুনভাবে সুরারোপ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। সোশ্যাল মিডিয়া, ইউটিউব, এমনকি পডকাস্টের মাধ্যমে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে পারি।
শহীদুল ইসলাম: ঠিক বলেছো। আরেকটি দিক হচ্ছে, নজরুল যে বহুভাষিক ও বহুসাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের কথা বলেছেন, সেটি আমাদের গ্লোবাল সমাজে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আজ যখন সংস্কৃতি নিয়ে বিভাজন বাড়ছে, তখন তাঁর মতো একজন কবির প্রাসঙ্গিকতা নতুনভাবে ভাবতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সাহিত্যে কীভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, সেটা কী ভেবেছো?
জামিল মণ্ডল: আমি বলব, নতুন সাহিত্যিকদের জন্য নজরুল এক আদর্শ হতে পারেন। বর্তমান গল্প, উপন্যাস বা কবিতায় আমরা যদি বৈষম্য আর সাম্যের বিষয়গুলো গুরুত্ব দিই, তাহলে নজরুলের প্রভাব সেখানে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাঁর বহুভাষিকতা থেকে আমরা শিখতে পারি, কিভাবে ভাষার সীমা ভেঙে সৃজনশীলতার নতুন পথ তৈরি করা যায়।
শহীদুল ইসলাম: একদম। আরেকটি বিষয় ভাবছিলাম, নজরুলের সাহিত্য থেকে আমরা যে রাজনৈতিক শিক্ষা পাই, সেটা কি বর্তমান সময়ে সাহিত্যিক আন্দোলনে ব্যবহার করা যায়? তিনি তো শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক নির্ভীক বিপ্লবী। তাঁর সাহিত্য রাজনৈতিক অসাম্য এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ। আমাদের কি এখন সেই বিদ্রোহী সত্তা আবার জাগিয়ে তোলা উচিত নয়?
জামিল মণ্ডল: একদম ঠিক। কিন্তু এই বিদ্রোহ কেবল ধ্বংসাত্মক না হয়ে সৃষ্টিশীল হতে হবে। নজরুল যেমন বিদ্রোহের মধ্যেও প্রেম আর মানবিকতার কথা বলেছেন, তেমনই আমাদের সাহিত্যেও এই ভারসাম্য থাকা দরকার। বিদ্রোহ যদি মানবিক সংহতি ও সমতার জন্য হয়, তবে সেটি চিরকাল প্রাসঙ্গিক থাকবে। আর এই দৃষ্টিভঙ্গি তরুণ প্রজন্মের সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে সমাজ বদলে যাবে।
শহীদুল ইসলাম: আমি মনে করি, নজরুলের ‘কাণ্ডারী হুঁশিয়ার’ আমাদের এখনকার সমাজের জন্য এক বিশেষ বার্তা। এই কবিতার প্রতিটি শব্দ যেন আমাদের তরুণদের নেতৃত্বের আহ্বান জানায়। আমরা কি তাঁদের এই দিকনির্দেশনা দিতে পারি না যে, সমাজ বদলানোর জন্য শুধু রাজনীতি নয়, সাহিত্যও একটি শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারে?
জামিল মণ্ডল: হ্যাঁ, নজরুল সেই উদাহরণ আমাদের সামনে রেখে গেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, সাহিত্যের শক্তি কেবল মানসিক আনন্দ দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি মানুষের চেতনাকে বদলাতে পারে। তাঁর রচনাগুলো আমাদের একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেয়। আমি বলব, আমাদের উচিত নজরুলকে নতুনভাবে পড়া, নতুনভাবে চর্চা করা এবং তাঁর দর্শনকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজে লাগানো।
শহীদুল ইসলাম: একদম। নজরুলের সাহিত্য আর দর্শন কেবলমাত্র পাঠ্যবইয়ের জন্য নয়, এটি আমাদের সমাজের নৈতিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। আমরা যদি তাঁকে নতুন প্রজন্মের মাঝে জীবন্ত করে তুলতে পারি, তাহলে আমাদের সমাজে এক নতুন সূর্যোদয় হবে।
শহীদুল ইসলাম: নজরুলের সাহিত্যিক সৃজনশীলতা এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি শুধু তাঁর সময়কালের জন্যই নয়, বরং আজকের নতুন লেখকদের জন্যও এক চিরন্তন দিশারী। তুমি কী মনে করো, নতুন লেখকরা কীভাবে নজরুলের কাজ থেকে অনুপ্রেরণা নিতে পারে?
জামিল মণ্ডল: আমার মতে, নতুন লেখকদের জন্য নজরুল এক বহুমাত্রিক শিক্ষা। তাঁর সাহিত্য এমন এক জীবন্ত উদাহরণ, যেখানে চিন্তা, আবেগ, এবং দর্শন একত্রে প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে বিদ্রোহ, অন্যদিকে প্রেম, এই বিপরীতমুখী সত্তাকে কীভাবে একত্রিত করতে হয়, তা নজরুলের সাহিত্য নতুন লেখকদের শিখিয়ে দিতে পারে। তাঁকে পড়লে মনে হয়, শিল্পের কোনো সীমানা নেই। নতুন লেখকদের তাঁর এই সীমাহীন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।
শহীদুল ইসলাম: একদম। নজরুল তো কেবল বিদ্রোহী ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক অমিত সম্ভাবনার কবি। তাঁর বহুমুখী ভাষা-ব্যবহার থেকে শুরু করে ধর্ম, সংস্কৃতি, প্রেম, এবং সাম্যের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা নতুন লেখকদের জন্য শিক্ষার এক অফুরন্ত উৎস। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, তাঁকে কীভাবে নতুন প্রজন্মের লেখকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়?
জামিল মণ্ডল: নজরুলের সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি ছিলেন স্রষ্টা এবং সংগ্রামী, যিনি সময়ের সীমাকে অতিক্রম করেছেন। নতুন লেখকদের ক্ষেত্রে প্রথমত নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিখতে হবে সাহসিকতা। তাঁর ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় যেমন অন্তর্নিহিত বিদ্রোহ ছিল, তেমনি ছিল গভীর মানবিকতার ছোঁয়া। লেখকদের উচিত তাঁর এই বৈশিষ্ট্যগুলো আত্মস্থ করা। তাঁদের সাহিত্যে সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর দৃঢ়তা থাকতে হবে এবং সেই সত্য হতে হবে মানবিক।
শহীদুল ইসলাম: আরেকটি দিক হলো তাঁর বহুভাষিকতা। নজরুল যেভাবে বাংলা ভাষায় আরবি, ফারসি, উর্দু, এবং সংস্কৃতের সমৃদ্ধ ব্যবহার করেছিলেন, তা কি নতুন লেখকদের ভাষার দিগন্তকে প্রসারিত করার জন্য দারুণ একটি উদাহরণ নয়?
জামিল মণ্ডল: অবশ্যই। ভাষার ক্ষেত্রে নজরুল নতুন লেখকদের শিখিয়েছেন, কিভাবে বহুজাতিক এবং বহুভাষিক চেতনা সাহিত্যে যুক্ত করা যায়। তাঁর এই ভাষাগত বহুত্ব শুধু সাহিত্যের শৈল্পিকতাই বৃদ্ধি করে না, বরং একধরনের সাংস্কৃতিক সংহতির প্রতীক। নতুন লেখকদের উচিত এই শিক্ষা গ্রহণ করা—যে ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি সংস্কৃতির সেতুও।
শহীদুল ইসলাম: নজরুলের কাছ থেকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো, সাহিত্যে অন্তর্দৃষ্টি বা অন্তর্ভেদ। তিনি নিজের সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবিচারগুলোকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে তা তাঁর রচনায় তুলে ধরেছেন। নতুন লেখকদের কীভাবে এই অন্তর্দৃষ্টিকে নিজেদের কাজে লাগানো উচিত বলে তুমি মনে করো?
জামিল মণ্ডল: নজরুল দেখিয়েছেন, একজন লেখক কেবল সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন না, তিনি সমাজের আয়না হয়ে ওঠেন। নতুন লেখকদের উচিত সমাজের বাস্তবতাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং তার প্রতিফলন তাঁদের সাহিত্যে তুলে ধরা। তাঁদের কলম হতে হবে সেই অস্ত্র, যা অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বলবে এবং যা এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সমাজকে উপহার দেবে। নজরুলের মতো, তাঁদেরও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ হতে হবে।
শহীদুল ইসলাম: নতুন লেখকদের জন্য নজরুলের প্রেমের কবিতাগুলোও এক বিশেষ অনুপ্রেরণা। তাঁর প্রেম মানে কেবল ব্যক্তি প্রেম নয়, এটি এক ধরনের বিশ্বজনীন মানবিক প্রেম। তাঁর ‘মরুঝর্ণার মতো’ কবিতাগুলো থেকে কী শিখতে পারি আমরা?
জামিল মণ্ডল: নজরুলের প্রেমের কাব্য দেখায়, কিভাবে ব্যক্তিগত আবেগ বৃহত্তর মানবিকতার সঙ্গে একীভূত হতে পারে। নতুন লেখকদের এই প্রেমিক দৃষ্টিভঙ্গি শেখা উচিত। তাঁদের সাহিত্য এমন হতে হবে, যা পাঠকের হৃদয়ে আবেগের সঞ্চার করবে এবং পাশাপাশি মানবিকতার বার্তা পৌঁছে দেবে। সাহিত্যিক প্রেম যেন সাম্যের ভিত্তি তৈরি করে, নজরুলের কাব্য থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই।
শহীদুল ইসলাম: ঠিক। তবে আমি আরও ভাবছি, নতুন লেখকদের ক্ষেত্রে নজরুলের রাজনীতি থেকে শিক্ষা নেওয়াটাও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি রাজনীতিকে কখনোই সাহিত্যের থেকে আলাদা করেননি। তাঁর সাহিত্য ছিল সামাজিক বিপ্লবের হাতিয়ার। আজকের লেখকদের কি সেই ধরণের দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয়?
জামিল মণ্ডল: একদম উচিত। নজরুল আমাদের শিখিয়েছেন, সাহিত্যের মাধ্যমে কিভাবে একটি জাতিকে জাগ্রত করা যায়। তাঁর রচনাগুলো শুধু সাহিত্যিক দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং সমাজ-পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবেও দৃষ্টান্ত। নতুন লেখকদের সাহিত্যে এমন বিষয়বস্তু আনতে হবে, যা মানুষের চেতনার উন্নয়ন ঘটায় এবং সমাজের প্রগতির পথে আলো জ্বালায়।
শহীদুল ইসলাম: আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করো, নজরুল কখনোই তাঁর সৃজনশীলতার স্বাধীনতাকে বিসর্জন দেননি। নতুন লেখকদের জন্য এটি কীভাবে অনুপ্রেরণা হতে পারে?
জামিল মণ্ডল: নজরুলের মতো একজন লেখক শিখিয়েছেন, সৃজনশীলতার স্বাধীনতা ছাড়া সাহিত্য অর্থহীন। নতুন লেখকদের সাহস নিয়ে লিখতে হবে—সামাজিক বাধা বা মতাদর্শিক চাপে পড়ে কখনোই নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে আসা উচিত নয়। তাঁদের কলমে থাকতে হবে সেই শক্তি, যা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিতে পারে।
শহীদুল ইসলাম: সবশেষে, নতুন লেখকদের জন্য নজরুলের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো আশা। তাঁর সাহিত্য কখনোই হতাশার নয়; এটি সবসময় আশার কথা বলে। তিনি দেখিয়েছেন, সবচেয়ে অন্ধকার সময়েও কিভাবে আলো খুঁজে পাওয়া যায়।
জামিল মণ্ডল: একদম ঠিক। নজরুল আমাদের শিখিয়েছেন, সাহিত্যের মাধ্যমে কেবল সমালোচনা নয়, নতুন পথ দেখানো যায়। নতুন লেখকদের উচিত এই আশার বার্তা তাঁদের কাজের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া। একদিন তাঁদের সাহিত্যও হয়তো নজরুলের মতোই সময় অতিক্রম করে চিরকালীন হয়ে উঠবে।
শহীদুল ইসলাম: নজরুলের সাহিত্য যেন এক অনন্ত মহাকাব্য। তাঁর চিন্তার গভীরতা এবং ভাষার প্রখরতা এমন যে, পাঠক প্রতিটি পঙক্তিতে আবিষ্কার করেন এক নতুন পৃথিবী। তবে, আজকের লেখকরা কি তাঁদের রচনায় সেই গভীরতাকে ধারণ করতে পারছে? নজরুলের মতো সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজকে নাড়া দিতে পারছে?
জামিল মণ্ডল: সমাজের গতিপথ বদলানোর মতো সাহিত্য সৃষ্টি করা কি সহজ কাজ শহীদুল? নজরুল আমাদের শিখিয়েছেন, লেখক হতে হলে হতে হবে এক মহীরুহের মতো, যে বাতাসে দোলে, কিন্তু শিকড় কখনো ছাড়ে না। তাঁর মতো কলম চালাতে গেলে প্রথমত প্রয়োজন অভিজ্ঞতার গভীরতা এবং বাস্তবতার সজাগ দৃষ্টিভঙ্গি। নজরুল কেবল শব্দ দিয়ে নয়, অনুভব দিয়ে লিখেছেন। তাঁর সাহিত্য একদিকে যেমন বিদ্রোহের প্রতীক, অন্যদিকে তা ভালোবাসার এক চিরন্তন উদযাপন। আজকের লেখকরা এই দুটি সত্তাকে কীভাবে নিজেদের মধ্যে ধারণ করবে, সেটাই আসল প্রশ্ন।
শহীদুল ইসলাম: একদম ঠিক বলেছ। নজরুল আমাদের শিখিয়েছেন, সাহিত্যিক হতে হলে কেবল চিন্তাশীল হলেই হয় না, হৃদয় দিয়ে অনুভব করাও সমান জরুরি। তাঁর ‘দুর্গম গিরি কান্তার মরু’ কবিতার পঙ্ক্তিগুলো কি আমাদের চোখে সেই দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে না! যেখানে সাহিত্যের রূপ এক বিস্ময়কর আবেগ ও যুক্তির মিশ্রণ?
জামিল মণ্ডল: নিশ্চয়ই! নজরুল আমাদের শিখিয়েছেন, কিভাবে একধরনের দার্শনিক চিন্তাকে শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হয়। তাঁর লেখাগুলো যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো, একদিকে সৃষ্টির সৌন্দর্য, অন্যদিকে অশান্তির বিদ্রোহ। নতুন লেখকরা যদি তাঁর ‘বিদ্রোহী’ কবিতার শব্দচয়ন এবং আঙ্গিক বিশ্লেষণ করেন, তবে বুঝতে পারবেন কীভাবে এক পঙক্তির মধ্যেই ব্যক্ত করা যায় বিপ্লবের অগ্নি এবং প্রেমের কোমলতা। এটা যেন সূর্যের আলো আর ছায়ার সহাবস্থান।
শহীদুল ইসলাম: কিন্তু, আমরা যদি বলি, নতুন লেখকদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো তাঁদের নিজস্ব কণ্ঠ খুঁজে বের করা? নজরুল তাঁর সময়ে কণ্ঠস্বর খুঁজে পেয়েছিলেন এবং সেটি কেবল বাংলার নয়, সমগ্র মানবজাতির কণ্ঠ হয়ে উঠেছিল। আজকের লেখকরা কি এমন কিছু করার সাহস দেখাতে পারবে?
জামিল মণ্ডল: নতুন লেখকদের মধ্যে সেই সাহস থাকতে হবে, শহীদুল। নজরুল দেখিয়েছেন, সাহসই হলো একজন লেখকের সবচেয়ে বড় সম্পদ। তাঁর ‘কারার ঐ লৌহ-কপাট’ কি শুধু একটি কবিতা, নাকি এক চেতনার প্রতীক? এটি যেন একধরনের মননশীল ডাক, যা আজও আমাদের জাগিয়ে দেয়। নতুন লেখকদের উচিত এই চেতনাকে আত্মস্থ করা এবং সাহিত্যে নতুন মাত্রা যোগ করা। তবে তাঁদের কলমের কালি হতে হবে নিষ্ঠার প্রতীক, আর তাঁদের চিন্তাভাবনায় থাকতে হবে জগতকে বদলে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা।
শহীদুল ইসলাম: আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, নজরুলের বহুমুখী অভিজ্ঞতা। তিনি একজন সৈনিক ছিলেন, সংগীতজ্ঞ ছিলেন, সাহিত্যিক ছিলেন। এই বহুমুখীতাই কি তাঁকে একজন পূর্ণাঙ্গ শিল্পী করে তুলেছে না?
জামিল মণ্ডল: হ্যাঁ, এটি তাঁকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। নজরুল ছিলেন বহুমাত্রিক শিল্পী। তিনি দেখিয়েছেন, জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা সাহিত্যিক রসদ হতে পারে। সৈনিকের শৃঙ্খলা, প্রেমিকের আবেগ, এবং সংগীতজ্ঞের সুর, সবকিছুর সম্মিলন ঘটে তাঁর রচনায়। আজকের লেখকদের এই দিকটি থেকে শিখতে হবে যে, অভিজ্ঞতাই লেখার প্রাণশক্তি। তাঁদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সাহিত্যের উপাদানে রূপান্তর করতে হবে। নজরুল যেন সেই মহাকাশ, যেখানে প্রতিটি তারা একেকটি নতুন দিগন্তের সূচনা। তাঁর সাহিত্য আমাদের শেখায়, কিভাবে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সমাজের গভীর সমস্যাগুলোকে উপলব্ধি করতে হয় এবং কিভাবে সেগুলোর প্রতিকারের পথ দেখাতে হয়। তিনি যেন সেই মহাসমুদ্র, যেখানে ঢেউয়ের প্রতিটি তরঙ্গ নিয়ে আসে নতুন ভাবনার স্পর্শ।
শহীদুল ইসলাম: নজরুলের বহুভাষিক দক্ষতা যেন তাঁর সাহিত্যকে এক অনন্য মাত্রায় উন্নীত করেছে। তাঁর রচনায় আমরা পাই বাংলা ভাষার মাধুর্য, আরবি-ফারসি-উর্দুর গভীরতা এবং সংস্কৃতের শাস্ত্রীয় ঋজুতা। আজকের লেখকদের কি তাঁর এই বৈশিষ্ট্য থেকে কিছু শেখার নেই?
জামিল মণ্ডল: অবশ্যই আছে, শহীদুল। নজরুল আমাদের শিখিয়েছেন, ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি একটি সাংস্কৃতিক সেতু। তাঁর রচনায় ভাষার ব্যবহার এমন, যেন প্রতিটি শব্দ তার নিজস্ব ইতিহাস এবং আবেগ বহন করে। তিনি দেখিয়েছেন, ভাষা যদি হৃদয় স্পর্শ করতে না পারে, তবে তা কেবল শব্দের বাহুল্য হয়ে থাকে। নতুন লেখকদের এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিখতে হবে—কিভাবে ভাষাকে শুধুমাত্র টেকনিক্যাল দক্ষতা নয়, শিল্পের স্তরে উন্নীত করা যায়।
শহীদুল ইসলাম: তাঁর এই বহুভাষিকতা কি শুধু শব্দগত প্রয়োগে সীমাবদ্ধ ছিল, নাকি এর ভেতরে ছিল একটি গভীরতর চেতনা?
জামিল মণ্ডল: এটি ছিল একটি চেতনার বহিঃপ্রকাশ। নজরুলের ভাষাগত বৈচিত্র্য কেবল আলংকারিক নয়; এটি ছিল তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। আরবি-ফারসি শব্দের মাধ্যমে তিনি একধরনের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক গভীরতা প্রকাশ করেছেন, যা তাঁর রচনাকে এক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দাঁড় করায়। একইসঙ্গে তিনি বাংলার লোকজ ঐতিহ্য এবং সংস্কৃত শিকড়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এটি একধরনের সাংস্কৃতিক সংহতি, যা আমাদের শেখায়, কিভাবে বহুজাতিক ও বহুভাষিক চেতনা সাহিত্যে যুক্ত করা যায়।
শহীদুল ইসলাম: আজকের লেখকদের কি এই বহুভাষিকতাকে তাদের কাজের মধ্যে সংযুক্ত করা উচিত?
জামিল মণ্ডল: নিঃসন্দেহে। আজকের বিশ্বায়নের যুগে, যেখানে ভাষা এবং সংস্কৃতির মেলবন্ধন প্রতিনিয়ত বাড়ছে, লেখকদের উচিত নজরুলের মতো এই বহুভাষিকতার শিক্ষা গ্রহণ করা। তবে এর জন্য প্রয়োজন গভীর পাঠ এবং চর্চা। শুধু অন্য ভাষার শব্দ ব্যবহার করলেই তা সাহিত্যিক শৈল্পিকতায় উন্নীত হয় না, সেই শব্দগুলোকে তাদের মূল প্রেক্ষাপটে উপলব্ধি করতে হয়।
উদাহরণ হিসেবে ভাবুন নজরুলের ‘ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ’ গানটি। এখানে আরবি শব্দের ছোঁয়ায় তিনি যে ধরনের আবেগ ও ধর্মীয় অনুভূতির জাগরণ সৃষ্টি করেছেন, তা একধরনের সেতুবন্ধন। এই বহুভাষিকতা তাঁর রচনায় কেবল ভাষার শৈলীই বৃদ্ধি করেনি, এটি একটি সাংস্কৃতিক সংহতির প্রতীক হয়ে উঠেছে।
শহীদুল ইসলাম: ভাষার এই সংহতিকে কি আমরা শুধু সাহিত্যিক সৌন্দর্যের জন্য ব্যবহার করব, নাকি এর ভেতরে আরো গভীর কিছু উদ্দেশ্য থাকা উচিত?
জামিল মণ্ডল: অবশ্যই ভাষার সংহতিকে আরও গভীর কিছু উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত। নজরুল আমাদের দেখিয়েছেন, ভাষার মাধ্যমে একটি সামাজিক-রাজনৈতিক বার্তাও ছড়ানো সম্ভব। তাঁর বহুভাষিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখায়, কিভাবে একটি শব্দ কেবল ভাষাগত অর্থ বহন করে না, এটি একটি ইতিহাস, একটি সংস্কৃতি, এমনকি একটি সংগ্রামের পরিচায়ক হতে পারে। নতুন লেখকদের উচিত ভাষার এই শক্তিকে বোঝা এবং এটি দিয়ে নতুন প্রজন্মের মধ্যে ঐক্যের বীজ বপন করা।নজরুলের সাহিত্য যেন এক বর্ণময় বাগান, যেখানে বাংলা হলো মূল মাটি, আরবি-ফারসি হলো সেই বৃক্ষের শিকড় এবং সংস্কৃত হলো তার উপর ছড়ানো ডালপালা। এই বাগানের প্রতিটি ফুল যেন বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি, যা একসঙ্গে হয়ে তৈরি করেছে এক অনন্য মহিমা ।
শহীদুল ইসলাম: তাহলে, নতুন লেখকদের কীভাবে এই ভাষাগত বৈচিত্র্য আত্মস্থ করতে হবে?
জামিল মণ্ডল: প্রথমত, তাঁদের নিজের মাতৃভাষার গভীরতায় ডুব দিতে হবে। নজরুলের মতো ভাষার শিকড় যদি নিজের মাটিতে শক্ত না হয়, তবে বহুভাষিকতা হবে কেবল একটি কৃত্রিম উপস্থাপন। দ্বিতীয়ত, তাঁদের পড়তে হবে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য, বুঝতে হবে সেই ভাষার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তাঁদের রচনায় এমন একটি সেতু তৈরি করতে হবে, যা বিভিন্ন ভাষার মানুষকেও একত্রে নিয়ে আসে।
শহীদুল ইসলাম: নজরুলের সাহিত্যের আরেকটি অনন্য দিক হলো এর রাজনৈতিক চেতনা। তিনি রাজনীতিকে কখনো সাহিত্যের বাইরে রাখেননি; বরং তাঁর রচনা ছিল সামাজিক বিপ্লবের হাতিয়ার। নতুন লেখকদের জন্য তাঁর এই অবস্থান কেমন দৃষ্টান্ত হতে পারে?
জামিল মণ্ডল: নজরুলের সাহিত্য এক জ্বলন্ত প্রদীপ, যা কেবল আলো দেয়নি, অন্ধকারের বিরুদ্ধেও দাঁড়িয়েছে। তিনি রাজনীতিকে তাঁর কলমের মাধ্যমে মানবিকতার রূপ দিয়েছেন। তাঁর ‘বিদ্রোহী’ কবিতার প্রতিটি পঙ্ক্তি যেন এক বিপ্লবের মন্ত্র। তিনি দেখিয়েছেন, সাহিত্যের কাজ শুধু সৌন্দর্যের সৃজন নয়, এটি এমন এক আয়না, যা সমাজের প্রতিচ্ছবি ধারণ করে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। নতুন লেখকদের জন্য এটি একটি পথ নির্দেশনা। নজরুলের সাহিত্যকে আমি তুলনা করি এক স্রোতস্বিনী নদীর সঙ্গে। এই নদী যেমন তার গতিতে পলিমাটি বহন করে জমিকে উর্বর করে তোলে, তেমনি তাঁর রচনা মানুষের চেতনার জমিকে সঞ্জীবিত করেছে। তাঁর কলমের শক্তি ছিল সেই বজ্রের মতো, যা ভয়ে নয়, বরং আলোর প্রত্যাশায় আকাশ ফাটায়।
শহীদুল ইসলাম: কিন্তু আজকের নতুন লেখকরা কি এই সাহসিকতা ধরে রাখতে পারবে? নজরুলের মতো সাহিত্যে সমাজের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মানসিকতা কি এখনো সম্ভব?
জামিল মণ্ডল: এটি সম্ভব, তবে তার জন্য প্রয়োজন সৃজনশীলতার সঙ্গে দায়িত্বশীলতার মেলবন্ধন। নজরুল কেবল তাত্ত্বিক সমালোচক ছিলেন না; তিনি ছিলেন এক বিপ্লবী চেতনার রূপকার। তিনি দেখিয়েছেন, একজন লেখক হতে হলে শুধু পাঠককে বিনোদন দেওয়া নয়, তাদের চেতনাকে আলোড়িত করাও প্রয়োজন। আজকের লেখকদের উচিত তাঁর এই শিক্ষা গ্রহণ করা এবং নিজেদের রচনায় এমন বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা, যা মানুষকে ভাবায়, জাগায় এবং বদলে দেয়। নজরুল যেন এক দীপ জ্বালিয়ে রেখে গেছেন, যা শুধু তাঁর সময়ের আঁধার কাটায়নি; এটি পরবর্তী প্রজন্মকেও পথ দেখিয়েছে। আর এই আলোকিত পথের অন্যতম উত্তরসূরী ছিলেন আহমদ ছফা। ছফার সাহিত্য যেন নজরুলের সেই দীপশিখারই আরেকটি ভাষ্য, যা নতুন প্রেক্ষাপটে নতুনভাবে সমাজকে চ্যালেঞ্জ করেছে।
শহীদুল ইসলাম: ছফা সত্যিই নজরুলের চিন্তার উত্তরসূরী। কিন্তু ছফার মতো এমন দৃষ্টিভঙ্গি কি আজকের নতুন লেখকরা তৈরি করতে পারবে?
জামিল মণ্ডল: যদি তাঁরা নজরুলের মতো দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজের দিকে তাকায়, তবে পারবে। নজরুল আমাদের শিখিয়েছেন, কিভাবে রাজনীতিকে সাহিত্যের মাধ্যমে এক মানবিক মঞ্চে উপস্থাপন করতে হয়। আজকের লেখকদেরও এই দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করতে হবে। তাঁদের সাহিত্য হতে হবে এমন, যা কেবল রাজনীতিকে প্রশ্ন করে না, বরং মানুষের প্রতি রাজনীতির দায়বদ্ধতাকেও তুলে ধরে।ভাবুন, নজরুলের সাহিত্য যেন এক মহীরুহ, যার শিকড় সমাজের গভীরে এবং শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আছে মানুষের চেতনায়। আহমদ ছফা সেই শাখারই একটি ফল, যা একই শিকড় থেকে শক্তি নিয়ে নতুন প্রজন্মকে এক ভিন্ন ধাঁচে পথ দেখিয়েছে।
শহীদুল ইসলাম: তাহলে কি আমরা বলতে পারি, সাহিত্যে রাজনীতি শুধু প্রতিবাদের ভাষা নয়, এটি একধরনের পুনর্নির্মাণের হাতিয়ারও?
জামিল মণ্ডল: একেবারেই। নজরুল শিখিয়েছেন, রাজনীতি যখন সাহিত্যে স্থান পায়, তখন এটি হয়ে ওঠে একধরনের সৃজনশীল বিপ্লব। তিনি দেখিয়েছেন, লেখকের কলম হতে পারে সেই কর্ণধার, যা সমাজের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। নতুন লেখকদের উচিত এই কর্ণধার হয়ে ওঠা, তাঁদের সাহিত্যে থাকা উচিত এমন বার্তা, যা শুধু প্রশ্ন তোলে না, উত্তরও দেয়।
শহীদুল ইসলাম: আমাদের এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, নজরুলের সাহিত্য কোনো সীমাবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ নয়। তাঁর রচনা একদিকে যেমন আবেগ ও সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ, অন্যদিকে এটি সমাজের নিপীড়িত মানুষের জন্য এক বিপ্লবের হাতিয়ার। নতুন লেখকদের জন্য নজরুলের এই দৃষ্টিভঙ্গি এক অনন্ত প্রেরণা।
জামিল মণ্ডল: একদম ঠিক বলেছ। নজরুল এমন একজন স্রষ্টা, যিনি কেবল সাহিত্যিক নন, এক আদর্শিক যোদ্ধা। তাঁর রচনার গভীরতা, ভাষার বৈচিত্র্য, মানবিকতার চেতনা এবং সাহসিকতা নতুন লেখকদের জন্য এক চিরন্তন পাঠশালা। তাঁর বিদ্রোহী চেতনা যেমন আমাদের প্রতিবাদের ভাষা শিখিয়েছে, তেমনি তাঁর প্রেমের কবিতা আমাদের মানবিকতার মূলে পৌঁছানোর শিক্ষা দিয়েছে।
শহীদুল ইসলাম: তাহলে আমরা এক কথায় বলতে পারি, নজরুলের সাহিত্য এক বহুমাত্রিক বিস্ময়। তাঁর রচনা শুধু সাহিত্য নয়, এটি মানবিকতার, প্রতিবাদের, এবং প্রেমের এক যুগান্তকারী ভাষ্য।
জামিল মণ্ডল: ঠিক তাই। তাঁর বিদ্রোহী সত্তা যেমন কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে, তেমনি মানবিকতার মূর্ছনা ছড়িয়েছে তাঁর প্রেমের কবিতায়। নজরুল দেখিয়েছেন, সাহিত্যের মাধ্যমে কেবল সমাজের অসঙ্গতি তুলে ধরা নয়, মানুষের হৃদয়ে আশার আলোও জ্বালানো সম্ভব।
শহীদুল ইসলাম: কিন্তু নজরুলের এই অন্তর্নিহিত শক্তিকে আজকের প্রজন্ম কতটা গ্রহণ করছে? নতুন লেখকরা কি তাঁর মতো সাহস এবং গভীরতা অর্জন করতে পারছে?
জামিল মণ্ডল: আমি মনে করি, নজরুলের মতো স্রষ্টারা আমাদের জন্য পথপ্রদর্শক। তাঁর সাহিত্য এক চিরন্তন মশাল। তবে এটাও ঠিক যে, প্রতিটি সময়ের নিজস্ব একটি কাঠামো থাকে। আজকের লেখকদের জন্য সেই কাঠামোর মধ্যে থেকেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে হবে। নজরুলের সাহসিকতা, প্রেম, এবং দায়বদ্ধতার দিকগুলো তাদের আত্মস্থ করতে হবে।
শহীদুল ইসলাম: তাহলে নজরুলকে আমরা এমন এক মশালের মতো দেখতে পারি, যা কেবল তাঁর যুগকে আলোকিত করেনি, বরং পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও দিকনির্দেশনা দিয়েছে। তবে, তাঁর সাহিত্য শুধু অতীতের নিদর্শন নয়, এটি যেন এক চলমান অনুপ্রেরণা।
জামিল মণ্ডল: ঠিক তাই। তাঁর সাহিত্যের প্রতিটি স্তরে যে বিদ্রোহ, প্রেম, এবং মানবিকতার মিশেল দেখা যায়, তা আমাদের শেখায় কীভাবে সৃজনশীলতাকে দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত করতে হয়। নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতা যেমন অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক বজ্রগর্জন, তেমনি তাঁর প্রেমের কবিতাগুলো যেন মরুর বুকে এক নির্মল ঝর্ণাধারা। নতুন লেখকদের তাঁর এই দ্বৈত সত্তা থেকে শিখতে হবে।
শহীদুল ইসলাম: কিন্তু নজরুলের উত্তরসূরি হিসেবে যদি আমরা কারও কথা বলি, তাহলে কি আহমদ ছফার নাম উঠে আসবে না? ছফাও তো একই রকমভাবে সাহিত্যে রাজনীতি ও মানবিকতাকে একত্রে মিশিয়েছেন।
জামিল মণ্ডল: একদম। আহমদ ছফা যেন নজরুলের উত্তরাধিকার বহন করেছেন এক নতুন প্রেক্ষাপটে। নজরুল যেখানে উপনিবেশবাদী শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানে ছফা আধুনিক রাষ্ট্রের সমাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে লিখেছেন। ছফার ‘ওঙ্কার’ কিংবা ‘গাভী বিত্তান্ত’-এর মতো রচনাগুলোতে আমরা সেই বিদ্রোহের এবং দায়বদ্ধতার অনুরণন পাই, যা নজরুলের সাহিত্যকেও সংজ্ঞায়িত করেছে।
শহীদুল ইসলাম: ছফার সাহিত্য যেন নজরুলের আলোরই আরেকটি নতুন রূপ। নতুন লেখকদের জন্য নজরুল যেমন একজন শিকড়, তেমনি ছফা এক আধুনিক শাখা।
জামিল মণ্ডল: একদম ঠিক। নজরুল আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে সাহিত্যের মাধ্যমে বিদ্রোহ করতে হয়, আর ছফা শিখিয়েছেন কীভাবে সেই বিদ্রোহকে সময়ের প্রেক্ষাপটে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হয়। নতুন লেখকদের উচিত এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখা এবং সাহিত্যের মাধ্যমে মানবতার সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করা।
শহীদুল ইসলাম: নজরুলের আলোচনার একটি সুন্দর পরিণতি হলো তাঁর উত্তরাধিকারকে চিহ্নিত করা। যাদের সাহিত্য এবং চিন্তাধারা আমাদের নতুন দিগন্তে পৌঁছে দেবে।
জামিল মণ্ডল: ঠিকই বলেছ।
পরিশেষে নজরুলকে শুধু বিদ্রোহের কবি বললে তাঁর সৃজনশীল সত্তাকে সংকুচিত করা হয়। তিনি ছিলেন কেবল কোনো একক পরিচয়ের অধিকারী নন, বরং এক বহুমাত্রিক স্রষ্টা, যাঁর সাহিত্য ও চিন্তাধারা একদিকে বিপ্লবের অগ্নিশিখা, অন্যদিকে প্রেমের স্নিগ্ধধারা। তাঁর কবিতা, গান, প্রবন্ধ ও উপন্যাসের মধ্যে যে বৈচিত্র্য, তা এক গভীর জীবনবোধের প্রতিফলন। তিনি যেন বাঙালির আত্মপরিচয়ের এক অনিবার্য ধ্রুবতারা, যাঁর রচনাবলী শাসকের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত প্রতিবাদ যেমন, তেমনি মানবমনের অন্তর্গত স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার এক সংবেদনশীল অনুরণন।তাঁর সাহিত্যকে কেবল একটি বিশেষ কালপর্বের আবদ্ধ প্রকাশ ভাবলে আমরা ভুল করব। নজরুল সময়ের সীমানায় আবদ্ধ নন, তিনি এক চিরকালীন চেতনার নাম। তাঁর বিদ্রোহ কেবল রাজনৈতিক বা সামাজিক নয়, তা গভীর দার্শনিক ও অস্তিত্ববাদী এক অভ্যুত্থান, যেখানে পরাধীনতার বিরুদ্ধে দ্রোহের পাশাপাশি রয়েছে আত্মার মুক্তির আকুতি। তাঁর প্রেম কেবল রোমান্টিক মোহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা এক সর্বজনীন মানবিক সংবেদন, যেখানে প্রেমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সৌন্দর্যের শাশ্বত উপলব্ধি।
নজরুলের সাহিত্য-সংগ্রাম কেবল অতীতের ইতিহাস নয়, তা বর্তমান ও ভবিষ্যতেরও দিশারি। আজ যখন সমাজ ক্রমাগত অন্যায়, বৈষম্য ও নিপীড়নের বন্ধনে আবদ্ধ, তখন নজরুলকে নতুন আলোয় পুনরাবিষ্কার করা জরুরি। তাঁর রচনার মধ্যে যে অসীম স্বাধীনতার ডাক, যে মুক্তির বার্তা, যে অন্তহীন মানবিকতা তা যদি আমরা সত্যিই আত্মস্থ করতে পারি, তবেই তাঁকে যথাযথ সম্মান জানানো হবে। তাঁকে পাঠ্যবইয়ের সীমায় আবদ্ধ রাখলে তাঁর প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, বরং তাঁকে চিনতে হবে জীবনের প্রতিটি অনুষঙ্গে, প্রতিটি নিঃশ্বাসে। কারণ নজরুল কেবল অতীতের নয়, তিনি বর্তমানের, তিনি ভবিষ্যতেরও।