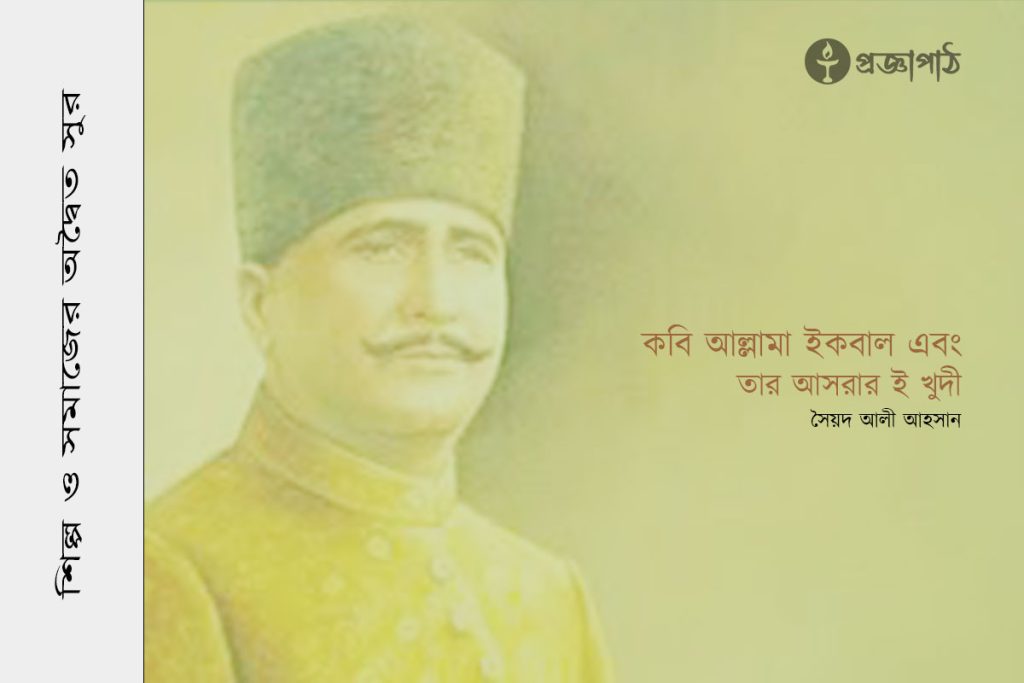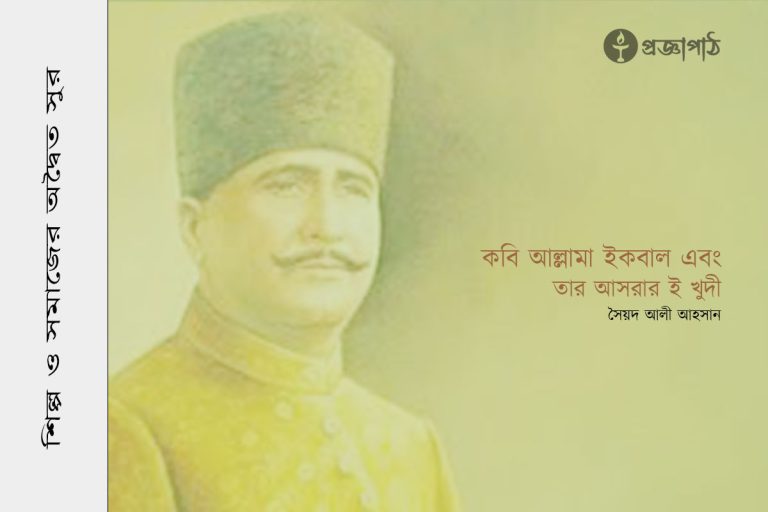অস্তিত্ব কি এবং আত্মাই বা কি- এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া খুব সহজ নয়। তার কারণ, অস্তিত্ব বা আত্মা এ দুটি শব্দের সীমাবদ্ধতা আছে। পৃথিবীতে আমাদের যে সমস্ত অভিজ্ঞতা ঘটে সে অভিজ্ঞতা বিভিন্ন সীমায় কেন্দ্রীভূত। প্রতিটি বস্তুর অথবা প্রতিটি অভিজ্ঞানের অথবা প্রতিটি বোধের আপনাপন সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু কোন কিছুই একটি সামগ্রিক চেতনায় বিচ্ছিন্ন নয়। এই সমগ্র বা এ্যাবসলিউট হচ্ছে সকল অস্তিত্বের একটি একীভূত ব্যঞ্জনা । এই একীভূত ব্যঞ্জনা একটি একক সৃষ্টি করে এবং সে এককের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। অর্থাৎ সেই একক তাঁর সীমাবোধকে এবং চিহ্নিতকরণকে হারিয়ে ফেলে। তখন প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, যদি সমগ্র বোধের কোন সীমা না থাকে তাহলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর বা অভিজ্ঞতার কেন সীমা থাকবে?
সীমার বোধটি হচ্ছে এক প্রকার মানসিক বোধ। যথার্থরূপে সসীম বলে কিছুই নেই । আমরা পৃথিবীতে যাকে বাস্তব বলি সে বাস্তবের কোন একক সত্তা নেই। একটি বাস্তব অন্য বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কিত। পৃথিবীর সকল বস্তুর মধ্যে পরস্পরগত একটি বয়ন আছে। আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অথবা বিশ্বভূমার কল্পনা যখন করি তখন তা বিভিন্ন বাস্তবের মধ্যে দিয়েই করি। যেহেতু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তুলনারহিত এবং সীমাসংবদ্ধ নয়, সুতরাং প্রতিটি জীবন নিজস্ব এককতায় পরিস্ফূট হয়েও অনন্তের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যথার্থ বাস্তব কাকে বলে তার পরীক্ষা করা খুবই কঠিন। আমরা শুধু সংক্ষেপে এ কথা বলতে পারি, বাস্তব হচ্ছে একটা সম্পর্ক বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক, বোধের সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ক, ইচ্ছার সঙ্গে প্রত্যয়ের সম্পর্ক । এভাবে চিন্তা করলে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি, সৃষ্টির প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি, এ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার নয়। আমরা অনবরত অগ্রসর হচ্ছি এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায়, এক ব্যবস্থা থেকে অন্য ব্যবস্থায়, বিশৃংখলা থেকে বোধে এবং কল্পনা থেকে প্রত্যয়ে। আমরা প্রত্যেকেই এক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় অংশভাগী। এ মুহূর্তে যেসব মানুষ পৃথিবীতে আছে তারাই কিন্তু সমগ্র মানব জাতি নয়। নতুন মানুষ পৃথিবীতে অনবরত আসছে এবং এভাবে অনন্তকাল ধরে সৃষ্টিকর্মে সকল মানুষই অংশ নিয়ে চলেছে। পৃথিবী সর্বদাই এক ধরনের পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরিপূর্ণায়ন কখনও সম্পূর্ণ হচ্ছে না। সুতরাং আমরা কখনও একথা বলতে পারি না যে, পৃথিবীর একটা সমগ্র সত্য রূপ ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে। এটা গড়ে ওঠার সাথে এবং সব সময় গড়ে ওঠার পথেই থাকবে। সৃষ্টিকর্মের ধারায় আমরা সকলেই অংশ নিচ্ছি। পবিত্র কোরআন শরীফে এ কথাই বলা হয়েছে— “আল্লাহ মহিমাময় এবং প্রশংসিত, যারা সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন প্রধান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ।
(কোরআন ২৩:১৪)
মানুষের এই যে স্রষ্টার গুণে গুণান্বিত হওয়ার ক্ষমতা বা প্রবণতা, একেই রাসূলে খোদা (সাঃ) বলেছেন— ‘তাখাল্লাকু বি আখলাক আল্লাহ।’ অর্থাৎ আল্লাহর গুণে নিজেদেরকে গঠন করে নাও। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, মানুষ অনন্যসাধারণ হচ্ছে আল্লাহর নিকটস্থ হবার চেষ্টায়।
প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে জীবন কি?
জীবন হচ্ছে অস্তিত্বের এককতা এবং এই অস্তিত্বের মহোত্তম বিকাশে যে আত্মবোধের প্রকাশ দেখি সেটি হচ্ছে ‘খুদী’ বা অহং। একটি পরিপূর্ণ চিৎপ্রকর্ষে এই অহং একটি স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে এবং আত্মসম্পূর্ণতা লাভ করে। এই আত্মসম্পূর্ণতা কিন্তু কোনদিনই আত্মসম্পূর্ণতা নয়। আল্লাহর কাছ থেকে মানুষের দূরত্ব যখন খুব বেশি থাকে তখন সে পরিপূর্ণ হয় না। মানুষ যখন আল্লাহর নিকটস্থ হয় তখন সে পরিপূর্ণতার দিকে যায়। মাওলানা রুমী তাঁর মসনভী’তে এ বিষয়ে একটি সুন্দর কাহিনী বলেছেন :
“রাসূলে খোদা তাঁর বালক অবস্থায় একবার মরুভূমিতে হারিয়ে গিয়েছিলেন। ধাত্রী হালিমা দুঃখে ব্যাকুল হয়ে যখন তাঁর অনুসন্ধান করছিলেন তখন তিনি একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, দুঃখ করো না, সে তোমার কাছ থেকে হারিয়ে যাবে না। অন্য দিকে সমস্ত পৃথিবী তাঁর মধ্যে হারিয়ে যাবে।”
যথার্থ একক সত্তা কখনই পৃথিবীর মধ্যে হারিয়ে যেতে পারে না। মূলত পৃথিবীই তার মধ্যে হারিয়ে যায়।
যথার্থ সত্যসন্ধানী পুরুষ বস্তুজগতকে নিজের মধ্যে যে ধারণ করে তাই নয়, এর উপর অধিকারও বিস্তার করে। সেই মহান প্রভু আল্লাহকেও তার অহং চৈতন্যের মধ্যে নিয়ে আসে।
কবি ইকবাল তাঁর ‘আসরার-ই খুদী’ কাব্যগ্রন্থে মানবসত্তার অহং-চৈতন্যের বিশিষ্টতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আসরার-ই খুদী প্রথম প্রকাশিত হয় লাহোরে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে । এই গ্রন্থটি একটি আকস্মিক কাব্য-প্রেরণার ফল নয়। ইকবাল প্রাচ্য দর্শন, বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন এবং পাশ্চাত্যের জ্ঞানও তিনি আহরণ করেছিলেন। তিনি জার্মানীর মিউনিখ এবং ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর গবেষণায় সফলকাম হয়েছিলেন। এ গবেষণার ফলস্বরূপ তিনি পারসিক অধিবিদ্যা বা মেটাফিজিক্স বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এটি প্রকাশিত হয় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে। এ সময় থেকেই তিনি একটি নিজস্ব জীবনদর্শন গড়ে তুলতে থাকেন।
আসরার-ই খুদী কবি’র জীবন-দর্শনের পরিচয় বহন করছে। তবে একটি কথা এখানে মনে রাখা দরকার, আসরার-ই খুদী কোন দার্শনিক নিবন্ধ নয়, এটি একটি কবিতা। এতে তিনি তাঁর জীবন এবং অস্তিত্ব সম্পর্কিত ধারণাকে বিভিন্ন কাব্য-রূপকের মাধ্যমে এ গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। যেহেতু আসরার-ই খুদী একটি কাব্যগ্রন্থ, সুতরাং কবি তাঁর কাব্যবোধের সাহায্যে তাঁর পাঠককে তাঁর প্রত্যয়ের বৃত্তে নিয়ে এসেছেন। যেহেতু ইকবাল একজন সাধারণ মাপের কবি ছিলেন না, তাই শুধু যুক্তি-তর্কের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান না করে তিনি কাব্যগত পারসুয়েশনের সাহায্যে তা করেছেন।
আমি পারসুয়েশন শব্দটি ব্যবহার করলাম ইচ্ছা করে। এটাকে ব্যাখ্যা করলে বলা যেতে পারে এক প্রকার চৈতন্যের দ্বার উদ্ঘাটন। ইকবাল বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছেন— ‘আজকের দিনের শ্রবণের কোন প্রয়োজন নেই, আমি হচ্ছি আগামী দিনের কন্ঠস্বর।’
তিনি আরও বলছেন— ‘আমি পথভ্রান্তকে গৃহে প্রত্যাগমনের সুযোগ করে দিতে চাই এবং অলস দর্শককে অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যে উদ্বুদ্ধ করতে চাই। আমি একটি উষ্ণ অভিযাত্রায় নতুন অন্বেষণে অগ্রসর হতে চাই। আমি পরিচিত হতে চাই নতুন প্রাণ-চৈতন্যের ঘোষণাকারী হিসেবে।’
জীবনের মৌলিক প্রবৃত্তি হচ্ছে অগ্রসরমানতা। সম্মুখে গমনের পথে যত বাধাই আসুক না কেন, সেসব বাধাকে জীবন উৎপাটন করে অথবা নিজের অন্তর্গত করে । অন্তর্গত করার অর্থ হচ্ছে গ্রহণ করা অথবা বলা যেতে পারে আত্মবোধের মধ্যে নিমজ্জিত করা । জীবন তার সম্মুখযাত্রায় বাসনার জন্ম দেয়, আদর্শের জন্ম দেয় এবং আপন সুরক্ষার জন্য বুদ্ধি, অনুভূতি ইত্যাদি প্রকরণেরও জন্ম দেয়। এ সময় প্রকরণ জীবনকে তার মর্যাদায় অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সর্বদা সাহায্য করে।
খুব গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা অনুভব করতে পারব যে, জীবনের অগ্রযাত্রার পথে বাধা হচ্ছে বস্তু অথবা বস্তুর স্বভাব। কিন্তু যাকে যাকে আমরা বস্তু অথবা বস্তুর স্বভাব বলছি তা কিন্তু পাপ কিংবা পরাজয় নয়, তা মানুষকে আকর্ষণ করে এবং আচ্ছন্ন করে । এবং এই আচ্ছন্নতা ও আকর্ষণের কারণে জীবন এমন একটি শক্তি লাভ করে, যে শক্তির সাহায্যে মানুষ সকল প্রকরণকে নিজের মধ্যে বিলীন করে দেয়। মানুষের যে অহংবোধ আছে, যাকে আমরা আত্মবোধ বলতে পারি, সেটা কিন্তু সর্বাংশে স্বাধীন নয়, সেটি অংশত স্বাধীন এবং অংশত সুনির্দিষ্ট। এই আত্মবোধটি তখনই পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করবে যখন তা আল্লাহর অস্তিত্বে অনন্ত চৈতন্যে বিলীন হবে।
ইকবাল তাঁর আসরার-ই খুদীতে মানুষের অহংবোধ বা আত্মবোধের এই স্বাধীনতার কথাই বলেছেন। তিনি আসরার-ই খুদীর আরম্ভে বলছেন— ‘যখন বিশ্ব-বিমোহনকারী উজ্জ্বল সূর্য রাত্রির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো একটি প্রবল দস্যুর মতো, তখন আমার ক্রন্দনে গোলাপের পাঁপড়ি নিষিক্ত হলো। আমার অশ্রু নার্গিস ফুলের অক্ষিকোটর থেকে নিদ্রা ধুয়ে ফেললো এবং আমার আবেগ কিশলয়কে জাগ্রত করল এবং প্রাণবন্ত করতে সাহায্য করল, উদ্যান-পালক আমার সঙ্গীতের ক্ষমতা পরীক্ষা করল। সে আমার কবিতাকে বপন করল এবং সেখান থেকে তরবাকীর জন্ম হলো। আমার অশ্রুর বীজকণাগুলো সে মৃত্তিকায় বপন করল। এবং আমার আর্তনাদকে সে উদ্যানের লতা-গুল্মের সঙ্গে বয়ন করল, যেমন করে কাপড় বয়ন করা হয়। যদিও আমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, তবু উজ্জ্বল দেদীপ্যমান সূর্য আমারই। আমার বৃক্ষের নিবিড়ে একশত ঊষা অবস্থান করে। জামসিদের পানপাত্রের চাইতে আমার ধূলিকণা উজ্জ্বল। আমার ধূলিকণা সে সমস্ত বস্তুকেও জানে যেগুলো এখনও জন্মলাভ করেনি।’
এভাবে প্রস্তাবনা করে ইকবাল তাঁর ‘আসরার-ই খুদী’তে আপন অভিপ্রায়ের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন। ইকবালের বক্তব্যের মধ্যে যুক্তি আছে, গভীর দর্শন আছে, কিন্তু আবেগ এবং কল্পনার উদ্দীপনা এমন একটি বিস্ময় সৃষ্টি করে যে, আমরা অভিভূত হয়ে পড়ি, তাঁর বক্তব্যকে প্রশ্ন করি না, বরঞ্চ গ্রহণ করি। যখন আসরার-ই খুদী প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন ভারতের মুসলমান যুবসমাজ বিশ্বয়ে আপ্লুত হয়ে এ বাণীকে গ্রহণ করেছিল। তাদের কাছে মনে হয়েছিল, ইকবাল এক মহান বাণীবাহক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন এবং মৃতকেও যেন প্রাণ দিয়েছেন। ইকবাল একজন আদর্শ মানুষের সন্ধানে ছিলেন, যে মানুষ বিশ্বকে অকল্যাণ থেকে, অব্যবস্থা থেকে মুক্তি দেবে। সমগ্র কাব্যের মধ্য দিয়ে এই আদর্শের পরিচয় ইকবাল আমাদের সামনে চিত্রিত করেছেন।
ইকবাল আত্মবোধসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান সেই মানুষের কল্পনা করেছেন, যে মানুষ তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে যাত্রা করে পূর্ণকাম হবে। এই তিনটি অবস্থা হচ্ছে :
(১) আল্লাহর আইনের শাসন মান্য করা;
(২) অহংবোধের চরমতম পর্যায়ে উপনীত হওয়ার জন্য আত্মসংযম এবং
(৩) আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহ্’র খলিফা হওয়ার উপযুক্ততা অর্জন ।
আল্লাহর নায়েব মানুষ তখনই হতে পারে যখন সে সর্বদিক দিয়ে সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ হবে। এই সম্পন্নতা এবং সম্পূর্ণতা হচ্ছে দেহ এবং মননের সমন্বিত বোধ এবং আমাদের মানসলোকের বিভিন্ন বিক্ষুব্ধতার মধ্যে সুর-সমন্বয়। সেই ব্যক্তিই মহোত্তম শক্তি অর্জন করতে পারেন যিনি জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে থাকেন । একজন পূর্ণকামী মানুষ তার জীবনে, চিন্তায় ও কর্মে, আবেগ এবং প্রজ্ঞায় একটি সমন্বিত অস্তিত্ব লাভ করেন । ইকবালের ভাষায় সেই মহৎ ব্যক্তি হচ্ছে মানব-বৃক্ষের সর্বশেষ পরিপক্ক ফল।
আসরার-ই খুদী’র প্রথম অধ্যায়ে কবি বলছেন— ‘অস্তিত্বের স্বরূপ হচ্ছে আত্মবোধের একটি প্রকাশ, তুমি যা কিছু দর্শন করো, সে সব কিছুই হচ্ছে ব্যক্তিসত্তার গোপন মাধুর্য যখন ব্যক্তিসত্তা পূর্ণ চৈতন্যে প্রকাশিত হলো, তখন তা চিন্তার বিচিত্র ভূমাকে প্রকাশ করল । বহুশত বাণীর রহস্য তার গভীরে লুকিয়ে আছে। আত্মপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা অনাত্মকে চিহ্নিত করতে পারি এবং এভাবে ব্যক্তিসত্তা তার বিরোধী সত্তাকেও প্রকাশ করে। সে নিজেকে একান্ত একক বলে ভাবে না, নিজেকে নিজের অতিরিক্ত বলে ভাবে। সে তার নিজের অস্তিত্ব থেকে অন্য অস্তিত্বের জন্ম দেয়, কেননা সে পৃথিবীতে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের আনন্দ নির্মাণ করতে চায়। এটা এক ধরনের হত্যা, যার সাহায্যে ব্যক্তিসত্তা আপন শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয় । এভাবে জীবনের সারবস্তুকে আমরা সংগ্রহ করি আত্মবিকীরণের মধ্যে যেমন করে গোলাপ ফুল আলোর রক্তে স্নান করে নিজেকে পরিস্ফুট করে। একটি রক্তিম গোলাপের জন্য অনেক উদ্যান ধ্বংস করতে হয় এবং বহু সব আর্তনাদের মধ্য দিয়ে একটি সুরসাম্য নির্মিত হয়, একটি মাত্র আকাশের জন্য একশটি চন্দ্র জাগ্রত করে, এবং একটি মাত্র শব্দের জন্য একশত সংলাপ নির্মাণ করে।
উপরের কথাগুলো ইকবালের ভাষণের গদ্য রূপান্তর। একসময় এ ভাষণকে আমি ছন্দে রূপান্তরিত করেছিলাম, সে উদাহরণটি নিচে উপস্থিত করছি :
‘আপনাকে হত্যা করা আপনার হাতে সেই তো শক্তির লভ্য জীবনের ব্যাপ্ত আঙ্গিনাতে অনুভব করে নেয়া আপনার সামর্থ্য-নিচয় আনন্দের আলোকের, সত্যসন্ধ জীবনের সেই হলো নব পরিচয়। জীবনের তথ্য পায় আপনারে কবি প্রবঞ্চনা। গোলাপের মতো গড়ে রক্তিম আলোকে তার জীবনের প্রমুক্ত-কল্পনা। একটি গোলাপ লাগি ভেঙ্গে ফেলে উদ্যানের পূর্ণাঙ্গ আম্বাদ, একটি সুরের লাগি আদি পথে গড়া হয় বহু আর্তনাদ। একটি আকাশ লাগি কত না নতুন চাঁদ গড়া হয় নতুন প্রভায়, সহস্র বিতর্কজাল শুধু এক সঙ্গহীন বাণীর সহায় । কেন এই অপব্যয়- নিষ্ঠুর ধরার মাঝে ব্যথার সঞ্চয় ধ্বংসের সংকট গড়ে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের নব পরিচয়।’ কবি ইকবাল তাঁর আসরার-ই খুদী মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমীর ‘মসনবী’র ভঙ্গিতে রচনা করেছিলেন। তিনি তাঁর কাব্যের প্রস্তাবনায় জালালউদ্দিন রূমীর কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, তিনি সত্য অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়ে বেদনা-বিষাদে এক রাত্রে তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। তখন তিনি একটি কল্যাণময় মধুর স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন যে, সত্যের গৃহীতা মাওলানা রুমী, তিনি ইরানী ভাষায় ফোরকান রচনা করেছেন, তিনি তাকে তন্দ্রা থেকে জাগিয়ে তুললেন এবং বললেন :
‘হে প্রেমিক নবীন প্রভাতে
প্রেমের অমৃতে পূর্ণ পাত্র তুমি লও হাতে।
হৃদয়ের সব গান এক তানে কল্লোলিয়া তুলুক উল্লাস।
একটি আঘাতে শুধু হৃদয়তন্ত্রীতে তব জাগুক উচ্ছ্বাস
পাত্রের কার্নিস যেন আঘাত আঁকিয়া দেয় মস্তকে তোমার
অক্ষির সান্নিধ্য তব দীপ্ত হোক বাঁকা তলোয়ার।
তোমার হাসির আলো উৎস হোক বহু বেদনার
তোমার চোখের পানি রক্তাক্ত করিয়া দিক অন্তর সবার ।
ঘুমন্ত কুঁড়ির মতো কতদিন রবে তুমি শান্ত অপ্রতুল?
প্রমুক্ত গোলাপ সব ব্যর্থভাবে উড়াইবে সৌরভ অতুল!
ব্যথায় মুমূর্ষ হয়ে বাক্যহীন রহিয়াছ তুমি!
রক্তিম আঙ্গারে জ্বলি চঞ্চল হউক আজি তব মনভূমি।
শান্তিরে লাঞ্ছিত করি কলকণ্ঠে জানাও বারতা
দেহের প্রতিটি রন্ধ্রে জানাইবে অন্তরের তীব্র আকুলতা।
পুঞ্জীভূত আঙ্গারের তুমি দীপ্ত প্ৰাণ
পৃথিবীতে প্রশস্ত হউক আলোর সন্ধান।’
কবি ইকবাল সূফীদের আত্মবিলোপে বিশ্বাস করতেন না, যাকে বলে ‘ফানাফিল্লাহ’। সত্তা বিলোপের যে ব্যঞ্জনার কথা তিনি বলেছেন সেটি হচ্ছে অজস্রকে আত্মবোধের মধ্যে বিনিঃশেষ করে এমন একটি অহংবোধের প্রকাশ ঘটানো, যে প্রকাশ হবে আল্লাহর যথার্থ প্রতিনিধির । মাওলানা রুমী যেভাবে আল্লাহর অস্তিত্বে বিলীন হওয়ার কথা বলেছিলেন, সে বিলীনতার মধ্যে ব্যক্তিসত্তা একেবারেই থাকবে না। ইকবাল রুমীর সে তত্ত্বকে গ্রহণ করেননি । কিন্তু তিনি রুমীর মহত্ত্বে এবং কাব্যগত তাৎপর্যে বিমুগ্ধ ছিলেন, তাই তিনি রুমীর রচনা-পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁর বিনিঃশেষ সাধনাকে গ্রহণ করেননি। ইকবাল যে জীবন দর্শন উপস্থিত করেছেন সে জীবন দর্শন হচ্ছে ইসলামের ধর্মীয় আদর্শ । যে ধর্মীয় .আদর্শ জীবনকে কৃষিক্ষেত্র বলেছে। অর্থাৎ এ পৃথিবীকে অস্বীকার করে নয়, বরং পৃথিবীর কর্মকে শুভ ও কল্যাণমুখী করে মানুষ তার ‘খুদী’ বা ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণ ঘটাতে পারে । এই সম্প্রসারণের মধ্যেই ইকবালের আত্মবোধের প্রতিষ্ঠা। ইকবাল কঠিন একটি দর্শনকে আনন্দবোধের দর্শনে পরিণত করেছেন, একটি অসাধারণ প্রজ্ঞাকে আবেগের উচ্চারণ করেছেন এবং মানুষের অস্তিত্বকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রে সমুজ্জ্বল করেছেন। তাঁর দর্শন বিনিঃশেষের দর্শন নয়, বরঞ্চ আত্মপ্রকাশের দর্শন, আত্মবিলুপ্তির দর্শন নয়, বরঞ্চ সকল সংকটের মধ্যে আত্মআবিষ্কারের দর্শন। যে মহান স্রষ্টা একক ও অদ্বিতীয়, তাঁরই প্রতিনিধি হয়ে তাঁরই সম্পূর্ণতার মধ্যে অবগাহন করার প্রচণ্ড ইচ্ছায় যে চৈতন্যের জন্ম হয়েছে সেই চৈতন্যই হচ্ছে ব্যক্তি-সত্তা বা আত্মবোধের চৈতন্য।