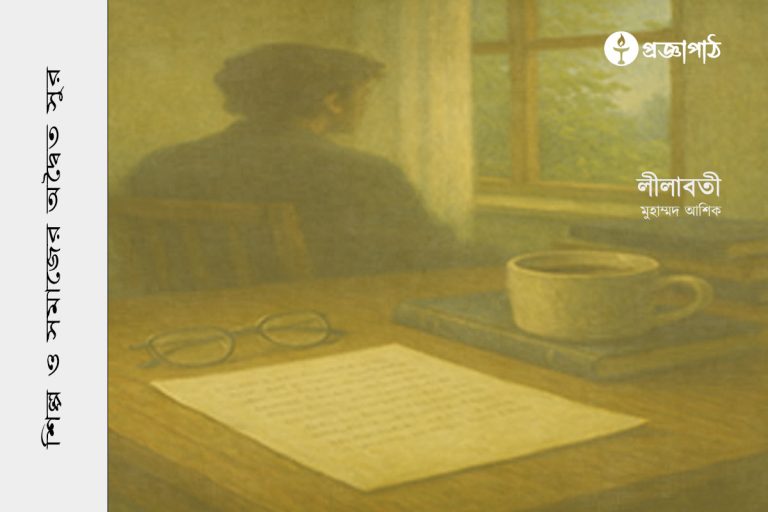তৃতীয় কিস্তি :
(গ)
জ্যোৎস্নামাখা রাত— নির্জন-নিস্তব্ধ গ্রামীণ মেঠোপথ ধরে হেঁটে চলেছি ধীরে ধীরে। পথের দুই প্রান্তে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত। মাঝে মাঝে ধানক্ষেতের ভেতর থেকে ঘাসফড়িংয়ের ক্ষীণ দপদপ শব্দ ভেসে আসছে। বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে কাঁচা ধানের গন্ধ। চাঁদের আলোয় ধূলিধুসর মেঠোপথটা যেন রূপকথার কোন দৃশ্যপট— স্বপ্নীল।
এমন সময় হঠাৎ করেই ইচ্ছে হলো, লীলাবতীকে ফোন করি। বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই— এমনিই। পকেট থেকে ফোনটা বের করে নম্বর চাপি। একটা রিং হলো। কল রিসিভ হলো। ওপাশ থেকে ভেসে এলো চেনা কন্ঠ, চেনা উচ্ছ্বাসে— “আসসালামু আলাইকুম, গুরুজী!”
“ওয়ালাইকুম আসসালাম! কী অবস্থা?”
“আলহামদুলিল্লাহ, ভাল। আপনি ভাল?
“আলহামদুলিল্লাহ, ভাল।”
“জানেন গুরুজী, আজকে একটা নতুন অভিজ্ঞতা হলো; ভাবছিলাম আপনাকে শেয়ার করবো, কিন্তু আপনিই আগে ফোন করলেন! টেলিপ্যাথি বুঝি!”
আমি হেসে বললাম— “বোধহয় তাই। কী হয়েছে বলো তো শুনি?”
“আজ একটা দাওয়াতে গিয়েছিলাম— (…ছাত্র সংগঠনের আয়োজন)। বন্ধুর অনুরোধে গিয়েছিলাম। কৌতূহল ছিল; এর আগে কখনো এমন আয়োজনে যাইনি তো, ভাবলাম দেখে আসি।”
আমি চুপ করে শুনতে থাকি। ওর গলায় তখন এক বিস্ময়— “তবে জানেন গুরুজী, প্রথম দেখায় খুবই গুছানো লাগলো— ছেলেগুলো ভদ্র, মার্জিত, অনেকেই আন্তরিকভাবে কথা বললো। মনে হলো, যেন একটা নিষ্কলুষতা আছে ওদের মধ্যে। কিন্তু যত গভীরে গিয়েছি, ততই একটা সংকীর্ণতা চোখে পড়েছে।”
“সংকীর্ণতা? কী রকম?”
“নিষ্কলুষতার ভেতরেই যেন একটা অনমনীয় কাঠিন্য রয়েছে। যে প্রশ্ন করবে, সেই যেন দুশমন। কোন ভিন্নমত পোষণ করলেই ওদের চেহারা কেমন কঠিন হয়ে যায়। মনে হচ্ছিল, তারা চায় শুধু অনুসরণ, ভাবনার স্বাধীনতা নয়।
আমি একটু চুপ থেকে বললাম— “যাদের ভিতরে নিশ্চয়তার অংহকার জন্মায় তারা প্রশ্নকে ভয় পায়। কারণ, প্রশ্ন মানেই চেতনার আয়নায় নিজের মুখোমুখি হওয়া— যেখানে ধরা পড়ে আত্মপ্রতারণার সমস্ত মুখোশ, ভেঙ্গে পড়ে অহমের সাজানো গরিমা।
আর শোন, রাজনৈতিক সংগঠনগুলো অনেক সময় মুখে বড় বড় কথা বললেও, আসলে ওরা নির্দিষ্ট একটা ক্ষমতা কাঠামোর অংশ হয়ে ওঠে। যেখানে আদর্শ কেবল উপরের দেয়ালে টাঙানো স্লোগান হয়ে থাকে, বাস্তব চর্চা হয়ে পড়ে নিয়ন্ত্রণ আর আনুগত্য প্রতিষ্ঠার খেলা।”
“গুরুজী!”
“হ্যাঁ, বলো।”
ও একটু চুপ থাকে। তারপর আবার বলে— “আপনার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে একটু বলবেন?”
“প্রথম কথা হলো, প্রচলিত রাজনীতিতে আমার আস্থা নেই।”
“কিন্তু, এই রাজনীতিই তো সমাজ বদলের পথ দেখায়, তাই না?”
“হয়তো। কিন্তু রাজনীতি যদি শুধু ক্ষমতা-কেন্দ্রীক হয়ে যায়, তবে সে আর মুক্তির পথপ্রদর্শক থাকে? থাকে না। বরং রূপ নেয় এক আত্মম্ভরী ব্যবস্থায়, যেখানে প্রভুত্বই শেষ সত্য, আর মানুষ হয়ে পড়ে শাসনের উপকরণ।
“তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন, ক্ষমতা নিজেই অকল্যাণকর?”
“না, ক্ষমতা নিজে অকল্যাণকর নয়; ক্ষমতা তো একধরণের আগুন, তা দিয়ে তুমি আলো দিতেও পার, দাহ করতেও পার। আসলে আগুন কখনো নিজে কল্যাণকর বা অকল্যাণকর নয়— তার নিয়ন্তাই মুখ্য।
মহাভারতের দিকে চেয়ে দেখ— অর্জুন গান্ডীব হাতে পেয়ে যুদ্ধ জিতেছেন, কারণ সে কুশলী, শৃঙ্খলিত, আর তার লক্ষ্য স্পষ্ট। অন্যদিকে কর্ণ— অসাধারণ ক্ষমতা-দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও, তাঁর ভেতরের দন্ধ, অন্যায়ের প্রতি আত্মসমর্পণ, আর বিভ্রান্ত অবস্থান— তাকে শেষ পর্যন্ত ট্রাজেডিক চরিত্রে পরিণত করেছে।
এখানে এই পার্থক্যটা বুঝতে হবে যে, ক্ষমতা নিজের গুণে কল্যাণকর বা অক্যাণকর নয়, এটা নির্ভর করে ক্ষমতা কে ধারণ করছে, কীভাবে করছে, আর কোন উদ্দেশ্যে করছে।
ক্ষমতা অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু তার ভিত্তি হওয়া চাই যোগ্যতা, নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ আর লক্ষ্যবোধ।”
“তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন, সমাজ বদলাতে হলে আগে মানুষকে বদলাতে হবে?”
“ঠিক তাই। যদি আমরা মানুষের চিন্তা, নৈতিকতা আর চরিত্র গড়তে না পারি, তাহলে যত কাঠামোই বদলাই, ফল খুব ভাল হবে না। আমি চাই, রাজনীতি হোক মানুষের বিকাশের মাধ্যম; কেবল ক্ষমতা ক্ষমতা খেলা নয়। যেখানে নেতৃত্ব মানে সেবা, আর সংগঠন মানে শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের জায়গা।”
“আপনি তাহলে এক ধরণের ইউটোপিয়া কল্পনা করছেন; যেখানে মানুষ স্বার্থপরতা ছাড়বে, লোভ ছাড়বে, আর নেতৃত্বের লড়াই নয়; খেদমতের প্রতিযোগিতা করবে?”
আমি হাসলাম। —“হ্যাঁ, ইউটোপিয়া বলেই তো চেষ্টা থেমে যায়। আমি তাকে বলি স্বপ্নের বাস্তব, যে স্বপ্ন বাস্তব হবার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু তার জন্য দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দরকার।
জেনে রাখ, সমাজ বদলের শুরুর বিন্দু মানুষ নিজে— ব্যক্তির বদল থেকেই আসে বৃহত্তর রূপান্তর; কারণ, মানুষ সমাজ বিচ্ছিন্ন নয়। আমার ভাল শুধু আমার ভাল থাকা নয়, তা সমাজের অন্যের কষ্টের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এই বোঝাপড়া থেকেই জন্ম নেয় পরিবর্তনের আকাঙ্খা। যে পরিবর্তন কেবল নিজেকে পাল্টাতে চায় না; চায় সবাইকে নিয়ে সামনে আগাতে। এই চেতনা বোধকেই আমি প্রকৃত রাজনতি বলে বিশ্বাস করতে চাই। যেখানে ক্ষমতা মানে আধিপত্য নয়— দায়িত্ব। যেখানে নেতৃত্ব মানে সেবা, আর সংগঠন হয় আত্মগঠনের স্থান।
এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই জন্ম নেয় ‘কল্যাণ রাষ্ট্র’র ধারণা। যেখানে রাষ্ট্র কেবল আইন বা দমনযন্ত্র নয়; বরং এমন একটি কাঠামো, যা ব্যক্তি ও সমাজকে একসাথে বিকশিত হতে সাহায্য করে।
এটা কোন স্বপ্নবিলাসী চিন্তা নয়; বরং বাস্তবের সম্ভাবনা। যদি আমরা বদলের সূত্র খুঁজি নিজেদের ভিতরে, তাহলে সমাজও বদলায়, আর নাগরিক চেতনার রূপান্তরেই রাষ্ট্র পায় নতুন রূপ।
এই জায়গা থেকেই মওলানা ভাসানী উচ্চারণ করেছেন— ‘যত সরকার বদল করি না কেন, কোন ফলোদয় হইবে না, যদি না শাসকর্গ চরিত্রবান হয়।’ কারণ রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ভর করে শাসকের চরিত্র আর মানুষের চেতনার উপর। যার সূচনাবিন্দু সেই প্রাচীণ সুফি প্রশ্নেই নিহিত— ‘আমি কে?’ এই আত্মসন্ধানের পথ ধরেই শুরু হয় সত্যিকার বদলের যাত্রা।”
“আপনি মনে করেন, এই পরিবর্তন সম্ভব?”
আমি পুকুরের জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখি, দেখি চাঁদের প্রতিবিম্ব জলে কাঁপছে। আমি বলি “আমি বিশ্বাস করতে চাই, একদিন এই জ্যোৎস্নার মতো আলো ঠিকই ছড়াবে, যারা দেখে না তারা দেখবে, যারা দেখে তারা দায়িত্ব নেবে।”
ওপাশ থেকে একটি শব্দ ভেসে এলো— “আমি দেখছি গুরুজী, আমি দেখছি।”