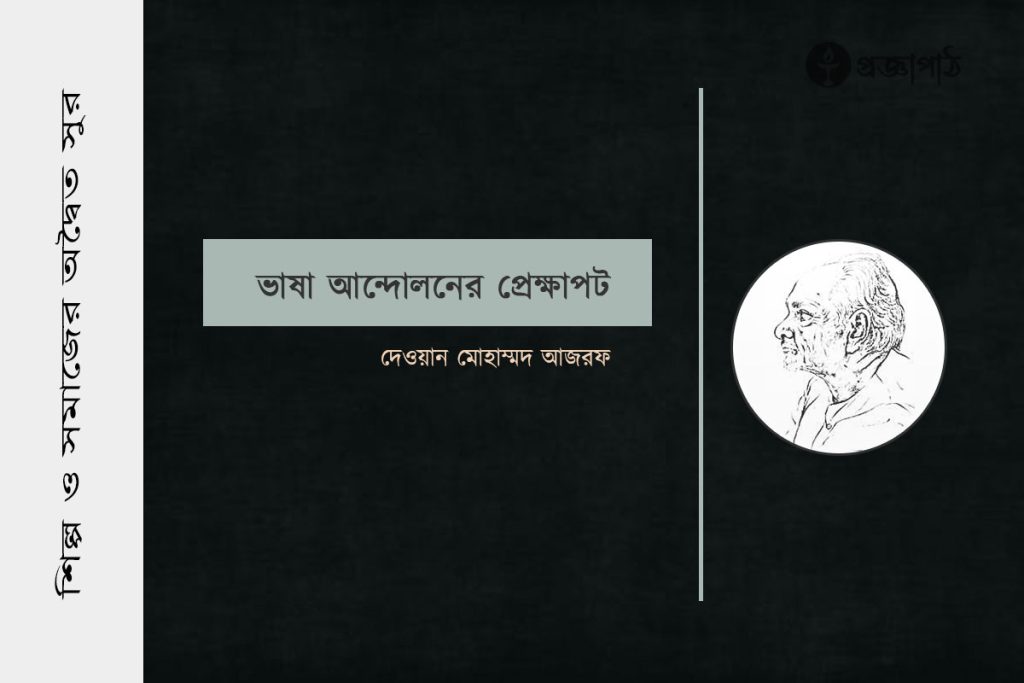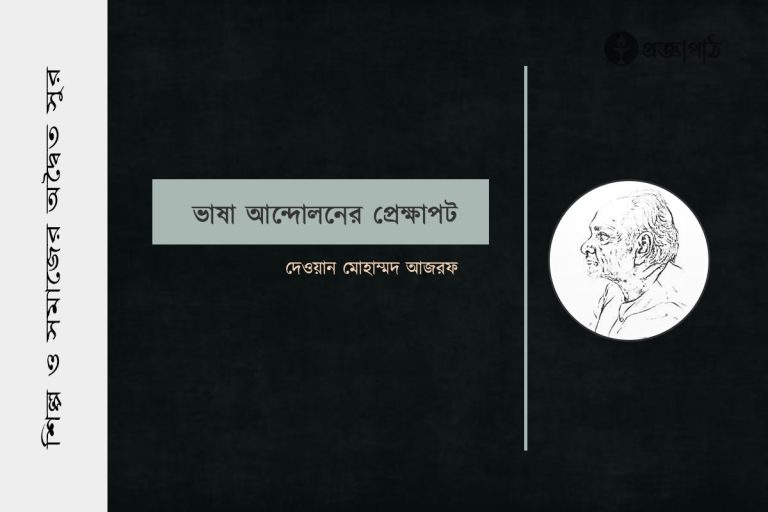আমাদের প্রথম স্বাধীনতা এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার মধ্যে ভাষা আন্দোলন হচ্ছে একটা মধ্যবর্তী পর্যায় । এ সম্বন্ধে অনেকের মনেই ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে, এজন্য এ সম্বন্ধে পরিষ্কার আলোচনা হওয়া প্রয়াজন ।
সপ্তম শতাব্দীতে এদেশে মুসলিমদের আগমন থেকে দীর্ঘকাল যাবৎ এদেশীয় মুসলিমরা বহিরাগত বলেই পরিগণিত ছিল। ফকির-দরবেশ ও মুসলিম বণিকেরা এদেশে নানা স্থানে বসতি স্থাপন করে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন। কোন কোন স্থানে নির্যাতিতও হয়েছেন। ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক এদেশ বিজিত হলে মুসলিমেরা এদেশে বাস করার একটা মস্তবড় নিরাপত্তা লাভ করে। ইখতিয়ারের পূর্ববর্তী সেন রাজাগণ বাংলা ভাষার প্রতি ছিলেন অত্যন্ত বিমুখ । তাদের রাজসভায় সংস্কৃত ভাষার নুতন রূপ প্রচলিত ছিল । বাংলা ভাষাকে তারা অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন। এজন্য তাদের রাজত্বকালে বাংলা ভাষা বিকাশ লাভ করতে পারেনি । দেবভাষা, প্রাকৃত, শৌরসেনী, মাঘধি প্রভৃতি স্তর পার হয়ে বাংলা ভাষা সেন রাজাদের সময় যেরূপ পরিগ্রহ করেছিল, ইখতিয়ার উদ্দিনের বিজয়ের পর তাতে আরবি, ফার্সি ও তুর্কি বেমালুমভাবে প্রবেশ করে। পরবর্তী শাসনকর্তা আলাউদ্দিন হুসেন শাহ’র পৃষ্ঠপোষকতায় সে ভাষাই বাংলাদেশের জনগণের ভাষা হয়ে দেখা দেয় । তবে তুর্কি সুলতানগণ এ ভাষাকে তাদের দরবারের ভাষা বলে গ্রহণ করেননি। তাদের ধর্মীয় ভাষা ছিল আরবি, তাদের দরবারের ভাষা ছিল ফার্সি এবং তাদের কথ্য ভাষা ছিল তুর্কি । ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত মোটামুটি এভাবেই চলে আসছিল ।
বঙ্গদেশের জনগণের ভাষা ছিল আরবি, ফার্সি ও তুর্কি মিশ্রিত বাংলা । ইংরেজরা এদেশ দখল করার পরে দরবারের ভাষা ফার্সিই থেকে যায়, কথ্য ভাষা পূর্বোক্ত ভাষায় পরিণত হয় এবং বঙ্গদেশের কবিগণ সেই মিশ্রিত ভাষাতেই রচনা করতে থাকেন।
১৮০০ সালে কোম্পানি সরকার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল সদ্যনিযুক্ত ইংরেজ সিভিলিয়ানগণকে বাংলাভাষায় শিক্ষাদান করা। সে পণ্ডিতগণের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামজয় তর্কালঙ্কর প্রমুখ ব্যক্তি । তারা অনুস্বর বিসর্গ বর্জিত সংস্কৃত ছাঁচে বাংলা ভাষা তৈরি করেন। তার ফলে মুসলমান সমাজে একটি বর্জনের ভাব দেখা দেয়। পূর্বোক্ত মিশ্রভাষায় রচিত পুস্তকাদি তখন বটতলার ছাপা, কলমী পুঁথি, দোভাষী পুঁথি প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত হয় ।
পাঠান রাজত্বকালে দিল্লির চতুর্পার্শ্বে অবস্থিত খড়িবুদির সঙ্গে তৎকালীন দরবারি ভাষা ফার্সির একত্র মিলন করে একটা মিশ্র ভাষা সৃষ্টি করার চেষ্টা বহুদিন থেকে চলে শ্বাসছিল। সেই মিশ্র ভাষার প্রথম কাব্যিক রূপ দেন কবি আমীর খসরু দেহলভী –
“হিন্দুবাচ্চেরা বনিগর আজব হুসনধর তো হ্যায়
দর অকতে সোখন গুফতম মুহফুল ঝারত হ্যায়
গুফতমবিয়া দর লবেতু বুসে বনীরম ।
গুফত আরে রাম ধরম নষ্ট করতে হ্যায়
এ ভাষা গঠন করার মূল উদ্দেশ্য ছিল আরব, পারস্য, তুর্কি প্রভৃতি দেশ থেকে আগত সৈন্যদের সঙ্গে এদেশীয় সৈন্যদের একটা সাধারণ ভাষা সৃষ্টি করা। এজন্য একে উর্দু ভাষা বলা হয় । উর্দু শব্দের অর্থ তাঁবু বা শিবির।
এ ভাষাই ক্রমশ দিল্লি, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের সাধারণ সাংস্কৃতিক ভাষা হয়ে দাঁড়ায়। জবচার্ণক প্রতিষ্ঠিত কলকাতা শহরে নানা কাজ উপলক্ষে আগত লোকদের মধ্যে মুসলমানদের কোন সাধারণ ভাষা না থাকায়, এরা উর্দুকেই তাদের সাংস্কৃতিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে। তার ফলে উর্দু অত্যন্ত দ্রুত গতিতে মস্তবড় ভাষাতে পরিণত হয়। পলাশীর পতনের পর কলকাতা ভারতের রাজধানী হওয়ায় ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে আগত পূর্বোক্ত মুসলমানেরা উর্দুকে অবলীলাক্রমে তাদের সাধারণ ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে ।
পূর্বেই বলা হয়েছে বঙ্গদেশের মুসলমানদের মধ্যে অভিজাত উচ্চকোটি মহল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রসূত বাংলা ভাষাক তাদের মাতৃভাষারূপে গ্রহণ না করে উর্দুকেই তাদের সাংস্কৃতিক ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে। কলকাতার বাইরে প্রায় সকল শহরেই এমন কতকগুলি পরিবার ছিল যাদের কথ্য ভাষা ছিল উর্দু।
বাংলাদেশে মুসলিম পুনর্জাগরণের সূত্রপাতের সূচনায় নওয়াব অব্দুল লতিফ কর্তৃক ১৮৬৩ সালে ‘মহামেডান লিটারেসি সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে আবদুল লতিফ সর্বসাধারণ মুসললমানের মাতৃভাষারূপে বাংলাকে গ্রহণ করার উপদেশ দেন । তবে তার এ উপদেশ সঙ্গে সঙ্গেই কার্যকরী হয়নি।
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যশোর জেলায় খ্রিষ্টান পাদ্রীগণ মুসলমানদের অধিক সংখ্যায় খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে আরম্ভ করলে মুন্সি মেহেরুল্লাহ বাংলা ভাষার মাধ্যমে তার বিরুদ্ধচারণ করতে আরম্ভ করলেন। এ সময় বাংলা ভাষা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তার পূর্ববর্তী মীর মোশাররফ হোসেন প্রমুখ কথা সাহিত্যিকগণ এবং তার পরবর্তী মওলানা মনিরুজ্জামান, মওলানা আকরাম খাঁ প্রমুখ আলেমগণ ইসলামের নানাবিধ বিষয়ে পুস্তকাদি লিখতে আরম্ভ করলেন । বাংলা ভাষা সকল স্তরের মুসলিমদের মধ্যে জনপ্রিয় ভাষা হয়ে পড়ে। তবে নজরুল ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত কোন কোন মহলে উর্দুর প্রতি আকর্ষণ তখনও লোপ পায়নি। যাক ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত পর্যন্ত তথাকথিত অভিজাত মহলে উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার পক্ষে অভিমত ছিল।
১৭৫৭ সনের পর ইংরেজ সরকার কর্তৃক এদেশীয় মুসলমানদের নানাভাবে নির্যাতনের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় হচ্ছে তাদের অর্থনেতিক জীবনকে নানাভাবে পঙ্গু করার চেষ্টা। একে একে দেওয়ানী বিভাগ থেকে মুসলমানদের বিতাড়ন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন, কোর্ট কাছারীর ভাষারূপে ফার্সির স্থলে ইংরেজি ভাষার প্রবর্তন, বাজেয়াপ্তী আইন প্রয়োগ করে মুসলমানদের বরাবরে দানকৃত নানাবিধ জায়গীর ও ওয়াকফ সম্পত্তিগুলো বিলুপ্ত করে মুসলমানদের সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত করার চেষ্টা চলে । মুসলমানেরা স্বভাবতই ইংরেজদের ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে এবং ১৮৫৭ সালে তাদের বিক্ষোভ সিপাহী বিপ্লবে প্রকাশ করে।
এতে পর্যুদস্ত হয়ে তারা এদেশ থেকে হিজরত করার চেষ্টা করে। সে সময়ে স্যার সৈয়দ আহমদ আলীগড় আন্দোলনের প্রবর্তন করে এদেশে মুসলমানদের একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। পূর্বে বর্ণিত নওয়াব আব্দুল লতিফের সঙ্গে তিনি মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্যে আলীগড়ে ‘মহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ’ স্থাপন করেন। তদবধি মুসলিম সমাজে একটা প্রবল স্বাতন্ত্র্য চেতনা দানা বাঁধতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত সৈয়দ জামালুদ্দিন আল আফগান এ বিশ্বে সকল মুসলিমদের মধ্যে একই জাতীয়তাবোধের চেতনা সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে যে প্রচারণা করেছিলেন, তাতেও এই ভারতে সকল মুসলমান এক জাতি বলে একটা প্রবল প্রচারণা ছিল। বঙ্গদেশে এ ধর্মীয় জাতীয়তাবোধের ধারক ছিলেন জাস্টিস সৈয়দ আমীর আলী ও স্যার আব্দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী। ১৯০৬ সালে ঢাকাতে মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার পরে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ সে চেতনাকে আরও সুদৃঢ় করেন এবং সে চেতনার পরিপোষকতায় ভারতের বাইরেও গাজী মোস্তফা কামাল পাশার উদ্যোগে ও সৈয়দ দলীল আহমদ সৈনৌশীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে “সিল-সিলায়ে জামিয়া-ই ওয়াহেদ উমান ইসলাম” নামে যে সমিতি গঠিত হয়েছিল, তাতেও মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলিকে ভারত থেকে পৃথক করে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করার তাগিদ ছিল। তার ফলে ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব এবং ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ এখন সর্বস্তরের লোকের নিকটই পরিচিত সত্য।
এ বিভাগের মূলসূত্র ছিল এক ধর্মাবলম্বী মানুষ মাত্রেই এক সংস্কৃতি এবং একই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী কাজেই তারা এক জাতি; তাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ধর্মকে রক্ষা করতে হলে তাদের জন্য পৃথক আবাস ভূমি প্রয়োজন। বিভাগ পরবর্তীকালে স্পষ্টই বুঝা গেল যে সে ধারণা প্রকৃতপক্ষে সঠিক নয়। কারণ সংস্কৃতির একটা প্রধান অঙ্গ হচ্ছে ভাষা। সে ভাষা নিয়েই প্রথম তৎকালীন পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে বিশেষ করে পাঞ্জাব অঞ্চলের লোকদের সঙ্গে বাংলাদেশবাসী লোকদের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। তারা উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে চায়। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশবাসীর মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটি পরিবার উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিল। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ (প্রায় ৯৯% জন) লোকই সম্পূর্ণরূপে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিল ।
এক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় যে এই ভাষা আন্দোলন ছিল এদেশীয় লোকের পক্ষে স্বাভাবিক।
সেন রাজাদের আমলে বাংলা ভাষা যে স্বাভাবিক বিকাশ পায়নি, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর তা যেভাবে বিকৃত হয়েছে, ভাষা আন্দোলন না হলে তা একেবারে বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত হতো ।
বাংলাদেশে এক জাতীয়তা সৃষ্টির জন্য বাংলা ভাষার স্থিতি অত্যন্ত প্রয়োজন একথা অনস্বীকার্য। পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যে এমন কোন শর্ত ছিল না যেকোন বিশেষ ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীকে নিষ্পিষ্ট করতে হবে। এজন্য যারা প্রকৃত পক্ষে পাকিস্তানবাদী ছিলেন তারাও বাংলা ভাষার স্বপক্ষে আন্দোলনকারীদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। মরহুম মাওলানা আকরাম খাঁ, মরহুম মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ এককালীন পাকিস্তানবাদী ব্যক্তিগণ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার পক্ষপাতী ছিলেন । ফলে আন্দোলনের প্রখরতা ছিল তীক্ষ্ণ।
স্বভাবতই কোন রাষ্ট্র সম্বন্ধে যেকোন ধারণাই পোষণ করা হোক না কেন, সে রাষ্ট্রে সর্বসাধারণের ভাষাকে নষ্ট করার কোন প্রচেষ্টাকে সে রাষ্ট্রের জনগণ সহ্য করতে পারে না। যার ফলশ্রুতিতে এ দেশীয়রা বাংলা ভাষার পক্ষে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল।
০